সাংবিধানিক সংস্কার ও গণতন্ত্রের অন্বেষণ

লাতিন একটি ম্যাক্সিম আছে ‘Ut res magis valeat quam pereat’, অর্থাৎ কোনো জিনিসের অকার্যকর হওয়া অপেক্ষা ফলদায়ক করে বাঁচিয়ে রাখা অধিকতর উত্তম। বলছিলাম বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনি দলিল ‘গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান’-এর কথা। সম্প্রতি বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রোষানলে পড়ে শেখ হাসিনা সরকারের পতন ত্বরান্বিত হয়েছে। বহু ছাত্র-জনতার প্রাণের বিনিময়ে স্বৈরাচারী সরকারের পতন নিশ্চিত হয়েছে, এমনই বাস্তবিক মন্তব্য করা হচ্ছে।
সরকার পতনের পর ‘অভ্যুত্থান যেখানে সফল সংবিধান সেখানে অকার্যকর’ শিরোনামেও লেখালেখি হচ্ছে। শিরোনামের ভাষ্য মোটামুটি প্রাসঙ্গিক। তবে এটাও ভেবে দেখার বিষয় যে, নতুন সংবিধান প্রণয়ন করা হলে বিতর্ক থেকে যাওয়ার মতো সম্ভাবনা আছে কি-না। আসলে সংসদীয় ও গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় সে দেশের সংবিধানকে ওই রাষ্ট্রের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের দর্পণ বলা হয়। বলাবাহুল্য যে, রাষ্ট্র যদি যন্ত্র হয়, তবে সংবিধান নামক সেই যন্ত্রের কলকব্জা কিভাবে চলবে।
আয়নায় আমরা যেমন আমাদের দেহের বাস্তব প্রতিবিম্ব দেখতে পাই, ঠিক তেমনি সংবিধানেও একটি দেশের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড কেমন হবে তার প্রতিফলন ঘটে। আমরা বিতর্কহীনভাবে অবগত যে, দলমত-ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে জাতীয়তাবাদী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি স্বৈরাচারী শাসন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আমরা বাঙালি জাতি পেয়েছিলাম সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা চিরসবুজ এক স্বাধীন দেশ। ৩০ লাখ শহীদের রক্ত ও ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমহানির মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে আমাদের এই স্বাধীনতা। তাদের রক্ত ও মর্যাদার মূল্য কখনো ভুলে যাওয়ার নয়।
শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের এ কথাও স্মরণ করা প্রয়োজন যে, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রাণের বিনিময়েই ৫৬ হাজার বর্গমাইলের (১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার) আমাদের এই ছোট ভূখণ্ডটি বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পেয়েছিল। আমাদের এটাও দৃঢ়ভাবে মনে রাখা প্রয়োজন, যে স্বৈরাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই স্বৈরশাসন ও বৈষম্য যেন স্বাধীন দেশে পুনরায় ফিরে না আসে। তবেই মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা স্বাধীন দেশে বিরাজমান থাকবে, শহীদদের আত্মা শান্তি পাবে।
এরই ধারাবাহিকতায় ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ সংবিধান প্রনয়নের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক গণপরিষদ আদেশ জারি করা হয়েছিল। উক্ত আদেশানুসারে স্বাধীনতাপূর্ববর্তী বিভিন্ন সময়ে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনগুলোতে বাংলাদেশের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। গণপরিষদ গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করা। এরপর ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গণপরিষদ খুবই স্বল্প সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সামনে রেখে স্বাধীন দেশের জনগণের জন্য এক পবিত্র দলিল উপহার দিয়েছিলেন।
উল্লেখ্য, উক্ত সংবিধানকে সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সামগ্রিকভাবে সকলের জন্য বাস্তবসম্মত করার লক্ষ্যে ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সংবিধানকেও অনুসরণ করা হয়েছিল। সর্বোপরি গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গৃহীত এবং একই সালের ১৪ ডিসেম্বর তৎকালীন স্পিকার শাহ্ আব্দুল হামিদ (ডেপুটি স্পিকার মোহাম্মদ উল্লাহ্) কর্তৃক প্রমাণীকৃত হয়ে সাধারণের ‘জ্ঞাতার্থে' বা অবগতির জন্য প্রকাশিত হয়। অতঃপর একই মাসের ১৬ ডিসেম্বর থেকে তার কার্যকারিতা দেয়া হয়।
মনে রাখার বিষয় হলো, উক্ত সর্বোচ্চ আইনি দলিলকে স্থায়ী রূপ দিতে অনুচ্ছেদ নং ৭-এ উক্ত সংবিধানকে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয় এবং এর সাথে অসামঞ্জস্য সকল আইনকে বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য বাতিল ঘোষণা করা হয়। পরিতাপের বিষয় হলো, সংবিধানকে স্বাধীনতার ৫৩ বছরের মধ্যে প্রয়োজনের চেয়ে স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক এ পর্যন্ত ১৭ বার সংশোধন করা হয়েছে। যদিও দুটি থেকে তিনটি সংশোধনী ছাড়া অন্য সংশোধনীগুলো স্ব স্ব সময়ে বিশেষজ্ঞ মহল কর্তৃক বহু আলোচনা-সমালোচনাও হয়েছে। কিন্তু প্রবাদ আছে, স্বার্থের কাছে সমালোচনা তুচ্ছ।
উল্লেখ্য, কয়েকটি সংশোধনীকে ইতোমধ্যে গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং কিছু সংশোধনীকে সময়োপযোগী হিসেবেও সর্বোচ্চ আদালত (সুপ্রিমকোর্ট) কর্তৃক ঘোষিত হয়েছে।
বর্তমান সংবিধানের নিরপেক্ষ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংবিধানের শুরুতে লিপিবদ্ধ প্রস্তাবনায় উক্ত সংবিধানের সামগ্রিক দর্শন হিসেবে আদর্শ রাষ্ট্রের রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অধ্যায়ে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র-শোষণমুক্তি, গণতন্ত্র-মানবাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা-ধর্মীয় স্বাধীনতা, মৌলিক-সামাজিক নিরাপত্তা, গ্রামীণ উন্নয়ন, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা, সুযোগের সমতা, নাগরিক ও সরকারি কর্মচারীদের কর্তব্য, ক্ষমতার পৃথকীকরণ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের নীতি শিরোনামে যে কয়টি অনুচ্ছেদ (৮-২৫) বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, সবকটি অনুচ্ছেদই একটি আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। ৮নং অনুচ্ছেদে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই অধ্যায়ে বর্ণিত নীতিসমূহ বাংলাদেশ পরিচালনার মূলসূত্র হবে, আইন প্রণয়নকালে রাষ্ট্র তাহা প্রয়োগ করবেন, এই সংবিধান ও বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যাদানের ক্ষেত্রে সেগুলো নির্দেশক হবে এবং তাহা রাষ্ট্র ও নাগরিকদের কার্যের ভিত্তি হবে।
একইভাবে তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে (২৬-৪৭নং অনুচ্ছেদ) দেশের জনগণকে আইনের দৃষ্টিতে সমতা, ধর্ম-বর্ণভেদে বৈষম্য বিলোপ, সরকারি নিয়োগে বৈষম্যরোধ, জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, গ্রেফতার ও আটকের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নীতি, জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা, বিচার ও দণ্ডের বিধান, নাগরিকের চলাফেরা-সমাবেশ-সংগঠন-চিন্তা ও বাকস্বাধীনতা, স্বাধীনভাবে পেশা নির্বাচন, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পত্তি ধারণের অধিকারসহ আরো কিছু বাস্তবসম্মত বিধান বর্ণিত হয়েছে। এমনকি ২৬নং অনুচ্ছেদে স্পষ্টভাবে এটাও বলে দেয়া হয়েছে যে, রাষ্ট্র তৃতীয় ভাগের কোনো বিধানের সহিত অসামঞ্জস্য কোনো আইন প্রনয়ণ করবেন না এবং অনুরূপ কোনো আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোনো বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্য, ততখানি বাতিল হইয়া যাবে।
এখানে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনুচ্ছেদ নং ৪৪-এর মাধ্যমে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত সকল মৌলিক অধিকারকে আরো সুসংহত করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে, এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকার দেয়া হইল। অর্থাৎ তৃতীয় ভাগের কোনো অধিকার কারো দ্বারা বা কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লঙ্ঘন হলে সেই অধিকার ফিরে পেতে হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করা যাবে। একই ভাবে আমরা যদি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৭নং, ২২নং, ৪৪নং, ১০২ নং এবং একই সাথে ১০৬নং অনুচ্ছেদ লক্ষ্য করি তবে বুঝতে পারি যে, সরকারের প্রধান তিনটি অঙ্গ নির্বাহী বিভাগ, আইনসভা ও বিচার বিভাগের মধ্যে কি সুন্দরভাবে ভারসাম্য নীতি (check and balance) নিশ্চিত করা হয়েছে। এমনকি সরকারের কোনো অঙ্গসংগঠন যেন ক্ষমতার অপব্যবহার করে স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে না পারে, সেজন্য অনুচ্ছেদ ৫৫-এর ৩নং উপ-অনুচ্ছেদে সমগ্র মন্ত্রিপরিষদকে (ক্যাবিনেট) স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে সংসদের নিকট যৌথ দায়ের বিধান (collective responsibility) নিশ্চিত করা হয়েছে।
এত সুন্দর সুস্পষ্ট নীতি দেশের সর্বোচ্চ আইন খ্যাত সংবিধানে বিধিবদ্ধ আকারে থাকলেও আদর্শ রাষ্ট্রের নামে বাংলাদেশকে সমালোচিত হতে হয়। এই সমালোচনা নির্মূল হতো, যদি দেশের সর্বোচ্চ আইনের বিধানগুলোর বাস্তবিক প্রয়োগ করা যেত। মুষ্টিমেয় কয়েকটা অনুচ্ছেদ ছাড়া আমাদের সংবিধানের বিধানগুলো যদি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, তবে বাংলাদেশকে আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট- এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান সমালোচিত হওয়ার পেছনে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অনুচ্ছেদ ও সংশোধনীকে দায়ী করা হয়/হচ্ছেও। উক্ত অনুচ্ছেদ ও সংশোধনীগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেশের গণতন্ত্রকে হুমকির মধ্যে ফেলে। উদাহরণস্বরূপ আমরা সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর কথা বলতে পারি, যার মাধ্যমে বাকশাল কায়েম করে রাষ্ট্রপতি শাসিত ও এক দলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা হয়েছিল। উক্ত সংশোধনীর মাধ্যমেই দেশের গণতন্ত্রকে তিরোহিত করা হয়। যদিও ১৯৯১ সালে দ্বাদশ সংশোধনী এনে গণভোটের মাধ্যমে পুনরায় সংসদীয় সরকার ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। আবার পঞ্চম, সপ্তাম সংশোধনীর কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেননা এই দুইটা সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে সামরিক শাসনকে বৈধতা দেওয়া হয়েছিল এবং দেশের সংবিধানকে স্থগিত করা হয়।
এরপর ২০১১ সালে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের আমূল পরিবর্তন করে বহু বিধান সংযোজন/বিয়োজন/প্রতিস্থাপন করা হয়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী সমালোচিত হওয়ার পিছে মূলত নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা(১৯৯৬ সালে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে প্রবর্তিত) বাতিল করে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত করাকে দায়ী করা হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১১ সালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের পর থেকে আজ অবধি(দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন পর্যন্ত) বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া প্রত্যেকটি নির্বাচনই দেশের অধিকাংশ জনগণ কর্তৃক অগ্রহণযোগ্য স্বীকৃত এবং বহির্বিশ্বে বিভিন্নভাবে সমালোচিত হয়েছে।
এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় হতে পারে, এমন এক নির্বাচনকালীন সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেখানে দেশের জনগণ প্রত্যেকটি নির্বাচনকালীন সময়ে যেন- উৎসবমুখর পরিবেশে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। যাহাতে উক্ত নির্বাচনী ফলাফল দেশ-বিদেশে সমালোচিত না হয়ে বরং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়।
বলা বাহুল্য যে, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ থেকে গণভোটের বিধানও বাতিল করে সংসদ সদস্যদের মতামতের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে (দুই-তৃতীয়াংশ) জাতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে এমন বিধান প্রতিস্থাপন করা হয়। কিন্তু সংবিধানের ৭০নং অনুচ্ছেদের কারণে উক্ত বিধান গনতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় প্রশ্নবিদ্ধ রয়ে যায়।
উল্লেখ্য, ৭০নং অনুচ্ছেদে বলা আছে, যদি কোনো ব্যক্তি কোন নির্বাচনে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরুপে মনোনীত হইয়া সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে উক্ত দল হতে পদত্যাগ করেন অথবা দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন তবে উক্ত নির্বাচিত সদস্যের সংসদ আসন শূন্য হইবে। যেটাকে আইনের ভাষায় Floor crossing(ফ্লোর ক্রসিং) বলে।
বিষয়টাকে যদি আরো সহজভাবে বলি, একজন ব্যক্তি কোনো একটা রাজনৈতিক দল(যেমন আওয়ামী লীগ/বিএনপি) থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হলো এবং পরবর্তীতে উক্ত রাজনৈতিক দলের নেতা সংসদে যদি কোনো একটা সুনির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে উদ্ধত হন এবং সেক্ষেত্রে কোনো স্বদলীয় সদস্য যদি সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ভোট দেন তবে উক্ত সদস্যের সংসদীয় আসন শূন্য হয়ে যাবে। এটা সহজে এখন অনুমেয় যে, সবাইকে অগ্রাহ্য করে এই অনুচ্ছেদের সুবিধা নিয়ে টেকনিক্যালি যেকোনো সরকার নিজের সুবিধামত নীতি নির্ধারণ করতে পারবেন, যেটা গণতান্ত্রিক সরকার প্রথায় একটুও কাম্য নয়। যদিও উক্ত অনুচ্ছেদের একটা পজিটিভ দিক আছে যে, যদি ওইরূপ নিয়ম না থাকত তবে স্বদলীয় সংসদ সদস্য যোগসাজশ করে সরকারের বিরুদ্ধে যেকোনো মুহুর্তে যেকোনো বিষয়ের ওপর সংসদে অনাস্থা প্রস্তাব এনে সরকার পতন ঘটাতে পারে।
এরকম ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটতে থাকলে কিছুদিন পরপর দেশের মধ্যে অরাজকতার সৃষ্টি হবে- দেশ অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে। এজন্য দেশের সরকারকে স্থায়ী রুপ দেওয়ার জন্য হলেও ফ্লোর ক্রসিং নীতির প্রয়োজন আছে। তবে উক্ত বিধানকে এমনভাবে রাখা প্রয়োজন যাতে দেশের সরকারের স্থায়িত্ব বজায় থাকার পাশাপাশি সংসদে কোনো বিল পাশের ক্ষেত্রেও যেন গনতান্ত্রিক প্রথার প্রতিফলন ঘটানো যায়।
আমরা জানি যে, বাংলাদেশ সংবিধানে ‘সংবিধানের কতিপয় বিধান সংশোধনের অযোগ্য’ শিরোনামে ৭(খ) একটি অনুচ্ছেদ আছে। উক্ত অনুচ্ছেদটি সংবিধানের মৌলিক কাঠামো (Basic structure) অনুচ্ছেদ নামেও পরিচিত। এই অনুচ্ছেদ মূলত সংবিধানের হুটহাট পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করে। আসলে দেশের সর্বোচ্চ আইনের মৌলিকত্ব বজায় রাখতে এবং স্থায়িত্ব রূপ দিতে এমন বিধান খুবই বাস্তবিক। তবে পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় সামগ্রিক স্বার্থে সাংবিধানিক বিধানকে যুগোপযোগী করার পথও যাতে প্রশস্ত থাকে, সেদিকেও খেয়াল রাখা বাঞ্ছনীয়।
আমরা যদি ৭(খ) অনুচ্ছেদের শেষ অংশের দিকে খেয়াল করি, যেখানে বলা হয়েছে ‘.....সহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হইবে’। যদিও এখানে 'অন্যান্য মৌলিক কাঠামো অনুচ্ছেদ' বলতে আর কোন কোন অনুচ্ছেদগুলোকে বোঝাবে সেটা স্পষ্ট করে বলা নেই, যার কারণে বিতর্ক থেকেই যায়।
আবার আমরা যদি সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনীর কথা বলি, যার মাধ্যমে বিচারকদের অপসারণের ক্ষমতা সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিলের পরিবর্তে সংসদের হাতে নেয়া হয়েছিল। উক্ত সংশোধনী আইনটি যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে সংবিধানের ৯৪(৪) এবং ১১৬(ক) অনুচ্ছেদকে প্রভাবিত করবে। যদিও উক্ত সংশোধনী আইনটি সুপ্রিমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক বাতিল হয়ে একই কোর্টের আপিল বিভাগে রিভিউ পর্যায়ে আছে।
আমরা এটাও অবগত যে, সংবিধানের ২২নং অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ থেকে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ রাষ্ট্র' নিশ্চিত করবে। কিন্তু অনুচ্ছেদ ১১৬ অনুসারে অধ্বস্তন আদালতসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বিধান রাষ্ট্রপতির ওপর (যিনি নির্বাহী বিভাগের অংশ) ন্যস্ত আছে, যেটা অনুচ্ছেদ ২২-্এর সাথে সাংঘর্ষিক। একই ভাবে আমরা যদি সংবিধানের ৩৩(৪) অনুচ্ছেদে নিবর্তনমূলক আটক এবং ৩৫(৬) অনুচ্ছেদে বর্ণিত নিরপেক্ষ বিচার আদালতে বিচারের নামে নিষ্ঠুর ও লাঞ্ছনাকর দণ্ডের বিধান লক্ষ্য করি, সেটাও মৌলিক অধিকারের জন্য হুমকিস্বরূপ।
উল্লেখ্য, নিবর্তনমূলক আটকের নামে বর্তমানে আমরা আয়নাঘর নামক লাঞ্ছনাকর পরিবেশের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। এছাড়া আমরা যদি সংবিধানের নবম-ক ভাগের জরুরি অবস্থা ঘোষণা শিরোনামের (১৪১(ক)-১৪১(গ) অনুচ্ছেদগুলো দেখি, তবে বুঝতে পারব যে, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিস্বাক্ষরের ভিত্তিতে দেশের মধ্যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন এবং উক্ত ঘোষণা বলবৎ থাকাবস্থায় জনগণের মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকে, যেটা গনতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার বিকল্পরুপ। যদিও জনস্বার্থে যে কোনো সময় দেশের মধ্যে জরুরি অবস্থা জারির প্রয়োজন পড়তে পারে, তাই বলে সেটা যেন বিতর্কিত না হয়ে যায় সেদিকে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন।
এখানে এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, জরুরি অবস্থা শুধুমাত্র তিনটি পরিস্থিতিতে (যুদ্ধ, বহিরাক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ গোলযোগ) জারি করা যায়। কিন্তু যুদ্ধ ও বহিরাক্রমণ সহজভাবে বুঝতে পারলেও অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বলতে কোনগুলো বোঝাবে সেটার ব্যাখ্যা উক্তরূপ অনুচ্ছেদগুলোতে স্পষ্ট করা হয়নি, যার কারণে যে কোনো সরকার দেশের মধ্যে যে কোনো গোলযোগের অজুহাতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে জনগণের মৌলিক অধিকার হরণ করতে পারে।
উল্লেখ্য, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমেই জরুরি অবস্থা চলমান থাকাবস্থায় জনগণের মৌলিক অধিকারের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। দেশের গনতান্ত্রিক চিন্তাধারাকে মাথায় রেখে সংবিধানের আরো কয়েকটি বিষয় পুনর্বিবেচনার প্রয়োজন। যেমন অনুচ্ছেদ নং ৪৮-্এর কথা বলা যায়- যেখানে রাষ্ট্রপতিকে নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান করে রাখা হয়েছে। আমরা অবগত যে, রাষ্ট্রপতিকে শুধুমাত্র ৫৬(৩) অনুসারে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ও ৯৫(১) অনুসারে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা ব্যতীত সকল কার্য প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে করতে হয়। এমনকি প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে আদৌ কোনো পরামর্শ দিয়েছেন কি-না, সে বিষয়ে কোনো তদন্ত করা যায় না। এমন বিধান রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে মোটেও কাম্য নয়।
এছাড়াও আমরা যদি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ৫০(২) দেখি, যেখানে বলা আছে- একাধিক্রমে হোক বা না হোক, দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতির পদে কোনো ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না। একই রকম নীতি যদি প্রধানমন্ত্রী পদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সংবিধানের ৫৭নং অনুচ্ছেদে গৃহীত হতো, তবে পরোক্ষভাবে হলেও সেটা সরকারের স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করত।
মোদ্দাকথা হলো, সংবিধানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারসাম্য আনা একান্ত প্রয়োজন। অধিকন্তু আমরা অবগত আছি যে, আমাদের সংবিধানে ন্যায়পাল নামে একটি অনুচ্ছেদ (৭৭নং) আছে, যেখানে বলা আছে- ন্যায়পালকে কোন মন্ত্রণালয়ের সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারি কর্তৃপক্ষের যে কোনো কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, সংবিধান প্রণয়নপরবর্তী ৫২ বছরের মধ্যে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো ন্যায়পাল নিয়োগ দেয়া হয়নি। ইতোমধ্যে যদি সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা যেত, তবে সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের তদারকির ব্যবস্থা হতো বৈকি।
মো. আলমগীর হোসেন, শিক্ষার্থী, আইন বিভাগ, বশেমুরবিপ্রবি, গোপালগঞ্জ
এমএসএম / জামান

এমন একটা সরকার চাই

পবিত্র শবে বরাত: হারিয়ে যেতে বসা আত্মার জন্য এক গভীর ডাক : মোহাম্মদ আনোয়ার

ঘুষ, দালাল ও হয়রানি: জনগণের রাষ্ট্রে জনগণই সবচেয়ে অসহায়!

সুস্থ জীবনের স্বার্থে খাদ্যে ভেজাল রোধ জরুরী

আস্থার রাজনীতি না অনিবার্যতা: তারেক রহমান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক শূন্যতা!

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
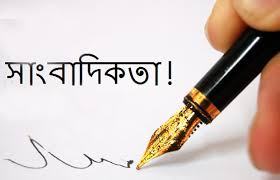
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

