দেশ ও দল পরিচালনায় একই ব্যক্তি নয়

রাষ্ট্র পরিচালনা ও রাজনৈতিক দল পরিচালনা দুটি পৃথক দায়িত্ব। রাষ্ট্র হলো একটি সাংবিধানিক কাঠামো, যার প্রধান লক্ষ্য জনগণের সার্বিক কল্যাণ, উন্নয়ন ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা। অপরদিকে রাজনৈতিক দল হলো একটি মতাদর্শিক সংগঠন, যার উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট নীতি ও কর্মসূচি নিয়ে জনগণের সমর্থন অর্জন করে ক্ষমতায় আসা। এই দুই ক্ষেত্রের উদ্দেশ্য ভিন্ন হলেও, বাংলাদেশসহ অনেক দেশে দেখা যায় এক ব্যক্তি একই সঙ্গে রাষ্ট্রপ্রধান ও দলপ্রধান, সরকারের মন্ত্রী, এমপি ও দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ফলস্বরূপ, দলীয় স্বার্থ অনেক সময় রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে ছাড়িয়ে যায়। এই অবস্থায় প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা হারায়, গণতন্ত্রের চেতনা ক্ষুণ্ন হয়, এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা ধীরে ধীরে দলীয়করণের দিকে ধাবিত হয়।
যে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতার ভারসাম্য একটি অপরিহার্য উপাদান। যদি এক ব্যক্তির হাতে রাজনৈতিক দল ও রাষ্ট্র, দুটির নিয়ন্ত্রণ চলে আসে, তাহলে জবাবদিহিতা কমে যায়। ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ দুর্নীতির জন্ম দেয়, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয় এবং দলীয় সিদ্ধান্তই রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। এর ফলে রাষ্ট্র নাগরিক নয়, বরং দলের অনুগতদের কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। তাই রাষ্ট্র ও দলের নেতৃত্ব আলাদা রাখা কেবল রাজনৈতিক শৃঙ্খলার বিষয় নয়, বরং একটি রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্য অপরিহার্য।
দল ও রাষ্ট্রের কাঠামোগত পার্থক্য:
রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সংবিধান অনুযায়ী। সংবিধান রাষ্ট্রের নীতি, কর্তৃত্ব, নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়। অপরদিকে রাজনৈতিক দল পরিচালিত হয় গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, যা নির্দিষ্ট আদর্শ ও রাজনৈতিক দর্শনের প্রতিফলন। সংবিধান সর্বজনীন; এটি সকল নাগরিকের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু দলের গঠনতন্ত্র কেবল দলের সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য। এখানেই মূল পার্থক্য।
রাষ্ট্রের প্রতিটি প্রতিষ্ঠান যেমন বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ, নির্বাচন কমিশন ইত্যাদি, নিরপেক্ষ ও দলমুক্ত থাকার কথা। তারা কোনো দল নয়, বরং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। অথচ যখন রাষ্ট্রের প্রধান একই সঙ্গে দলপ্রধান হন, তখন এসব প্রতিষ্ঠানের ওপর দলীয় প্রভাব বাড়তে থাকে। দলীয়করণ শুরু হয় প্রশাসনের গভীরে, যেখানে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলির সিদ্ধান্ত দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে নেওয়া হয়, যোগ্যতার ভিত্তিতে নয়। ফলস্বরূপ রাষ্ট্রীয় কাঠামো দুর্বল হয়, দক্ষতা নষ্ট হয় এবং জনগণের আস্থা হারায়।
দলীয় দায়িত্ব ও সরকারি দায়িত্বের ভিন্নতা:
দলের দায়িত্ব হলো জনগণের চাহিদা ও মতামত সংগ্রহ করা, সংগঠনকে শক্তিশালী করা এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গড়ে তোলা। অপরদিকে, সরকারের দায়িত্ব হলো প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, নীতি বাস্তবায়ন করা এবং জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করা। একই ব্যক্তি যখন দুই দায়িত্বে থাকেন, তখন তিনি স্বাভাবিকভাবেই কোনো এক দিকে বেশি মনোযোগ দেন। এতে হয় দলীয় কর্মকাণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়, নয়তো প্রশাসনিক কাজে গাফিলতি আসে।
সরকার পরিচালনায় দরকার পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা, ও কার্যকর বাস্তবায়ন। অন্যদিকে, দল পরিচালনায় প্রয়োজন সাংগঠনিক দক্ষতা, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষমতা। এই দুই ধরনের দক্ষতা এক ব্যক্তির পক্ষে একসঙ্গে প্রয়োগ করা প্রায় অসম্ভব। ফলে উভয় ক্ষেত্রেই কর্মদক্ষতার ঘাটতি দেখা দেয়।
একই ব্যক্তির দ্বৈত ভূমিকার ঝুঁকি:
একই ব্যক্তি যখন রাষ্ট্র ও দলের দায়িত্বে থাকেন, তখন দুটি বড় সমস্যা দেখা দেয়, স্বার্থসংঘাত এবং জবাবদিহিতার অভাব।
দলের নেতা হিসেবে তিনি দলের স্বার্থ রক্ষা করতে চান, আর সরকারের অংশ হিসেবে তাঁর উচিত পুরো জনগণের স্বার্থ দেখা। কিন্তু বাস্তবে দলীয় স্বার্থই প্রাধান্য পায়। যেমন, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, বাজেট বরাদ্দ, উন্নয়ন প্রকল্প, সব কিছু দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে থাকে। এতে সাধারণ নাগরিক, বিশেষ করে বিরোধী মতের মানুষ রাষ্ট্রীয় সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।
তদুপরি, সংসদ ও প্রশাসন কার্যত দলীয় কার্যালয়ের অংশে পরিণত হয়। রাষ্ট্রের সম্পদ ব্যবহৃত হয় দলীয় কর্মকাণ্ডে, যা গণতন্ত্রের মৌলিক ধারণার পরিপন্থী।
আরেকটি বড় সমস্যা হলো “একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ”। একজন ব্যক্তি যখন সবকিছুর কেন্দ্রে থাকেন, তখন পরামর্শ ও সমালোচনার সংস্কৃতি বিলুপ্ত হয়। দলের মধ্যে গণতন্ত্র থাকে না, রাষ্ট্রেও থাকে না। তখন ভুল সিদ্ধান্তে দেশ এগিয়ে যায় না, বরং একনায়কতান্ত্রিক ধারা তৈরি হয়।
একক নেতৃত্বের নেতিবাচক প্রভাব:
একক নেতৃত্বের ফলে দলীয় গণতন্ত্রের মৃত্যু হয়, ভিন্ন মত বা সমালোচনা দলীয় সভায় টিকে না। ফলে নেতৃত্ব একতরফা সিদ্ধান্ত নেয়, এবং নীতি নির্ধারণ হয় প্রশ্নহীনভাবে।
নেতৃত্বে স্থবিরতা:
এক নেতা দীর্ঘদিন ধরে থাকলে নতুন নেতৃত্বের বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। তরুণ প্রজন্ম রাজনীতিতে আগ্রহ হারায়, কারণ তারা দেখে পদবণ্টন নির্ধারিত, যোগ্যতা নয়, আনুগত্যই মুখ্য।
ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ:
একক নেতৃত্ব ধীরে ধীরে প্রশাসনিক ক্ষমতাও নিজের চারপাশে কেন্দ্রীভূত করে। এতে প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল হয়, সংসদ, নির্বাচন কমিশন, এমনকি দলের কমিটিও কাগুজে হয়ে পড়ে।
দলীয় দুর্নীতি বৃদ্ধি:
যখন একজন ব্যক্তির কথাই চূড়ান্ত হয়ে যায়, তখন স্বজনপ্রীতি ও অর্থবাণিজ্য বাড়ে। কেউ জবাবদিহি করতে পারে না, কারণ বিরোধিতা মানে নেতৃত্বের বিরোধিতা।
দলের ভেতরে নেতৃত্ব বিকাশের প্রতিবন্ধকতা:
যখন দলীয় শীর্ষ পদগুলো সরকারি মন্ত্রীদের হাতে থাকে, তখন তরুণ বা নতুন নেতারা নেতৃত্বের সুযোগ পান না। এতে দলটি ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র দুর্বল হয়ে যায়। দলীয় চর্চা কমে গেলে ভবিষ্যতে যোগ্য নেতৃত্বের ঘাটতি তৈরি হয়। তাদের মধ্যে হতাশা জন্ম নেয়, তারা রাজনীতি থেকে সরে যান। ধীরে ধীরে দলটি “ক্ষমতাধরদের ক্লাব” এ পরিণত হয়, যেখানে নীতি নয়, পদই মুখ্য। এই প্রবণতা দীর্ঘমেয়াদে দলকেও দুর্বল করে তোলে, কারণ নতুন প্রজন্ম নেতৃত্বের সুযোগ না পেলে দলটির অস্তিত্বও প্রশ্নের মুখে পড়ে।
ইতিহাসে এর প্রতিফলন:
আমাদের রাজনীতিতে দল ও সরকারের নেতৃত্বের মিশ্রণ এখন সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। দলীয় সাধারণ সম্পাদক বা সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের মন্ত্রী হওয়া প্রায় নিয়মের মতো। এমনকি ইউনিট কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক বা কোন প্রভাবশালী নেতা সরকারের অংশ হয়ে বসে থাকে। স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় সব দলেরই গুরুত্বপূর্ণ পদের নেতারা রাষ্ট্রক্ষমতায় থেকেও দলীয় নেতৃত্ব ধরে রেখেছেন। এতে রাষ্ট্রীয় নীতিতে দলীয় ভাবধারা প্রভাব ফেলেছে, প্রশাসন নিরপেক্ষতা হারিয়েছে, এবং বিরোধী রাজনীতি সংকুচিত হয়েছে। কিন্তু এতে দলীয় কর্মীরা দূরে সরে যান, কারণ তারা মনে করেন সরকারই এখন দল, আর দল মানে কিছু প্রভাবশালী মন্ত্রী। তৃণমূলের অসন্তোষ বাড়ে, মতের অমিল জন্ম নেয়, এবং পরিশেষে দলীয় ঐক্য ভেঙে পড়ে। ফলে সরকারও রাজনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, কারণ দলের ভিত মজবুত না থাকলে প্রশাসনিক শক্তিও টেকে না।
দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোতেও একই দৃশ্য। পাকিস্তানে জুলফিকার আলি ভুট্টো দলপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী উভয় ছিলেন, যার ফলে ক্ষমতার অপব্যবহার বেড়েছিল। শ্রীলঙ্কায় রাজাপাকসে পরিবারের সদস্যরা দল ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পদে থেকে ক্ষমতার ভারসাম্য নষ্ট করেন। এসব উদাহরণ দেখায়, ক্ষমতা এক হাতে কেন্দ্রীভূত হলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ধ্বংস হয় এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে।
দলীয়করণ ও প্রশাসনিক ক্ষতি:
যখন রাষ্ট্রযন্ত্র দলীয়করণে আক্রান্ত হয়, তখন আমলাতন্ত্র আর জনগণের নয়, বরং দলের সেবক হয়ে পড়ে। যোগ্য ও নিষ্ঠাবান কর্মকর্তারা উপেক্ষিত হন, আর আনুগত্যশীলরা পুরস্কৃত হন। এতে কর্মদক্ষতা কমে যায়।
শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইনশৃঙ্খলা, সবক্ষেত্রেই দলীয় প্রভাব পড়ে। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে না।
যেখানে রাষ্ট্রের উচিত যোগ্যতার ভিত্তিতে মানুষকে সুযোগ দেওয়া, সেখানে দেখা যায় “আপনি কোন দলে?” সেটাই হয় মূল প্রশ্ন। এই অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে রাষ্ট্রের মৌলিক নৈতিকতা ভেঙে পড়ে।
নীতিগতভাবে কেন আলাদা থাকা জরুরি:
উন্নত দেশগুলোতে দলীয় ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব আলাদা রাখার নীতি কঠোরভাবে মানা হয়। যুক্তরাজ্যে প্রধানমন্ত্রী দলীয় নেতা হলেও সরকারি কর্মকাণ্ডে সিভিল সার্ভিস সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। কানাডায় সরকার পরিবর্তন হলেও আমলারা একই নিয়মে কাজ করেন; সেখানে কোনো রাজনৈতিক প্রভাব নেই। জাপানে দলীয় নেতৃত্ব পরিবর্তন হলেও প্রশাসনের কাঠামো অপরিবর্তিত থাকে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও প্রেসিডেন্ট দলের হলেও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করে। তাদের মূল বিশ্বাস, দল হলো ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যম, কিন্তু রাষ্ট্র হলো জনগণের সেবা করার প্রতিষ্ঠান।
বাংলাদেশেও এই নীতি প্রয়োগ করা জরুরি। দলীয় প্রধানকে যদি রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব দেওয়া হয়, তবে দলীয় পদটি অন্য কাউকে দিতে হবে, যেন প্রশাসন ও রাজনীতি পৃথকভাবে চলতে পারে।
রাষ্ট্রনেতা ও দলীয় প্রধানের দ্বৈত দায়িত্বে জবাবদিহিতা সংকট:
দলীয় প্রধান হিসেবে একজন নেতা নিজের দলের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি পুরো জাতির কাছে দায়বদ্ধ। যখন এই দুটি ভূমিকা একত্র হয়, তখন কেউই তাঁকে জবাবদিহি করতে পারে না। বিরোধী দল দুর্বল হয়, কারণ সরকার সমালোচনা মানতে চায় না। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হয়, কারণ সমালোচনা মানে দলবিরোধিতা বলে গণ্য হয়। এভাবে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রে একমুখী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।
অন্যদিকে, সংসদে দলীয় শৃঙ্খলার নামে সংসদ সদস্যরা স্বাধীনভাবে মত দিতে পারেন না। ফলে সংসদ কেবল একমত পোষণকারী প্রতিষ্ঠান হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের প্রাণ, অর্থাৎ “বিতর্ক” ও “বিকল্প মত” হারিয়ে যায়।
রাষ্ট্রযন্ত্রের দক্ষতা হ্রাস ও প্রশাসনিক অচলাবস্থা:
দলীয় প্রভাবের কারণে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তগুলো অনেক সময় বাস্তবতা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে নেওয়া হয় না। মন্ত্রীদের অনেক সিদ্ধান্ত দলীয় স্বার্থে নেওয়া হয়। যেমন, উন্নয়ন প্রকল্পে তহবিল বণ্টন, রাস্তা নির্মাণ, স্কুল অনুমোদন, সব কিছুই দলীয় অঞ্চল বা ভোটভিত্তিক এলাকাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এতে জাতীয় উন্নয়ন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। আমলাদের মধ্যে ভয় কাজ করে, “দলের নির্দেশ অমান্য করলে পদ হারাতে পারি।” এই ভয় তাদের নিরপেক্ষ সিদ্ধান্ত নিতে বাধা দেয়। ফলে দুর্নীতি, ঘুষ ও অদক্ষতা বাড়ে। রাষ্ট্রযন্ত্র তখন আর জনগণের সেবক থাকে না, বরং দলীয় স্বার্থরক্ষার যন্ত্রে পরিণত হয়।
আদর্শ নেতৃত্বের চিত্র:
ইতিহাসে এমন বহু রাষ্ট্রনেতা আছেন যারা দল ও রাষ্ট্রকে আলাদা রেখেছেন। নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর দলীয় নেতৃত্ব অন্যকে দিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্র পরিচালনায় নিরপেক্ষতা দরকার। লি কুয়ান ইউও সিঙ্গাপুরে একই নীতি অনুসরণ করেছিলেন, তিনি প্রশাসনে কোনো দলীয় প্রভাব রাখেননি। মালয়েশিয়ার মহাথির মোহাম্মদও দলীয় নেতৃত্ব ছাড়াই প্রশাসনিক সংস্কার চালিয়েছেন। এসব উদাহরণ দেখায়, রাষ্ট্র পরিচালনায় দলীয় প্রভাব কম থাকলে দক্ষতা বাড়ে, উন্নয়ন টেকসই হয়, এবং নাগরিকের আস্থা ফিরে আসে।
বাংলাদেশেও এ ধরনের উদাহরণ তৈরি করা সম্ভব, যদি নেতৃত্ব দলীয় অবস্থান থেকে সরে এসে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে নিরপেক্ষতা বজায় রাখে।
আলাদা নেতৃত্বের সুফল:
দল ও সরকার আলাদা রাখলে উভয়ের কাজের স্পষ্টতা আসে। দল জনগণের দাবি তুলে ধরতে পারে, আর সরকার তা বাস্তবায়নে মনোযোগ দিতে পারে। একজন নেতা যদি কেবল সংগঠনকে শক্তিশালী করতে কাজ করেন, আর আরেকজন প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন, তবে উভয়ের মধ্যেই জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বাড়ে। এছাড়া দল সরকারের ভুলগুলো শনাক্ত করে সংশোধনের সুযোগও পায়, যা একটি কার্যকর গণতন্ত্রের অন্যতম শর্ত।
একক নেতৃত্বের ইতিবাচক দিক:
সত্যি বলতে, একক নেতৃত্বের কিছু সুফলও আছে। প্রথমত, সিদ্ধান্ত গ্রহণে গতি আসে। সংকট মুহূর্তে বিভ্রান্তি কমে যায়। দ্বিতীয়ত, নেতা দলের ঐক্যের প্রতীক হয়ে ওঠেন, যা অনেক সময় বিরোধের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে। তৃতীয়ত, নতুন বা দুর্বল রাজনৈতিক পরিবেশে একটি শক্তিশালী নেতৃত্ব জনগণের আস্থা বাড়ায়।
কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এই সুবিধাগুলো ক্ষণস্থায়ী। কারণ একটি দল যদি কেবল একজন ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল হয়, তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে সংগঠন ভেঙে পড়ে।
সমাধান ও নীতিগত প্রস্তাব:
দলীয় সংবিধানে উল্লেখ থাকা উচিত যে, মন্ত্রীত্ব পাওয়া ব্যক্তি যেন সাংগঠনিক পদ না রাখেন। দলীয় নীতি নির্ধারণে এক্সিকিউটিভ বোর্ড গঠন করা যেতে পারে, যেখানে প্রশাসনিক পদধারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না। দলের সাংগঠনিক নেতৃত্বে তরুণ ও মেধাবী কর্মীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। সংসদ সদস্যদের জন্য দলীয় নির্দেশনা থাকা উচিত, তারা যেন সরকারি দায়িত্বে থাকলে দলীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোট না দেন। সরকার ও দলের কার্যক্রমের মধ্যে নিয়মিত পর্যালোচনামূলক বৈঠক থাকা উচিত, যেখানে উভয় পক্ষের দায়িত্বের সীমা স্পষ্ট থাকবে।
উপসংহার:
রাষ্ট্র ও দল, দুটোই প্রয়োজনীয়, তবে তাদের কাজের ক্ষেত্র আলাদা। দল মানুষকে সংগঠিত করে, রাষ্ট্র তাদের সেবা দেয়। একজন মানুষ যদি একই সঙ্গে দল ও রাষ্ট্রের প্রধান হন, তবে তার সিদ্ধান্ত সবসময় নিরপেক্ষ হতে পারে না। গণতন্ত্রের প্রাণ হলো “বহুমত”; একক নেতৃত্ব সেই বহুমতকে দমন করে। তাই, রাষ্ট্র ও দলের নেতৃত্ব আলাদা করা সময়ের দাবি। এতে প্রশাসন নিরপেক্ষ থাকবে, জনগণ আস্থা পাবে, এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন হবে ভারসাম্যপূর্ণ। একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়তে হলে দলীয় প্রভাবমুক্ত প্রশাসন ও জবাবদিহিতামূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন অপরিহার্য। দল রাষ্ট্রের সিঁড়ি হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র কখনো দলের হাতিয়ার হতে পারে না।
এই মৌলিক সত্য মেনে চললেই সম্ভব হবে সুশাসন, ন্যায়বিচার ও জনগণের প্রকৃত কল্যাণ।
লেখক: কবি, সাংবাদিক ও সভাপতি, রেলওয়ে জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন।
এমএসএম / এমএসএম

পবিত্র শবে বরাত: হারিয়ে যেতে বসা আত্মার জন্য এক গভীর ডাক : মোহাম্মদ আনোয়ার

ঘুষ, দালাল ও হয়রানি: জনগণের রাষ্ট্রে জনগণই সবচেয়ে অসহায়!

সুস্থ জীবনের স্বার্থে খাদ্যে ভেজাল রোধ জরুরী

আস্থার রাজনীতি না অনিবার্যতা: তারেক রহমান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক শূন্যতা!

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
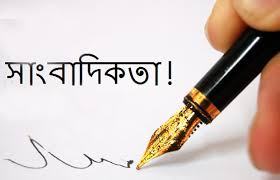
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

অকুতোভয় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা: ২২ বছরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল পরিকল্পনাকারীরা

