বৈষম্য ও দারিদ্র্য কমাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়

বাংলাদেশে দারিদ্র্যতা কমছে না বরং ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। কিন্তু সরকার বলছে দেশে দারিদ্র্যতা কমছে। আবার সাধারণ মানুষ বলছে, আগের মতো দিন চালানোই এখন দায় হয়ে পড়েছে। সমাজে জনগণের এক বিশাল অংশ জীবন-জীবিকার এসব উন্নত উপকরণ ও প্রাচুর্যের খুব সামান্যই ভোগ করার মতো সামর্থ্য রাখে। আদিম মানব সমাজে জীবন সংগ্রামের প্রচণ্ড কষ্ট থাকলেও, সমাজে কোনো ধনী না থাকার কারণে দারিদ্র্যের কোনো উপলদ্ধি সে সময় ছিল না। সেই উপলদ্ধি জন্ম নেয়ার সুযোগ কেবল তখনই সৃষ্টি হয়েছিল যখন সমাজে উদ্ভব ঘটেছিল ধন-বৈষম্য ও শ্রেণি-বৈষম্যের।বাংলাদেশে ধন-বৈষম্য শ্রেণি-বৈষম্য এখন অতি কুৎসিত রূপ ও আকার ধারণ করেছে। জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বাড়লেও, সম্পদের বণ্টন হয়ে পড়েছে প্রচণ্ড ভাবে অসম। ধনী-গরিবের ফারাক কল্পনাতীত পরিমাণে বেড়েছে। উল্লম্বিক সামাজিক স্থানান্তরের সুযোগ প্রায় রুদ্ধ হয়ে পড়েছে। দেশের একেকজন লুটেরা ধনিক বছর-বছর ৯৯ শতাংশ দেশবাসীকে শোষণ-বঞ্চনা-প্রতারণা করে হাজার-হাজার কোটি টাকা কুক্ষিগত করছে। এর প্রধান অংশ তারা বিদেশে পাচার করে দিচ্ছে। তারা পাল্লা দিয়ে বিলাসিতার চোখ ধাঁধানো জৌলুসে লিপ্ত থাকছে। দুঃখজনক হলেও সত্য,বিদেশে ও দেশের মানুষের মাঝে সরকারের মেকি সাফল্যের চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রায়সই ফরমায়সি তথ্য হাজির করা হয়। তাছাড়া দারিদ্র্যের হিসাব কিসের ভিত্তিতে করা হবে তা নিয়েও বিতর্কের শেষ নেই। দারিদ্র্যের সংজ্ঞায়ন এদিক-ওদিক করলেই তার হার উঠিয়ে-নামিয়ে দেখানো যায়। তুলনা করার ভিত্তি-বছর এদিক-ওদিক করার দ্বারাও তা করা যায়। সংখ্যাতত্ত্বের এসব মারপ্যাচ এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোর জরিপের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে দেশ-বিদেশের অধিকাংশ
বিশেষজ্ঞরাই সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন। দেশের বেশিরভাগ মানুষ আজ অভাবের মধ্যে বাস করছে। অভাব বোধই হলো দারিদ্র্যের একটি প্রধান উপসর্গ।
তাছাড়া, সব ধরনের তথ্য একথারই প্রমাণ দেয় যে সমাজে বৈষম্য হু হু করে বাড়ছে। বৈষম্য বাড়লে দারিদ্র্যও বাড়তে বাধ্য। কারণ, দরিদ্র তো বৈষম্যেরই উপজাত! তাই, সবাই যেহেতু একবাক্যে একথা স্বীকার করেন যে দেশে বৈষম্য বাড়ছে, তাই দারিদ্র্য কমছে একথা কতোটুকু সত্য ভেবে দেখার বিষয়। বিশ্বব্যাংকের দেওয়া পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০২৫ সালে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২১.২ শতাংশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে। সমাজের সচেতন নাগরিক পরিসরে এটি এখন বহুল আলোচিত প্রসঙ্গ। কিন্তু যেটি আলোচনায় নেই তা হচ্ছে: দীর্ঘ তিন দশক ধরে ক্রমাগতভাবে কমতে থাকা দারিদ্র্যের হার কভিডকালে এসে থমকে দাঁড়ানোর পর এখন যে তা আবার ধারাবাহিকভাবে বাড়তে শুরু করেছে, সেটি কি তাহলে স্থায়ী প্রবণতায় রূপ নিতে চলেছে, নাকি এটি খুবই সাময়িক? দারিদ্র্যের হার বেড়ে যাওয়ার বিষয়ে এর চেয়েও অধিক করুণ চিত্র উঠে এসেছে পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) পরিচালিত অধিকতর হালনাগাদ এক জরিপেও। ২০২৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দেশের পরিবারগুলোর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি শীর্ষক শেষোক্ত ওই জরিপের ফলাফল জানাচ্ছে যে গত তিন বছরে দেশে দারিদ্র্যের হার ৯.৩ শতাংশ বেড়ে এখন তা ২৮ শতাংশে এসে উপনীত হয়েছে। দারিদ্র্যের হার নির্ধারণ বিষয়ে বিশ্বব্যাংকের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং পিপিআরসির নমুনাভিত্তিক জরিপ-এ দুইয়ের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকার কারণে খুব স্বাভাবিকভাবেই এতদসংক্রান্ত ফলাফলের পরিসংখ্যানে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। তবে এসব পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে পরিদৃষ্ট যৎসামান্য ভিন্নতা সত্ত্বেও এ উভয়বিধ ফলাফল থেকে অভিন্ন যে প্রবণতার চিত্র উঠে এসেছে, তার সারকথা হচ্ছে, দেশে দারিদ্র্যের হার আবার বাড়তে শুরু করেছে। বিষয়টি শুধু যে উদ্বেগজনক তা-ই নয়, রাষ্ট্র, সমাজ ও এর নাগরিকদের জন্য ভয়াবহ এক অশনিসংকেতও। কিন্তু অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে, উক্ত আঘাত মোকাবেলা করে ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে যেসব নীতিগত সহযোগিতা, নগদ প্রণোদনা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়েছে, তার খুব সামান্যই দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যে জুটেছে। বরং সেসবের অধিকাংশই দেশের বিত্তবানদের জন্য সম্পদ অর্জনের নতুন পথ খুলে দিয়েছে।
২০২৪-এর আগস্ট পরিবর্তনের পর রাষ্ট্রীয় পরিসরে সম্পদের লুণ্ঠন প্রক্রিয়া যেহেতু আগের মতোই একই ধারায় অব্যাহত আছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা আগের চেয়েও বেড়ে গেছে।এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ২০২৫ পরবর্তী বছরগুলোতেও কি দারিদ্র্য হারের এ ক্রমবর্ধমানতা একই ধারায় অব্যাহত থাকবে, নাকি কোনোভাবে এর লাগাম টানা সম্ভব হবে? বৈশ্বিক অভিজ্ঞতা বলে, কোনো দেশে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্রমহ্রাসমান ধারা যদি কোনো কারণে মাঝপথে বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে,তারপর পরবর্তী তিন-চার বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে খারাপের দিকেই যেতে থাকে। অর্থাৎ একদিকে ধনিক শ্রেণি কর্তৃক সম্পদের ব্যাপক আয়ত্তকরণ ও অন্যদিকে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের দ্বারা সম্পদের ব্যাপক লুণ্ঠন অব্যাহত থাকার কারণে দেশে উচ্চতর জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার বহাল থাকলেও দারিদ্র্যের হার বাড়তেই থাকবে। উল্লিখিত অবস্থার মধ্যেও দারিদ্র্য হারের ক্রমবর্ধমানতা কিছুটা হলেও ঠেকানো সম্ভব হতো যদি সমাজে সম্পদবৈষম্য কমিয়ে আনা যেত, যার জন্য মূলত দায়ী হচ্ছে রাষ্ট্রের নীতিকাঠামো। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদিসহ বিভিন্ন খাত ঘিরে বর্তমানে রাষ্ট্রের যে নীতিকাঠামো বিদ্যমান রয়েছে, তার প্রায় পুরোটাই হচ্ছে ধনিক শ্রেণির স্বার্থের অনুগামী, বিত্তহীন বা নিম্নবিত্তের সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার সেখানে প্রায় নেই বললেই চলে। আর এর অবধারিত পরিণতি হচ্ছে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ক্রমে সীমাহীন হয়ে পড়া। এরূপ একটি অবস্থা এখন আফ্রিকার কোনো কোনো দেশে বিরাজমান রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশকে কোনো দিন আবার ওইসব দেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় আসতে হবে, এমনটি বোধ হয় এ দেশের সাধারণ নাগরিকদের চিন্তার মধ্যেও ছিল না। অথচ এটাই এখন বাস্তবতা। বাংলাদেশ এই মুহূর্তে ক্রমশই প্রসারমাণ বৈষম্য ও দারিদ্র্যের পথে এগোচ্ছে। এই পরিস্থিতি সচেতন নাগরিকের জন্য উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার।
কিন্তু যাদের চিন্তা ও মননে এ উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা কাজ করলে এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বদলাতে পারত, সেই রাজনীতিকরা তো ব্যস্ত ক্ষমতায় আরোহণের কলাকৌশল নিয়ে। রাজনীতিকরা ক্ষমতায় আরোহণের কলাকৌশল খুঁজবেন, এতে দোষের কিছু নেই। কিন্তু দোষের হচ্ছে, ক্ষমতায় থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিপক্ষে নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা; অথবা ক্ষমতায় আরোহণের আগে জনগণ ও নির্বাচকমণ্ডলীর সামনে পরিস্থিতি মোকাবেলায় তাঁদের কর্মকৌশল কী হবে, তা পরিষ্কার না করা। সমাজের দারিদ্র্যকে কিভাবে কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়, সে লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। যেমন: রাষ্ট্রের বর্তমান বৈষম্যমুখী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাংকিং, রাজস্ব ও আনুষঙ্গিক নীতিকাঠামোকে পুনর্বিন্যাস করে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে, যাতে এর মধ্য দিয়ে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। রাষ্ট্রীয় নীতিমালার অদক্ষ, দুর্বল ও পক্ষপাতিত্বপূর্ণ বাস্তবায়নের কারণে দরিদ্র, নিম্নবিত্ত মানুষ, খুদে ব্যবসায়ী, গ্রামীণ উদ্যোক্তা প্রমুখের জন্য প্রবর্তিত অনেক রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধাই বর্তমানে বিত্তবান শহুরে ও সুবিধাবাদী উদ্যোক্তারা অবলীলায় ভোগ করে যাচ্ছেন, যার মধ্য দিয়ে সম্পদ শোষণ ও বৈষম্য দুই-ই বাড়ছে। আর এর জন্য দায়ী হচ্ছে রাষ্ট্রের ভ্রান্তনীতি, যার প্রণেতারা এর ফলাফল সম্পর্কে আদৌ অবহিত নন। বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের চাপ, দাবি ও তদবিরে এনবিআর যখন-তখনই নানা পণ্যের কর, শুল্ক ইত্যাদি মওকুফ করে দেয়। এর মাধ্যমে একদিকে সরকার রাজস্ব হারিয়ে তা উসুলের জন্য যেমন সাধারণ জনগণের ওপর প্রত্যক্ষ কর আরোপের উদ্দেশ্যে ছুটেন, অন্যদিকে এ প্রক্রিয়ায় বিত্তবানের মুনাফার অঙ্কও ক্রমশই আরো স্ফীত হয়ে ওঠে। দেশ থেকে দারিদ্র্য ও বৈষম্য কমাতে হলে অবিলম্বে এ চর্চা বন্ধ হওয়া উচিত। বাংলাদেশে শোষণ ও বৈষম্য যে কত প্রকট, তার একটি উত্কৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে শিল্পশ্রমিকের মজুরি হার। পৃথিবীর কোনো দেশেই শ্রমিকরা এত অল্প মজুরিতে কাজ করে না। দেশ থেকে দারিদ্র্য কমাতে হলে এই অসহায় দুঃখী দরিদ্র শ্রমিকদের বেতন ব্যাপক হারে বাড়াতে হবে।
কিন্তু এ রাষ্ট্র কখনোই শ্রমিকের পক্ষে দাঁড়ায় না। কারণ তারা হচ্ছে মালিকের মুনাফা ও স্বার্থের সংরক্ষক ও পাহারাদার। এ অবস্থার পরিসমাপ্তি হওয়া জরুরি। সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে বৈষম্য ও দারিদ্র্য কমাতে হলে অবশ্যই জনপ্রশাসনের সেবার মান ও পরিধি বাড়াতে হবে এবং বৈষম্যের বিলোপ সাধনের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের নীতিকাঠামোকে পরিপূর্ণভাবে ঢেলে সাজানো।আর এসব কাজ কিন্ত রাজনীতিকদের করতে হবে। কিন্তু যে রাজনীতি এটি করতে আগ্রহী হবে, সে রাজনৈতিক শক্তির দেখা অতীতে যেমন পাওয়া যায়নি, তেমনি বর্তমানেও তা চোখে পড়ছে না। আর নিকট ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে, সে লক্ষণও অনুপস্থিত। উন্নয়নের যাত্রাকে দ্রুততর করতে হলে শুধু শিল্পায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি বা ‘চুইয়ে পড়া অর্থনৈতিক নীতির’ দিকে লক্ষ্য রাখলেই হবে না, স্বজনতোষী অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হবে। জাতীয় পুঁজির সংবর্ধনে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত রাষ্ট্রের নীতিকাঠামোয় গ্রামের প্রতি যে বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করছে, সেটি থেকেই কৃষকের মধ্যে বর্ধিত হারের এ খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার সৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে, বৈষম্যের মাত্রা কতটা বেড়েছে, এর তথ্যও রয়েছে আয় ও খানা জরিপ প্রতিবেদনে। প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, দেশের মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ এখন দখল করে আছে সমগ্র জাতীয় আয়ের প্রায় ৪১ শতাংশ। রাষ্ট্রীয় নীতি, পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থনে সৃষ্ট এই যে বৈষম্য, দীর্ঘদিন ধরে বিরাজমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, সেটিকে ক্রমান্বয়ে আরো বহুলাংশে বাড়িয়ে তুলেছে এবং এরই প্রতিফলন ঘটেছে রাষ্ট্রীয়প্রতিষ্ঠান বিবিএসের জরিপে। বৈষম্য বৃদ্ধির সুবাদে সর্বাধিক মাত্রায় ও হারে এবং সবচেয়ে আগে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে গ্রামের মানুষ, যারা এখন পর্যন্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ গ্রামীণ মানুষ যদি এরূপ ক্রমবর্ধমান হারে দারিদ্র্য, আয়বৈষম্য ও খাদ্যনিরাপত্তাহীনতার শিকার হতে থাকে, তাহলে প্রকারান্তরে তা দেশের মানুষকে চরম ভোগান্তিতে ফেলে দেবে। আর যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশে বিরাজমান রয়েছে, তা যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে এই ভোগান্তির মাত্রা নিকট ভবিষ্যতে আরো বেড়ে যাবে।
লেখক: গবেষক ও কলাম লেখক, যুক্তরাজ্য
এমএসএম / এমএসএম

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
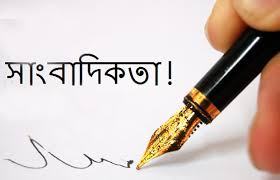
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

অকুতোভয় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা: ২২ বছরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল পরিকল্পনাকারীরা

বিতর্ক থেকে বিবর্তন: তারেক রহমানের রাজনৈতিক রূপান্তর

কুয়েত দূতাবাস সহ মধ্যপ্রাচ্য দূতাবাস গুলো সংস্কার অতি জরুরি

রাজনীতি মানেই কি ক্ষমতার লড়াই?

অধিক আসনের হিসাব না গ্রহণযোগ্য নির্বাচন- তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কোন পথে?

