ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সচেতনতার বিকল্প নেই

ভূমিকম্প একধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর কোনো ভালো দিক নেই। পৃথিবী পৃষ্ঠের ভূমিরূপ পরিবর্তনের আকস্মিক কারণ হচ্ছে ভূমিকম্প। আমরা আজকে পৃথিবীর যে রূপ দেখছি, তা পৃথিবীর পরিবর্তিত রূপ। ভবিষ্যতেও আজকের এই রূপ থাকবে না। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আজকে যেখানে সাহারা মরুভূমি, সেখানটা একসময় সবুজ ঘন অরণ্য দ্বারা আবৃত ছিল। আজকে যেখানে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত মালা হিমালয় অবস্থিত, সেখানে কোটি কোটি বছর পূর্বে টেথিস নামক সাগর ছিল। এই রকম সব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে। আর বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগও আঘাত হানছে। এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে ভূমিকম্প। বিজ্ঞানের এই উৎকর্ষতার সময়ে এসেও ভূমিকম্প হওয়ার কোনো লক্ষ্মণ বা পূর্বাভাস এখন পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব হয়নি। এই কারণে ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতিও বেশি। কোনো একটি অঞ্চলে যখন বড় মাত্রার ভূমিকম্প হয়, তার আগে ছোট আকৃতির ভূকম্পন হতে থাকে একটু পর পর-এটা অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য। যা হোক, বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের দেশ। দক্ষিণে সমুদ্র ও উত্তরে হিমালয় পর্বত অবস্থিত হওয়ায় এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটের গতির কারণে বাংলাদেশে যে কোনো সময় বড় মাপের ভূমিকম্প হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘটিত ভূমিকম্প পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ভূমিকম্পের পূর্বাভাস না থাকায় ক্ষয়ক্ষতি যা হওয়ার হয় যায় এবং তা মেনে না নেওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। উন্নত দেশগুলো উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম হয়তো দ্রুত করতে পারে কিন্তু ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে যায় আগেই। এখন কথা হলো, আমাদের বাংলাদেশ ভূমিকম্প মোকাবিলায় কতটা প্রস্তুত? বাংলাদেশে অনেক দিন থেকেই ছোট আকৃতির ভূমিকম্প হয়ে আসছে।
বিশেষজ্ঞরাও বারবার বলছেন, ‘যে কোনো সময় বাংলাদেশে বড় মাপের ভূমিকম্প হতে পারে।’ এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের প্রধান শহরগুলো এবং শহরে গড়ে উঠা অপরিকল্পিত বাড়িঘর। এতে যে সম্পদ ও জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হবে, তা বলাই বাহুল্য। এর কারণ হলো, পুরোনো বাড়িঘর, অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠা স্থাপনা, বিল্ডিং কোড না মানা, ভূমিকম্প নিরোধক ব্যবস্থা না রাখা, অপ্রশস্ত রাস্তা ইত্যাদি। সম্প্রতি বাংলাদেশে ভূমিকম্পে যে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভূত হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে তা সর্বোচ্চ। ভূমিকম্প হয় টেকটোনিক প্লেটের সংঘর্ষের কারণে। পৃথিবীতে এরকম অনেক প্লেট আছে। বাংলাদেশের উত্তরে আছে ইন্ডিয়ান প্লেট এবং ইউরেশিয়ান প্লেটের সংযোগস্থল। আর পূর্বে বার্মিজ প্লেট ও ইন্ডিয়ান প্লেটের সংযোগস্থল। দুই প্লেটের সংযোগস্থলে প্রচন্ড শক্তি মুখোমুখি অবস্থায় থাকে। সেই শক্তি এতদিন আটকে ছিল। এখন বের হতে শুরু করেছে। ফলে পরবর্তী সময়ে আবার ভূমিকম্প হতে পারে। ঢাকার এত কাছে গত কয়েক দশকে বড় ভূমিকম্প হয়নি। কয়েক প্রজন্ম এবারের মতো ভূমিকম্প দেখেনি। দেশে সাম্প্রতিক সময়ে হালকা ও মাঝারি মাত্রার কয়েকটি ভূমিকম্প হলেও সেগুলো মাত্রার দিক থেকে মৃদু ছিল। তবে গত ৩০০ বছরে কয়েকটি অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকম্প ঘটেছে। সেগুলোর উৎপত্তিস্থল দেশের ভেতরে বা আশপাশের এলাকায় ছিল।টেকনাফ থেকে মিয়ানমার পর্যন্ত প্রায় ৪০০ কিলোমিটার বিস্তৃত ভূ-চ্যুতিতে ১৭৬২ সালে ৮ দশমিক ৫ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়। ওই ভূমিকম্পেই সেন্টমার্টিন দ্বীপ প্রায় তিন মিটার ওপরে উঠে আসে; আগে সেটি ছিল ডুবন্ত দ্বীপ। সেবার সীতাকুণ্ডে পাহাড়ের নিচ থেকে কাদা-বালুর উদ্গিরণ ঘটে, বঙ্গোপসাগরে বিশাল আকারের ঢেউ তৈরি হয়ে বহু ঘরবাড়ি ভেসে যায়, প্রায় ২০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটে। ১৭৮৭ সালের ভূমিকম্প ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথ বদলে দেয়। রিখটার স্কেলে ৭ দশমিক ৫ মাত্রার এ ভূমিকম্প কাচার আর্থকোয়াক নামে পরিচিতি পায়।এর উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেটের খুব কাছে জৈন্তা পাহাড়ের উত্তরাংশে অবস্থিত শিলচরে। সেই ভূমিকম্পে আসামের শিলচর, নওগাং ও মণিপুরের ইম্ফল এলাকায় বহু স্থাপনা ধসে পড়ে। তবে প্রাণহানির সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি।
এ ছাড়া ‘গ্রেট ইন্ডিয়ান আর্থকোয়েক’ নামে পরিচিত এক ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৮ দশমিক ৭। উৎপত্তিস্থল ছিল মেঘালয়ের শিলং অঞ্চল। সেই ভূমিকম্পে দেড় হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়, সিলেটেই প্রাণহানির সংখ্যা ছিল পাঁচ শতাধিক। সিলেটের বহু বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়, ময়মনসিংহ এবং দেশের উত্তরাঞ্চলেও ব্যাপক ক্ষতি হয়। সেইবার বিভিন্ন এলাকায় ফাটল দেখা দেয় এবং সুরমা ও ব্রহ্মপুত্র নদের গতিপথে প্রভাব পড়ে। ১৯১৮ সালে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। এর মাত্রা ছিল রিখটার স্কেলে ৭ দশমিক ৬। উৎপত্তিস্থল ছিল শ্রীমঙ্গলের বালিছড়া। সেই সময় শ্রীমঙ্গল ও ভারতের ত্রিপুরা অঞ্চলে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়। তবে প্রাণহানির সংখ্যা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। চট্টগ্রামে ৬ দশমিক ১ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্পে ২৩ জনের মৃত্যু হয়, তবে ক্ষয়ক্ষতি খুব বেশি হয়নি। মহেশখালীতে পরবর্তী সময়ে ৫ দশমিক ২ মাত্রা ভূমিকম্প হয়। তখন অন্তত ছয়জনের প্রাণহানি হয়।দেশে এখন ঘন ঘন কম মাত্রার যে ভূমিকম্পগুলো হচ্ছে, সেগুলো ৮ দশমিক ২ থেকে ৯ মাত্রার ভূমিকম্প তৈরি হওয়ার মতো যে শক্তি ভূ-ত্বকের মধ্যে জমা হয়ে আছে, এই শক্তিটা বের হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে। বাংলাদেশ কম ভূমিকম্পপ্রবণ দেশ হলেও ঝুঁকির দিক দিয়ে খুব ওপরে রয়েছে। যে পরিমাণ শক্তি ইন্ডিয়ান-বার্মা প্লেটের সংযোগস্থলে জমা হয়ে আছে, সেই শক্তিটা যদি বের হয়, তাহলে বড় মাত্রার ভূমিকম্প হতে পারে। এটি আগামীকালও হতে পারে, আগামী ৫০ বছর পরেও হতে পারে। কখন হবে, সেটি আমরা বলতে পারি না। তবে যেটি হবে, সেটি খুব ব্যাপক হবে। সাবডাকশন জোনের ভূমিকম্পগুলো ভয়ংকর হয়।এখন একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রস্তুতিমূলক মহড়া। ভূমিকম্পের সময় কয়েক কদমের মধ্যে নিরাপদ জায়গায় চলে যাওয়ার প্রশিক্ষণ নিতে হবে। দেশের যে অবকাঠামো তা তো পরিবর্তন করা যাবে না। তাই সচেতনতা ও প্রস্তুতিই ভরসা। দুঃখজনক বিষয় হলেও সত্য, ঢাকা শহরে ২১ লাখ ভবনের কথা বলা হলেও ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের সঠিক পরিসংখ্যান কোনো মন্ত্রণালয়ের হাতে নেই। অবশ্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, ঢাকায় ৭২ হাজার ভবনকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
তা ছাড়া ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করার প্রক্রিয়াও প্রশ্নবিদ্ধ। মূলত ২০১৫ সালে নেপালে ভূমিকম্পের পর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঢাকার ভবনগুলোর ভূমিকম্প ঝুঁকি চিহ্নিত করার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলোকে লাল ও কম ঝুঁকিপূর্ণগুলোকে সবুজ রং দেয়ার কথা বলা হয়েছিল; কিন্তু কয়েকদফা এ বিষয় নিয়ে আলাপ হলেও তা এগোয়নি। আশার কথা হচ্ছে, দেশ স্বাধীন হওয়ার ২২ বছর পর ১৯৯৩ সালে ‘বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড’ প্রণয়ন করা হয়; কিন্তু আইনি জটিলতার কারণে ১৩ বছর পর ২০০৬ সালে এটিকে গেজেট হিসেবে প্রকাশ করা হয়। তবে সময়োপযোগী না হওয়ায় এবং পেশাজীবীদের দাবির মুখে ২০২১ সালে এই কোড সংশোধন করা হয়। ভবন নির্মাণে ন্যূনতম মান নিশ্চিত করাই ছিল এই আইনের লক্ষ্য। অথচ বাংলাদেশে যখন আইনই ঠিকঠাক প্রণয়ন হয়নি সেখানে মানের পরিবর্তন হবে কিসের ভিত্তিতে? এটিই এখন বড় প্রশ্ন! বাংলাদেশে বড় ভূমিকম্প না হওয়ার ফলে আমাদের মধ্যে শিথিলতা কাজ করে এবং সচেতনতাও তৈরি হয়নি। জনগণ, বিশেষজ্ঞ ও সরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ ও সচেতনতার অভাব রয়েছে। সম্প্রতি যেহেতু একটি ভূমিকম্প হয়েছে তাই কিছুটা নড়েচড়ে বসেছে, খোঁজখবর নিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো ভূমিকম্প যেকোনো সময় সংঘটিত হতে পারে। তাই আমাদের প্রস্তুতি সারা বছরই থাকতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মানুষকে ভূমিকম্পের করণীয় সম্পর্কে অবগত করতে হবে। ঢাকা শহরে তেমন কোনো উন্মুক্ত জায়গা নেই। উঁচু অট্টালিকা রয়েছে। মানুষ বাইরে বের হলেও তাদের ওপরই ভবন ধসে পড়তে পারে। যেকোনো উঁচু ভবনের সবচেয়ে দুর্বল জায়গা হচ্ছে সিঁড়ি ও লিফট। ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে ভবন না ভেঙে যেকোনো সময় সিঁড়ি ভেঙে পড়তে পারে। এতে হতাহতের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তাই ঘরই নিরাপদ। এ ধরনের সচেতনতা বাড়াতে হবে। আর যেটা আগেও বলেছি, যেসব ভবন দুর্বল রয়েছে সেগুলো দ্রুত খালি করতে ও ভেঙে ফেলতে হবে।
এবং নতুন ভবন তৈরির ক্ষেত্রে বিল্ডিং কোড যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাহলেই ছোট বা মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে আসবে। তা ছাড়া শুধু বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটার পরপরই সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা সক্রিয় হয়ে ওঠে কেন? তখন তাদের পরিদর্শন, প্রতিশ্রুতি কিংবা আশ্বাস দুর্ঘটনা ঠেকাতে কতটা ভূমিকা রাখে সেটিও এখন খতিয়ে দেখার সময় এসেছে।ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত। তবে অবকাঠামো নির্মাণে ভূমিকম্পের ঝুঁকির বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বিগত দশকগুলোতে বেশ কয়েকটি ছোটখাটো ভূমিকম্প হলেও ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে গুণগতমান নিশ্চিত না হওয়ার বিষয়টি নিয়েও রয়েছে বিতর্ক। প্রকৌশলীরা বলছেন, ঝুঁকি থাকলেও গত দুই দশকে ভবন নির্মাণ-প্রক্রিয়ায় উল্লেখযোগ্য তেমন পরিবর্তন হয়নি। তাই ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা রোধে‘বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড আইন’থাকলেও এর বাস্তবায়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ভূমিকম্প মোকাবিলায় একেবারেই সক্ষম নয়। ভূমিকম্প হলে ঢাকা শহর ধ্বংসস্তূপ ও মৃত্যুর নগরীতে পরিণত হবে। ধারণা করা হয়, ৭ মাত্রার ভূমিকম্প হলেই ঢাকা শহরের প্রায় অর্ধেক বাড়িঘর ধ্বংস হয়ে যাবে এবং ১০ থেকে ২০ লাখ লোকের প্রাণহানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বাদ যাবে না অন্য শহরগুলোও। পুরো দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।সুতরাং, ভূমিকম্প মোকাবিলায় সচেতনতা প্রয়োজন। একমাত্র ঢাকার শহরেই যে পরিমাণ অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা রয়েছে এবং যে পরিমাণে ঝুঁকিপূর্ণ ও পুরোনো বাড়িঘর রয়েছে, তা আগেভাগে সরানো প্রয়োজন। ঢাকা শহরের ভূ-অভ্যন্তরের পানির স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে পানি উত্তোলন বন্ধ করা প্রয়োজন। শহরের রাস্তাগুলো প্রশস্ত হওয়া প্রয়োজন। ভূমিকম্প মোকাবিলায় উদ্ধার কাজে দক্ষ ও চৌকশ বাহিনী গড়ে তোলা প্রয়োজন। এসব করা গেলে হয়তো ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কিছুটা হলেও কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।
লেখক: গবেষক ও কলাম লেখক, লন্ডন থেকে
Aminur / Aminur

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
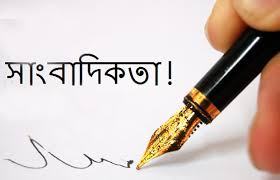
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

অকুতোভয় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা: ২২ বছরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল পরিকল্পনাকারীরা

বিতর্ক থেকে বিবর্তন: তারেক রহমানের রাজনৈতিক রূপান্তর

কুয়েত দূতাবাস সহ মধ্যপ্রাচ্য দূতাবাস গুলো সংস্কার অতি জরুরি

রাজনীতি মানেই কি ক্ষমতার লড়াই?

অধিক আসনের হিসাব না গ্রহণযোগ্য নির্বাচন- তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কোন পথে?

