গণতান্ত্রিক হতে হলে মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখতে হয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য সদর্থক পরিবর্তন আনার বিষয়ে বিস্তর লেখালেখি ও আলোচনা হলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দূরদর্শিতার অভাবকে এর জন্য দায়ী করা যায়। রাজনীতিতে মেধাবী, দক্ষ, সর্বোপরি ভালো মানুষের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে কাঙ্ক্ষিত কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব। ছাত্রজনতার আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র-সংস্কারের যে পটভূমি তৈরি হয়েছে, তা কাজে লাগিয়ে নির্মোহ-সৃষ্টিশীল চিন্তাসমূহের সমন্বয়ে রাষ্ট্র মেরামতের একটি বাস্তবায়ন যোগ্য রূপরেখা প্রণয়নের কাজ চলছে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা, প্রতিবন্ধকতা বিহীন কার্যকর গণতন্ত্র চর্চা এবং জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্র পরিচালনার প্রশ্নে সবাইকে অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়ার কোন বিকল্প নেই। ৩০০ আসনে সরাসরি নির্বাচন বহাল রেখে মিশ্র পদ্ধতির সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পরিবর্তিত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সংখ্যানুপাতিক নির্বাচনের বিষয়টি গুরুত্বসহকারে আলোচিত-পর্যালোচিত হচ্ছে। বিশ্বের অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এ পদ্ধতি বিভিন্ন ফরমেটে প্রচলিত রয়েছে। বেশিরভাগ ভোটারের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করণে এটি একটি কার্যকর পদ্ধতি। আমাদের দেশে বিদ্যমান ৩০০ আসনে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতার পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রেখে, এসব আসনে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে ১০০ জন সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন। আসনসংখ্যার অনুপাতে নারী আসনসংখ্যা বণ্টিত হওয়ার বিদ্যমান পদ্ধতির পরিবর্তে সারাদেশে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে এ বণ্টন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে পারে। এককক্ষ বা দ্বিকক্ষ পার্লামেন্টের বিতর্ক ছাড়াই বর্তমান ব্যবস্থায় ৫০টি আসন বাড়ালেই এর বাস্তবায়ন সম্ভব।
এ ব্যবস্থায় সারাদেশে ১% ভোটপ্রাপ্ত দলেরও সংসদে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা যায়। সদস্য বণ্টনে অর্ধেক নারী সদস্যভুক্তির বিধান করে এই ১০০ আসনের শতকরা ৫০ ভাগ নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা যায়। ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানপরবর্তী একটি গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র গড়ার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে। কল্যাণরাষ্ট্র দান বা করুণার ওপর দাঁড়ায় না। অধিকার কল্যাণরাষ্ট্রের মৌলিক ভিত্তি। রাষ্ট্রকে নাগরিকদের অধিকারভিত্তিক মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা দিতে হয়। খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক চাহিদা সুরক্ষিত হতে হয়। গণতান্ত্রিক হতে হলে মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখতে হয়। যেমন: অর্থনীতিতে সক্রিয় এনজিও ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান অনেক। ৭২৪টি ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান প্রায় ১ লাখ ৫৯ হাজার ৪০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করে। তাদের ৩ কোটি ২০ লাখ ঋণগ্রহীতা রয়েছে। রাষ্ট্রের কল্যাণের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক এনজিও ও ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুধু ঋণ, সেবা ও ত্রাণ বিতরণের প্রচলিত গণ্ডি থেকে বের করে আনা দরকার। এ সংস্থাগুলো সম্পদ ও ব্যাপ্তি বাজারব্যবস্থাকে নতুন রূপ দিতে সক্ষম। তাদের খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, কৃষকের আয় নিশ্চিত করা ও সাশ্রয়ী আবাসন সরবরাহের মতো ব্যবস্থায় নিয়োজিত করা সম্ভব। অবশ্যই নাগরিক সমাজের স্বাধীন কণ্ঠ, জনমত তৈরি, অ্যাডভোকেসি, সংগঠিতকরণ ও জবাবদিহি তৈরির ক্ষেত্র অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। গণতন্ত্রের স্বার্থে নাগরিক সমাজের এ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আরও বেশি করে জারি রাখা জরুরি। খাদ্যপণ্যের আকাশচুম্বী দাম চলমান দীর্ঘস্থায়ী মুদ্রাস্ফীতির একটি বড় কারণ। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে, ২০২৪ সালের জুনে খাদ্যপণ্যের মুদ্রাস্ফীতি ১৪ শতাংশ ছিল, যা এক দশকের মধ্যে সর্বোচ্চ। গৃহস্থালি আয় ও ব্যয় জরিপে দেখা যাচ্ছে, খাদ্য এখনো পরিবারের ব্যয়ের সবচেয়ে বড় অংশ ৪৫ দশমিক ৭৬ শতাংশ।
কিন্তু ভোক্তারা যে দাম দেয়, তার সামান্য অংশই কৃষকেরা পায়।মধ্যস্বত্বভোগীরাই মুনাফা লুটে নেয়। তারাই পণ্য সংরক্ষণ, পরিবহন ও পাইকারি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে। সম্মিলিত মালিকানার মাধ্যমে পণ্যের দাম সাশ্রয়ী রাখা যায়। একইভাবে ভারতের আমুল দুগ্ধ সমবায় সংস্থা গ্রামের ছোট দুধ উৎপাদনকারীদের একত্র করে শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত করেছে। গ্রাম পর্যায়ে সংগ্রহব্যবস্থা, প্রক্রিয়াকরণ অবকাঠামো ও সরাসরি খুচরা বিপণন চ্যানেল তৈরির মাধ্যমে এটি সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো চাল, সবজি, ডালের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের জন্য এ ত্রিপক্ষীয় মডেল তথা উৎপাদক সংগঠন, সমন্বিত সরবরাহব্যবস্থা ও নিজস্ব ব্র্যান্ডের খুচরা বিপণনব্যবস্থা নিয়ে কাজ করতে পারে। এসবের বাস্তবে রূপ দিতে হলে যে কাজগুলো করতে হবে, তা হচ্ছে; এনজিওগুলো ছোট কৃষকদের একত্র করে আইনিভাবে স্বীকৃত কৃষক উৎপাদক সংগঠন তৈরি করতে পারে। কৃষকেরা সম্মিলিত দর-কষাকষির ক্ষমতা পাবেন। সমন্বিত হিমঘর ও পরিবহন নেটওয়ার্কে বিনিয়োগ করলে কৃষকের প্রাপ্তি বাড়বে। এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এসক্রো অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সরাসরি উৎপাদকের সঙ্গে ক্রেতাদের সংযোগ ঘটানো সম্ভব। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে সুরক্ষাব্যবস্থা অপরিহার্য। উৎপাদক ও ভোক্তাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে নির্বাচিত পরিচালনা পর্ষদ থাকতে হবে। এ ছাড়া নিয়মিত নিরীক্ষা, স্বচ্ছ সংগ্রহ ও মূল্য নির্ধারণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। এনজিও পরিচালিত বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি সরকারি তদারকি কমিশন গঠন করা যেতে পারে। অর্থ মন্ত্রণালয়, ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রক সংস্থা, নাগরিক সমাজ ও উৎপাদকের প্রতিনিধিরা থাকবেন।
দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় কারিগরি সহায়তা ব্যবহার করে শাসনব্যবস্থা-সম্পর্কিত স্ট্যান্ডার্ডগুলো প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।সর্বাত্মক সমাজভিত্তিক অংশীদারত্ব পরিবর্তনগুলো কেবল মূল্যস্ফীতি ও বাসস্থানের ব্যয় কমাবে না; বরং অর্থনৈতিক সুযোগকে গণতান্ত্রিক করবে ও কল্যাণরাষ্ট্রের এজেন্ডাকে এগিয়ে নেবে। পাশাপাশি মূল্য স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে। ভবিষ্যৎ পথচলায় কেবল টেকনোক্রেটিক সমাধান যথেষ্ট নয়। সামাজিক চুক্তি ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নতুনভাবে ভাবতে হবে।এনজিওনিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান গুলোকে সম্মিলিত দর-কষাকষি, ন্যায্যমূল্য নির্ধারণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের অংশীদারে রূপান্তরিত করলে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে। গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্রের পথ আপনা-আপনি তৈরি হবে না। সর্বাত্মক সমাজভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে সাহসী অংশীদারত্বমূলক সহযোগিতাই পাথেয়। একটি দেশের রাজনীতির উপর সে-দেশের ভালোমন্দ অনেকাংশে নির্ভর করে। সৎ-যোগ্যদের রাজনীতিতে আসতে হবে; ভালোরা রাজনীতি থেকে দূরে থাকলে তা ক্রমশ অযোগ্যদের দখলে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। রাজনৈতিক সংস্কারের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে একটি গ্রহণীয় রাজনৈতিক বন্দোবস্ত প্রতিষ্ঠিত হোক। রাষ্ট্র মেরামত বা রাজনৈতিক সংস্কারের পরিবেশ সবসময় পাওয়া যায় না বা তৈরি হয় না। জুলাই বিপ্লবের প্রত্যাশানুযায়ী বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে যেসব ভাবনা ইতোমধ্যে সকলমহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে সেগুলোকে আইনি ভিত্তি দিয়ে দ্রুত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী না হওয়া, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ে একধরনের ঐকমত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে।
এছাড়া শতকরা ৫১ ভাগ ভোটারের উপস্থিতি না থাকলে পুনরায় নির্বাচনের বিধান রাখা, ভোট প্রক্রিয়ায় জড়িতদের পক্ষপাতিত্ব, কারচুপিসহ ভোটাধিকার হরণের যে-কোনো কার্যক্রমে সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান রেখে আইন প্রণয়ন করা প্রয়োজন; যাতে নির্বাচন-সংশ্লিষ্ট সবাই নিরপেক্ষভাবে দায়িত্ব পালনে বাধ্য হয়। মানবাধিকার হলো একজন মানুষের সেই অধিকার, যা নিয়ে মানুষ জম্মায়। অর্থাৎ একজন মানবসন্তান জন্মলগ্ন থেকে কিছু অধিকার প্রাকৃতিকভাবেই প্রাপ্ত। যেমন-তার বেঁচে থাকা বা জীবনধারণের অধিকার, বেড়ে ওঠার জন্য খাদ্য ও চিকিৎসাসেবা পাওয়ার অধিকার ইত্যাদি। রাষ্ট্র ও সমাজ তার এসব অধিকার মেনে নিতে বাধ্য। এসব অধিকার হরণ করলে একজন ব্যক্তি সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সমাজে জীবন যাপন করতে পারে না। মানুষ হিসেবে তার গর্ব, আত্মসম্মানবোধ ও মানসিক প্রশান্তি থাকে না। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, একজন মানুষ জন্মসূত্রেই পায় নিজের স্বাধীন চিন্তাশক্তি, মত প্রকাশ ও কথা বলার অধিকার ও মানবাধিকার। কিন্তু রাষ্ট্রের একজন নাগরিক এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তাকে তার মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। তখন তার মধ্যে ক্ষোভ ও প্রতিবাদস্পৃহা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে মানুষের মৌলিক অধিকার হলো সেই সব অধিকার, যা বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য, যেমন-খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। বেঁচে থাকার জন্য একজন নাগরিকের এই পাঁচটি অধিকার মৌলিক অধিকারের মধ্যে পড়ে। এগুলোর অভাবে একজন মানুষ স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। সব মৌলিক অধিকারই মানবাধিকার, কিন্তু সব মানবাধিকার মৌলিক অধিকার নয়। কোনো দেশের সংবিধান যে অধিকারগুলো মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেয় কেবল সেই মানবাধিকারগুলো নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হিসেবে পরিগণিত হয়।
বাংলাদেশের মতো গণতন্ত্রকামী জনবহুল দেশের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবে এদেশের উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বহুলাংশে বাধাগ্রস্ত হয়ে আসছে। বহুকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্য আমাদের দেশের উপযোগী কার্যকর মৌলিক ভাবনা ও তার বাস্তবায়ন প্রয়োজন। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পরও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত না থাকায় নির্বাচনি এলাকাসমূহে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকে। সামান্য ভোটে পরাজিত প্রার্থী বা তাঁর সমর্থকদের পক্ষে অনেকসময় জানমাল রক্ষা করা এবং এলাকায় অবস্থান করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই একক দখলদারিত্বের সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ৩০০ সংসদীয় নির্বাচনি আসনের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে যদি আইনগতভাবে একটি অবস্থান ও মর্যাদা দিয়ে শাসন-প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা যায়, তবে তা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও গণতন্ত্রের জন্য এবং ঐ প্রার্থীর সুরক্ষায় বড় ভূমিকা রাখতে পারে। অপরদিকে নিরপেক্ষ ব্যবস্থাপনা ও প্রযুক্তিবিদদের সহযোগিতায় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে গণভোট গ্রহণের কার্যক্রম কিছু জাতীয় সংকট নিরসনে সহায়ক হতে পারে। প্রতিবার নির্বাচনের আগে নির্বাচনকালীন সরকার ও নির্বাচন কমিশন গঠন প্রশ্নে জাতি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সংকট থেকে বের হয়ে আসার জন্য রাজনৈতিক দল ও সংশ্লিষ্টদের নির্মোহ ভাবনা ও তার বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে হয়তো একটি সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব। পরিশেষে বলব, সদর্থক সংস্কারের পথ ধরে কাঙ্ক্ষিত স্থিতিশীল রাষ্ট্র ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাক-এটিই জনগণের একান্ত প্রত্যাশা।
লেখক: গবেষক ও কলাম লেখক
Aminur / Aminur

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
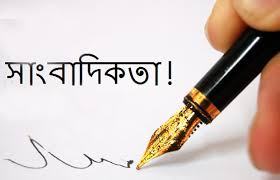
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

অকুতোভয় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা: ২২ বছরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল পরিকল্পনাকারীরা

বিতর্ক থেকে বিবর্তন: তারেক রহমানের রাজনৈতিক রূপান্তর

কুয়েত দূতাবাস সহ মধ্যপ্রাচ্য দূতাবাস গুলো সংস্কার অতি জরুরি

রাজনীতি মানেই কি ক্ষমতার লড়াই?

অধিক আসনের হিসাব না গ্রহণযোগ্য নির্বাচন- তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কোন পথে?

