এক ভয়ংকর সন্ধিক্ষণে বাংলাদেশ

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই রাজনৈতিক বেড়াজালে আটকে বার বার হোঁচট খাচ্ছে বাংলাদেশ। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মতবিরোধ, ক্ষমতার লোভ ও ক্যুসহ নানান ধরণের আন্দোলন সংগ্রামে বার বার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে বাংলাদেশ। গত বছরে সর্বস্তরের ছাত্র-জনতার অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। সরকারি চাকরিতে কোটা নিয়ে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন শুরু হলেও গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ কর্তৃত্ববাদী শাসনের পতন ঘটে। এখন প্রশ্ন হলো, এই অভ্যুত্থান আমাদের কী বার্তা দিয়ে গেল? এই অভ্যুত্থানের প্রধান বার্তা হলো, জুলুম, নির্যাতন ও বৈষম্যমুক্ত সমাজ নির্মাণের জন্য গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ তৈরি করা। কিন্তু গণতন্ত্রে উত্তরণ কীভাবে নিশ্চিত করা যাবে? এখানেই টেকসই রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনা প্রয়োজন। এরই মধ্যে নির্বাচন কমিশন ৭৩টি পর্যবেক্ষক সংস্থাকে প্রাথমিকভাবে নিবন্ধিত করার ঘোষণা দিয়েছে। এই বিষয়ে মোটামুটি ধারণা করা যায় যে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের যে কাঠামো গড়ে তোলার প্রচেষ্টা দেখা যাচ্ছে কিংবা কমিশন যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে বাইরে থেকে মনে করা হচ্ছে যে নিরপেক্ষ নজরদারির পথ তৈরির চেষ্টা চলছে। তবে পর্যবেক্ষক নিবন্ধন এ কথা নিশ্চিত করে না যে পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবে স্বচ্ছ ও স্বাধীন হবে; তা মূলত কার্যকারিতার ওপর নির্ভর করে। এই নিবন্ধনের প্রসঙ্গে দেওয়া সময়সীমা, আপত্তি-উত্তরণের প্রক্রিয়া ও সমন্বয়ের মেকানিজম- এসবই এখন মূল প্রশ্ন। আমাদের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে নষ্ট নির্বাচন কেবল মানদণ্ডের সমস্যা নয়, এটি একটি ব্যাধি। বর্তমান নির্বাচন কমিশনারদের বক্তব্য থেকেই আমরা পেয়ে থাকি যে বাংলাদেশে নব্বই-পরবর্তী সব রাজনৈতিক দলের কমিটমেন্ট থাকলেও বিভিন্ন ভাবেই বিগত সময়ের বেশ কিছু নির্বাচনের ফলাফলে জন-আস্থা সংকটে পড়েছে। যদি জনগণ মনে করে, নির্বাচনের ফলাফল আগেই নির্ধারিত, দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ এবং অংশগ্রহণ নিরাপদ নয়, তাহলে ভোটকেন্দ্রে জনগণের উপস্থিতি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে হবে না।
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া তখনো জীবিত থাকে, যতক্ষণ মানুষ সেটিতে অংশ নেওয়ার জন্য আত্মবিশ্বাস বোধ করে; আর আত্মবিশ্বাস ভাঙলে গণতন্ত্রই ভেঙে পড়ে। এখানে একটি মৌলিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতাও আছে। আর সেটি হলো জনপ্রত্যাশাকে মূল্য দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক উদ্বেগ, মূল্যস্ফীতি, মৌলিক সেবা পাওয়ার অনিশ্চয়তা-এসব যখন বাড়ে, তখন রাজনৈতিক আস্থাহীনতা গভীর হয়। জাতীয় নির্বাচন যতই সন্নিকটে আসছে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক আকাশে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ ততই ঘনীভূত হচ্ছে। সরকারের উপদেষ্টাদের কয়েকজন সেফ এক্সিট খুঁজছেন বলে মন্তব্য করেছেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। পক্ষে-বিপক্ষে এই আলোচনা এখন টক অব দ্য কান্ট্রি। যদি তা সত্যি হয়, অন্যায় কাজের সঙ্গে তাদের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে নিশ্চয়ই? এমনটা হলে এক্সিট খোঁজা স্বাভাবিক। অথচ ৮ আগস্ট ২০২৪ সালে এই ক্যাবিনেটের প্রতি আস্থা রেখেছিল বাংলাদেশের জনগণ, অভ্যুত্থান- কারী ছাত্র-জনতা। এক্সিটের মূল কারণ শুধু কি দুর্নীতি! সম্ভবত এখানে অন্য অনেক কারণ বিরাজমান। জুলাই সনদের স্বাক্ষর বাস্তবায়ন, পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন এবং পিআর প্রসঙ্গে গণভোটের কাঠামো তৈরির উদ্যোগই মূলত নির্বাচনকে ঝুঁকিতে ফেলার আশঙ্কা তৈরি করছে।যদিও বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক্সিট নতুন কিছু নয়। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকারীরা বিদেশের মাটিতে এক্সিট নিয়েছিল। সম্ভবত সেটিই ছিল প্রথম বড় রাজনৈতিক এক্সিট, যেখানে দায়বদ্ধতার বদলে দেখা গিয়েছিল দায় এড়ানোর সংস্কৃতি। ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের হত্যার পরও অনেকে সামরিক ও রাজনৈতিক বলয়ে নিরাপদ ছিল। ২০০৮ সালের পর ফখরুদ্দীন ও মইন ইউ আহমেদের নেতৃত্বাধীন সরকারও নির্বাচন সম্পন্ন করেই এক্সিট নেয় তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে, যেন তাদের ভূমিকার কোনো দায়ই ছিল না।সম্প্রতি শেখ হাসিনাও জুলাই আন্দোলনের মুখে সামরিক প্রহরায় এক্সিট নিয়েছেন। এসব আদতে রাজনৈতিক ব্যর্থতার মুখে নৈতিক পশ্চাদপসরণ ছাড়া কিছু নয়।
বিপরীতে, তারেক রহমানের ক্ষেত্রে ইতিহাস ভিন্ন কথা বলে, এই এক্সিটটি মূলত ছিল চিকিৎসা নেওয়া ছাড়াও অনিচ্ছায় রাজনৈতিক নির্বাসন। পরবর্তী সময়ে সেই তারেক রহমান মঞ্চে ফিরে বাংলাদেশ ও বিএনপির রাজনীতিকে নতুন পথে দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর এই প্রত্যাবর্তন যেন দায় গ্রহণের নতুন এক ইতিহাস।বর্তমান উপদেষ্টাদের অবস্থানও কি সেই ধারার পুনরাবৃত্তি ঘটাতে যাচ্ছে। উপদেষ্টাদের প্রধান দায়িত্ব ছিল জুলাই সনদের স্বাক্ষর বাস্তবায়ন, যেখানে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল জনগণের অংশগ্রহণমূলক শাসন, দায়বদ্ধ প্রশাসন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যাচ্ছে, বাস্তবায়নের ইচ্ছার চেয়ে ভয়ই তাঁদের বেশি গ্রাস করছে। শুধু দুর্নীতি নয়, নির্বাচন পদ্ধতি, প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়ন নিয়েও ভয়। পিআর পদ্ধতিতে সংসদের আসন ভাগ হবে প্রতিটি দলের প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে। অর্থাৎ কোনো একক দল বা জোট পুরো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারবে না। পিআর পদ্ধতিতে বড় দলগুলোর আধিপত্য ভেঙে যায়, ছোট দল ও বিকল্প নেতৃত্বের জন্য খুলে যায় নতুন দরজা। ফলে পিআর মানে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, এমনকি অস্তিত্ব সংকটও, আদতে এই পদ্ধতি হঠাৎ করে সংকটই তৈরি করবে। বাংলাদেশ এই মুহূর্তে আরেকটি সরকার পতনের ধকল সহ্য করতে পারবে না। সেই আশঙ্কা থেকেই কেউ কেউ চাইছেন পুরনো পদ্ধতিতে নির্বাচনব্যবস্থার বাস্তবায়ন। তাই বর্তমান এক্সিটপ্রবণতা কেবল প্রশাসনিক ক্লান্তি নয়, বরং রাজনৈতিক অস্থিরতা ও ভীতির প্রকাশও। এদিকে জুলাই সনদের প্রতিশ্রুতি- গুলো এখনো প্রশ্নবিদ্ধ অবস্থায়। এই সনদ জনগণের অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্রচিন্তার এক ঐতিহাসিক দলিল। রাষ্ট্র হবে জনগণের কাছে জবাবদিহিমূলক; কোনো সরকার বা প্রশাসন ক্ষমতার একচ্ছত্র মালিক নয়। আজ সেই অঙ্গীকারই ঝুলে আছে প্রশাসনিক কাগজে। সনদ বাস্তবায়নের পথে দাঁড়িয়ে আছে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বিদেশি প্রভাব আর রাজনৈতিক গোষ্ঠীর কৌশল। অথচ জনগণ অপেক্ষা করছে, কবে তারা সত্যিকার অর্থে নিজের হাতে রাষ্ট্রের মালিকানা ফিরে পাবে। পিআর বাস্তবায়নের আগে গণভোট আয়োজনের উদ্যোগ এসেছে নতুনভাবে।
নির্বাচনের আগে আরেকটি নির্বাচন, যেন নতুন সংকট ঘনীভূত! এর আগে বাংলাদেশের ইতিহাসে গণভোট হয়েছে; যার একটি হচ্ছিল উনিশ শো সাতাত্তর সালে, আর অন্যটি ছিল উনিশ শো পঁচাশি সালে। যদিও আগের গণভোটের সঙ্গে বর্তমান গণভোটে অমিল অনেক। দীর্ঘ চার দশক পর আবারও যখন গণভোটের আলাপ উঠছে, তখন তা কেবল পিআর পদ্ধতির বৈধতা নয়, রাষ্ট্রচিন্তার দিকনির্দেশনা, শক্তি, হিম্মত জানানোর সক্ষমতাও। ব্যর্থ হলে অনুমিত আগামী দিনের জন্য পিআর পদ্ধতি চিরতরে কবরে শায়িত হবে, সেই সঙ্গে রাষ্ট্র পড়বে গভীর সংকটে। এ জন্য দায়ী থাকবে অতি উত্সুক ও পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চাওয়া দলটিই। গণভোট মানে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ। কিন্তু ইতিহাস বলে, গণভোট যতটা গণতান্ত্রিক সম্ভাবনা তৈরি করে, ততটাই সহজে তা রাজনৈতিক প্রহসনেও পরিণত হতে পারে। তাই আসন্ন গণভোটের সাফল্য নির্ভর করবে মূলত জনগণের চাহিদা ও আস্থার ওপর। এটি সত্যিকার অর্থে জনগণের মতামত প্রতিফলিত করলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে; বিপরীতে যদি ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের হাতিয়ার হয়, তাহলে এক্সিটের ধারাবাহিকতা আবারও ফিরে আসবে। আজকের বাংলাদেশ এক ভয়ংকর সন্ধিক্ষণে।উপদেষ্টারা চাইলে এখনই ইতিহাসের দায় নিতে পারেন। যৌক্তিক ও কাঙ্ক্ষিত জুলাই সনদের বাস্তবায়ন, গণভোটের মাধ্যমে জনগণের মতামত গ্রহণ, পিআর পদ্ধতি নির্বাচিত সরকারের অধীনে পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা হবে, বাস্তবায়নের এই আশ্বাস। নয়তো রিস্কি সময়ে রিস্কি এক্সপেরিমেন্টের অর্থ রাষ্ট্রকে বাঘের মুখে ফেলা।
আবার উপদেষ্টারা যদি সেফ এক্সিট বেছে নেন, তাহলে ইতিহাস তাঁদেরও সেই একই অন্ধকার অধ্যায়ে লিখে রাখবে, যেখানে দায়ের চেয়ে ভয়, নৈতিকতার চেয়ে স্বার্থই বড় হয়ে দাঁড়ায়। জুলাই সনদ বলতে চায়, রাষ্ট্রের মালিক জনগণ, প্রশাসন তাদের প্রতিনিধি।
এখন সময় এসেছে সেই কথাটিকে বাস্তব রূপান্তরের। রাজনৈতিক বড় দলগুলোই যদি কৌশলীভাবে একে অপরকে অন্যায়ভাবে দমনের চেষ্টা করে, তবে দেশের গণতান্ত্রিক ভবিষ্যৎ কুয়াশাচ্ছন্ন হবে। রাজনৈতিক ঐক্য মানে হিংসার মধ্যে লুকিয়ে রাখা নয়, বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংস্কৃতি যখন সম্মানভিত্তিক হবে, তখনই গণতন্ত্র বিকাশ পাবে। রাজনৈতিক অঙ্গনে যদি বড় দলগুলো একে অপরকে গ্রহণযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখতে না শেখে, ভোট ও তার ফলাফল সব সময় সন্দেহের ডালায় থাকবে। এ কারণে এমন এক কাঠামো বানাতে হবে, যেখানে দলগুলো একে অপরকে নিয়মের মধ্যে মেনে চলতে শেখে। জনগণের প্রত্যাশাকে কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হবে। নির্বাচন শুধু রাজনৈতিক কর্মীদের লড়াই নয়, এটি জনগণের জীবনমান ও কল্যাণের আঙিনায় বিশাল প্রভাব ফেলে। জনগণ যদি প্রত্যাশা হারায় চাকরি, মুদ্রাস্ফীতি, স্বাস্থ্যসেবা কিংবা শিক্ষার মান নিয়ে, তাদের ভোটও এমন কোনো বাস্তব ক্ষমতায় রূপান্তরিত হবে না, যা তাদের জীবন বদলে দেয়।তাই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আর্থ-সামাজিক নীতিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দরকার। দেশের ভবিষ্যৎ আলোতে হাঁটবে, নাকি অন্ধকারে ঢুকবে, তা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ভবিষ্যৎ আলোকিত করতে হলে রাজনৈতিক দল, নির্বাচন কমিশন, পর্যবেক্ষক সংস্থা, সুধীসমাজ এবং সর্বোপরি জনগণ-সবাইকে সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে আসতে হবে। পুরো প্রক্রিয়া জবাবদিহি, স্বচ্ছতার সঙ্গে করতে হবে। এখন সময় কাজের। কারণ এ ক্ষেত্রে ঢালাওভাবে শুধু আশ্বাস নয়, বাস্তব পদক্ষেপই গণতন্ত্রকে বাঁচাবে। সব মিলিয়ে বলা যায়, আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাংলাদেশের জন্য এক বড় পরীক্ষা। এটি শুধু ক্ষমতার লড়াই নয়, বরং দেশের গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রীয় স্থিতিশীলতার জন্য নির্ণায়ক।
লেখক: গবেষক ও কলাম লেখক, যুক্তরাজ্য থেকে
Aminur / Aminur

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
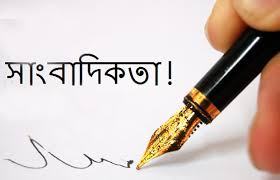
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

অকুতোভয় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা: ২২ বছরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল পরিকল্পনাকারীরা

বিতর্ক থেকে বিবর্তন: তারেক রহমানের রাজনৈতিক রূপান্তর

কুয়েত দূতাবাস সহ মধ্যপ্রাচ্য দূতাবাস গুলো সংস্কার অতি জরুরি

রাজনীতি মানেই কি ক্ষমতার লড়াই?

অধিক আসনের হিসাব না গ্রহণযোগ্য নির্বাচন- তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কোন পথে?

