জবাবদিহিতা নিশ্চিত হলে ফিরে আসবে শান্তি-শৃঙ্খলা

স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ সীমিত সম্পদ নিয়ে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করেছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অনেকটাই বেড়েছে। মাথাপিছু আয়ও ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে। দারিদ্র্যের হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বাংলা দেশের সক্ষমতা বিশ্বের সেরাদের সমতুল্য। খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে চলেছে দেশ। কিন্তু উন্নয়নের সুফল সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছেনি। স্বাধীনতার ৫২ বছর পার করে বাংলাদেশের অর্থনীতি এখন ঘুরে দাঁড়িয়েছে এটা বলাই যায়। ১৯৭১ সালের যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থা থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অনেকগুলো সূচকে বাংলাদেশের বড় ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। স্বাধীনতার প্রথম কয়েক বছর লেগে গেছে অর্থনীতি ঠিক করতে। এরপর যেভাবে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে, সেটা খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক। এখন পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের কোনো তুলনা চলে না। কারণ, দু-একটা বাদে প্রায় সব অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকেই পাকিস্তানের থেকে আমরা অনেক ভালো করেছি। আমাদের তুলনা হতে পারে ভারত, শ্রীলঙ্কা বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য কোনো দেশের সঙ্গে।তাছাড়া দীর্ঘমেয়াদি যেসব উন্নয়ন পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে, সেগুলো যথেষ্ট মানসম্পন্ন। এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে কোন বিষয়গুলোকে আমরা বেশি গুরুত্ব দেব। সরকারি খাতের বিনিয়োগ বা উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বেসরকারি খাতকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। যেকোনোভাবে টাকা খরচই যেন সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যাতে মূল লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। বছর শেষে প্রকল্পের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের কাজে জোর দিতে হবে। একটি প্রকল্প বাস্তবায়নে যদি ভালো ফল পাওয়া যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে আরও পুরস্কৃত করা যেতে পারে। একইভাবে কোনো প্রকল্প যদি ভালোভাবে কাজ না করে, তাহলে সেটা কেন ভালো করল না, সেই জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে এর সুফল বেসরকারি খাতও পাবে।
বিশ্বব্যাংকের সহজে ব্যবসা করার সূচকে বাংলাদেশের পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও কালক্ষেপণ। এটা কর আদায় ব্যবস্থাপনায় আরও বেশি দেখা যায়। কর দেওয়ার বিষয়টিও বাংলাদেশে সাধারণ মানুষের জন্য খুব সহজবোধ্য নয়। কর কর্মকর্তাদের কর আদায়ে যতটা দক্ষতা ও সততা থাকা দরকার, সেটারও ঘাটতি আছে। সাধারণ মানুষকে হয়রানি করারও একটা প্রবণতা কর কর্মকর্তাদের রয়েছে। প্রতিটি আর্থিক লেনদেনকে যদি ব্যাংক হিসাব ও টিআইএনের সঙ্গে যুক্ত করা যায়, তাহলে কর আদায় অনেকটা সহজ করা সম্ভব। কর বাড়ানোর বিষয়টি এমনভাবে করতে হবে, যাতে তা করদাতাদের জন্য বাড়তি বোঝা মনে না হয়। পণ্য আমদানির উৎস হিসেবে এক সময় বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের প্রথম পছন্দের দেশ ছিল ভারত, তবে এক যুগ আগেই তা পাল্টে গেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে চীনা পণ্যের যে দাপট চলছে বাংলাদেশের বাজারে, এখনো তা বজায় আছে। অর্থাৎ পণ্য আমদানিতে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের প্রথম পছন্দের দেশ চীন।আর ভারত এখন দ্বিতীয় পছন্দের দেশ। আমদানিনির্ভর দেশ হিসেবে বাংলাদেশের মোট আমদানি ব্যয়ের বড় অংশ ব্যয় হয় জ্বালানি তেল, ভোজ্যতেল, গম, সার, কাঁচা তুলা, সুতা, মূলধনী যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পন্য কেনার ক্ষেত্রে। যেসব দেশ থেকে এসব পণ্যের বড় অংশ আমদানি করা হয়,সেই তালিকায় শীর্ষ ১০ দেশ হচ্ছে চীন, ভারত, সিঙ্গাপুর, জাপান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, হংকং, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া ব্রাজিল, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকেও অনেক পণ্য আমদানি হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০২৩ অনুযায়ী, বাংলাদেশ প্রধানত প্রাথমিক পণ্য, শিল্পজাত পণ্য ও মূলধনী যন্ত্রপাতি-এ তিন শ্রেণিতে বেশি পণ্য আমদানি করে। প্রাথমিক পণ্যের মধ্যে রয়েছে চাল, গম, তৈলবীজ, অপরিশোধিত জ্বালানি তেল ও কাঁচা তুলা।
আর শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভোজ্য তেল, জ্বালানি তেল, সার, ক্লিংকার, স্টেপল ফাইবার ও সুতা।ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির তথ্য মতে, ভারত থেকে বাংলাদেশ মূলত খাদ্যপণ্য আমদানি করে আসছিল। মাঝে খাদ্যপণ্যের কিছু ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এসেছে। ফলে এসব পণ্যের আমদানি নির্ভরতা অনেকটাই কমেছে। আর এটা খুব স্বাভাবিক যে চীন এখন বাংলাদেশের প্রধান আমদানি উৎস হবে। কারণ, ১৫ থেকে ২০ বছরের মধ্যেই দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত হয়েছে।শিল্পের যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের জন্য চীনের বিকল্প এ সময় কেউ হতে পারে না।কোভিড- ১৯ মহামারি শুরু হলে এর প্রভাবে উভয় দেশ থেকেই পণ্য আমদানি আগের অর্থবছরের তুলনায় কমে যায়। যেমন ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভারত থেকে আমদানি করা পণ্যের মূল্য ছিল ৬৬৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার, অন্যদিকে চীন থেকে আমদানি হয় ১ হাজার ৪৩৬ ডলারের পণ্য। আগের অর্থবছরের তুলনায় ভারত থেকে এ অর্থবছরে আমদানি কমে ১৫৮ কোটি ডলার ও চীন থেকে ২৯০ কোটি ডলার। তবে কোভিড একটু দুর্বল হয়ে এলে উভয় দেশ থেকেই ব্যাপকভাবে বাড়ে দেশের পণ্য আমদানি। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভারত থেকে আমদানি হয় ১ হাজার ৫১৮ কোটি ডলারের পণ্য। ওই বছর চীন থেকে আমদানি হয় ২ হাজার ৪২৫ কোটি ডলারের পণ্য। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশের মোট আমদানি দাঁড়ায় ৮ হাজার ৯১৬ কোটি ডলারে। অথচ ঠিক আগের অর্থবছরে মোট আমদানি হয়েছিল ৬ হাজার ৫৫৯ কোটি ডলারের পণ্য। বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) তথ্য মতে, বাংলাদেশ এক সময় মূলধনী যন্ত্রপাতি বেশি আনত জার্মানি, যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া-এসব দেশ থেকে। অর্থনীতির বৈচিত্র্যের অংশ হিসেবে চীন যখন প্রতিযোগিতামূলক দামে বিভিন্ন মানের পণ্য উৎপাদনের দিকে গেল এবং প্রায় একই সময়ে বাংলাদেশের শিল্পায়নেও গতি এল, তখন সংগত কারণেই চীন থেকে বাংলাদেশের আমদানি বেড়ে গেল।
দেশে ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদবৈষম্যের কারণে সবাই সমানভাবে উন্নয়নের সুফল পায়নি। আরেকটি সমস্যা হলো অর্থনৈতিক কার্যক্রম ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো বড় শহরে কেন্দ্রীভূত থাকা। ফলে গ্রাম-শহরের ব্যবধান এবং নগর দারিদ্র্য বেড়েছে।আইসিসিবির প্রতিবেদনের ভাষ্যমতে, বাংলাদেশের জন্য এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো প্রবৃদ্ধি ও বিকাশের ফল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো। সাম্প্রতিক এক গবেষণার সূত্রে আইসিসিবির নির্বাহী বোর্ডের প্রতিবেদনে বলা হয়, কোভিড-১৯ সময়ে বাংলাদেশে ৯৬ শতাংশ মাইক্রো, ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তা (এমএসএমই) আয় হারিয়েছেন। দেশের ৮২ শতাংশ এমএসএমই জাতীয় ছুটির দিন গুলোতে ব্যবসায়িকভাবে মাঝারি মাত্রায় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং গড়ে ৬৭ শতাংশ ভোক্তা কমেছে তাদের। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় বেশির ভাগ অর্থনীতির তুলনায় বাংলাদেশ ভালোভাবে মহামারি মোকাবিলা করেছে। বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দীর্ঘমেয়াদি কাঠামোগত চ্যালেঞ্জের সমাধান করোনা পরবর্তী পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে পারে। সংস্কারের অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে আছে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, আর্থিক খাত গভীর করা, নগরায়ণের উন্নতি ও জনপ্রশাসন শক্তিশালীকরণ। আইসিসি বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাস ও সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়ন ও গণতন্ত্রকে দারিদ্র্যবান্ধব এবং জনগণের ক্ষমতায়নের হাতিয়ার করতে হলে দুর্নীতিবিরোধী যুদ্ধকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। অন্যদিকে সন্ত্রাস তথা গুম, খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনী গুলোর অন্যায়-অবৈধ কাজ এবং জুলুম-নির্যাতনকে দৃঢ় হাতে দমন করতে হবে। সরকারি দলের নাম ভাঙিয়ে সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজি জনজীবনে এক বড় অভিশাপ। বিশেষ করে খুন-সন্ত্রাস খোদ প্রধানমন্ত্রীর আদেশ-নির্দেশ সত্ত্বেও অব্যাহত রয়েছে।অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে বিবরণ শুরুতে আছে, তা সত্য এবং প্রশংসনীয়।
কিন্তু মানুষ চায় উন্নয়নের সুফল সবাই যেন পায়। সেটা সমান না হোক, অন্তত যেন ন্যায়সঙ্গত হয়। সিপিডির সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা যায়, সমাজের উঁচু স্তরের ৫ শতাংশ মানুষ নিচু স্তরের ৫ শতাংশ মানুষের চেয়ে ১২১ গুণ বেশি আয় করে। এ ধরনের বিরাট ধন বৈষম্য গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। এজন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে একটি রাজনৈতিক অভিযান বা সংগ্রাম পরিচালিত হলে তা ভালো ফল বয়ে আনতে পারে। অন্যদিকে দেশের শিক্ষিত, সচেতন এবং সুশীল সমাজ সুশাসনের পক্ষে এবং ঘুষ-দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। আমাদের বিশ্বাস প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এদেশের মানুষের কল্যাণের ব্যাপারে যথেষ্ট আন্তরিক। তার মতো দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রনায়কের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক উন্নয়নযজ্ঞের সঙ্গে সুশাসন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়নের মতো গণতন্ত্রায়নের লড়াইটাও সমানভাবে চলুক। দেশবাসী উন্নয়নের সঙ্গে গণতন্ত্রের প্রসারও চায়। উভয়ের অগ্রগতি সমানভাবে দরকার। উন্নয়ন বলতে যেমন শুধু অবকাঠামো নয়, তেমনি গণতন্ত্র বলতেই কেবল নির্বাচনকে বোঝায় না। উন্নয়ন ও গণতন্ত্র অনেক ব্যাপক অর্থবোধক। তাই এসব কিছুর সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। জাতির পথ চলার জন্য অন্তর্ভুক্তি মূলক গণতন্ত্রের পাশাপাশি কার্যকর উন্নয়ন থাকতে হবে। এ জন্য সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন যেমন দরকার, তেমনি দরকার স্থায়ী ও কার্যকর উন্নয়ন কার্যক্রম। গণতন্ত্র বনাম উন্নয়ন বিতর্ক করে এই উভয় বিষয়ের অবমূল্যায়ন করছি। অথচ দুটোই সংশ্লিষ্ট দেশের পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকেন, তাদের বড় কাজ। উন্নত দেশে এসব বিষয়ে তর্ক হয় না। অনুন্নত দেশে এসব নিয়ে তর্কবিতর্কে সময় নষ্ট করা হচ্ছে। সত্যিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উন্নয়ন হবে-এটা অনিবার্য। হয়তো এর গতি একটু শ্লথ হয়ে থাকে। তবে উন্নয়ন এমন হয় না যে, জনগণ অতিষ্ঠ, হয়রান বা বিরক্ত হয়ে গালাগাল করবে। জনজীবন বিঘ্নিত হলেও জনগণ উন্নয়নের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে রাজি।
তবে অহেতুক তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে না ওঠে উন্নয়নের নামে। যদি প্রত্যহ জাতির হাজার হাজার কর্মঘণ্টা বিনষ্ট হয়; ধুলার অন্ধকারে প্রতিদিন পরিবেশ হয়ে পড়ে জঘন্যভাবে দূষিত, তা হলে তো মানুষ ক্ষেপে উঠবেই। তারপরও অবশ্য বোঝা উচিত যে, উন্নয়ন জনগণের জন্যই। ২০৩০ সাল নাগাদ জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশ হতে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ আছে। এখন যে প্রবৃদ্ধি হচ্ছে তার সুফল সবার কাছে পৌঁছানোটাই বড় চ্যালেঞ্জ। দারিদ্র্য দূরীকরণে সাফল্য এলেও দেখা যাচ্ছে ধনী-গরিবের মধ্যে সম্পদবৈষম্য আগের চেয়ে বেড়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণে বর্তমানের যে গতি, সেটা ধরে রাখতে হবে, সম্ভব হলে তা আরও বাড়াতে হবে। পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির সুফল সব মানুষ যাতে সমানভাবে পায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ দেশের যে উন্নতি হচ্ছে, তার ভাগ সবাইকে দিতে হবে। এটি নিশ্চিত করতে হলে মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান বাড়াতে হবে। মানসম্পন্ন কর্মসংস্থান বাড়াতে হলে শিল্পায়নের গতিও বাড়াতে হবে। মূল শ্রমবাজারে নারীদের অংশগ্রহণ এখনো যথেষ্ট নয়, এটি বাড়াতেও যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। সমাজের অর্ধেক অংশকে অর্থনৈতিকভাবে পেছনে রেখে টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।
লেখক: গবেষক ও কলাম লেখক raihan567@yahoo.com
এমএসএম / এমএসএম

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
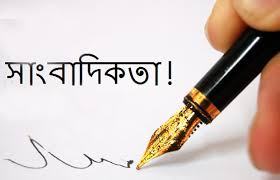
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

অকুতোভয় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা: ২২ বছরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল পরিকল্পনাকারীরা

বিতর্ক থেকে বিবর্তন: তারেক রহমানের রাজনৈতিক রূপান্তর

কুয়েত দূতাবাস সহ মধ্যপ্রাচ্য দূতাবাস গুলো সংস্কার অতি জরুরি

রাজনীতি মানেই কি ক্ষমতার লড়াই?

অধিক আসনের হিসাব না গ্রহণযোগ্য নির্বাচন- তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কোন পথে?

