বিশ্বব্যাপী ডলার সংকট এবং বাংলাদেশে তার প্রভাব

আন্তর্জাতিক বাজারে বড় ধরনের সংকট চলছে।এক্ষেত্রে জ্বালানি তেল এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সব ধরনের পণ্যের দাম বাড়ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক ধরনের অস্থিতিশীল ও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। ২০০৮-০৯ সালে বিশ্ব অর্থনীতি ও ব্যাংকিং খাতে বড় সংকটের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর ১৩-১৪ বছরে এবারই সবচেয়ে চাপে বা টানাপড়েনে দেশের সামষ্টিক অর্থনীতি। বাংলাদেশে ডলার সংকট তীব্র হলে দ্বিপক্ষীয় লেনদেন ও কারেন্সি পরিবর্তন নিয়ে বেশ জোরেশোরেই আলোচনা শুরু হয়েছিল। কিন্তু বিষয়টি আর সেভাবে এগোয়নি। এই না এগোনোর কারণ আমাদের কাছে মোটেই বোধগম্য নয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ হয়তো ভাবতে পারে যে দেশ থেকে ডলার সংকট কেটে যেতে শুরু করেছে, তাই দ্বিপক্ষীয় লেনদেনের এমন জটিল বিষয়ের সঙ্গে আর জড়িত হওয়ার প্রয়োজন নেই। তারা সেটা ভাবতেই পারে, কিন্তু বাস্তব অবস্থা মোটেও তা বলে না। ডলার সংকট খুব শিগগির কেটে যাবে এমনটা ভাবার কোনো কারণ আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া বিশ্বরাজনীতি ক্রমেই যে জটিল রূপ ধারণ করছে, তাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যম হিসেবে ডলারের বিকল্প ব্যবস্থা সব সময় প্রস্তুত রাখা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, বর্তমানে অনেক দেশই দ্বিপক্ষীয় লেনদেন পরিচালনা করছে এবং তা থেকে ভালো উপকৃতও হচ্ছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট বিশ্বমন্দা ও ডলার সংকট এত দিনে কেটে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। অধিকন্তু বিশ্বরাজনীতি ক্রমেই যে জটিল আকার ধারণ করছে, তাতে এই সংকট খুব শিগগির কাটার কোনো সম্ভাবনা আপাতত দেখা যাচ্ছে না। এর ওপর দেখা দিয়েছে আমেরিকায় জাতীয় ঋণসংকট, যা বিশ্বব্যাপী বিরাজমান ডলার সংকটকে আরো তীব্র ও দীর্ঘ করতে পারে।
তা ছাড়া বর্তমান জটিল বিশ্ববাস্তবতায় আন্তর্জাতিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় ডলারের ওপর নির্ভরশীল থাকাটাও ঝুঁকিপূর্ণ বটে। এ কারণেই বিশ্বে চলমান ডলার সংকট থেকে নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থায় রাখার উদ্দেশ্যে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে অতিমাত্রায় ডলারের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে নিয়ে আসার স্বার্থে ডলারে লেনদেনের পাশাপাশি অন্যান্য মুদ্রায়ও লেনদেন চালুর বিষয় গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। সত্যি বলতে কি, এখন সময় এসেছে দ্বিপক্ষীয় লেনদেন শুরু করার। যেসব দেশের সঙ্গে বছরে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আমদানি-রপ্তানি হয়, সেসব দেশের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। লেনদেন সফল করতে একাধিক দেশের সঙ্গে একই রকম লেনদেন করার সুযোগ রাখতে হয়। যেহেতু ইউএস ডলার ব্যতীত অন্য কোনো মুদ্রা সব দেশের কাছে এখনো সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি, তাই একাধিক দেশের মধ্যে বাণিজ্য প্রসারিত করে দ্বিপক্ষীয় লেনদেন দীর্ঘ সময় পর্যন্ত চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে। যেকোন দুইটি দেশের মধ্যে যখন সরাসরি আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালিত হয় এবং সেই আমদানি-রপ্তানির মূল্য পরিশোধ করা হয় নিজ নিজ দেশের মুদ্রায়, তখন সেই বাণিজ্যকে দ্বিপক্ষীয় লেনদেন বলা হয়ে থাকে। এই দ্বিপক্ষীয় ট্রেড চালু করতে হলে কিছু পূর্বশর্ত মেনে চলার বাধ্যবাধকতা আছে। যেমন-এ ধরনের ক্রস-বর্ডার বা আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য চালু করার জন্য দুটি দেশের মধ্যে সরকারি সহযোগিতা থাকতে হবে। দুটি দেশের সরকার যখন সম্মত হবে যে তারা নিজ নিজ দেশের মুদ্রায় আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিষ্পত্তি করবে, তখনই সেটা সম্ভব হবে। প্রত্যেকটি দেশ তাদের ব্যবসায়ীদের সরাসরি এই মর্মে নির্দেশনা দেবে যে দুই দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য নিজ নিজ দেশের মুদ্রায় করতে হবে।
একই সঙ্গে প্রত্যেক দেশের ব্যাংকগুলোর ওপর নির্দেশনা থাকবে যে তারাও যেন রপ্তানিকারকের দেশের মুদ্রায় এলসি খুলতে কোনো রকম সমস্যা না করে। এসব শর্ত পূরণ করতে পারলেই দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চালু করা সম্ভব এবং তা সফলও হবে। দুইটি দেশের মধ্যে সরাসরি আমদানি-রপ্তানি এবং কারেন্সি পরিবর্তন যেহেতু বহুল প্রচলিত বাণিজ্যের কোনো মাধ্যম নয়, তাই বিষয়টি অনেকের কাছেই বেশ জটিল মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্ত দ্বিপক্ষীয় লেনদেন সফলভাবে পরিচালনার জন্য প্রতি লেনদেনের ক্ষেত্রে বা প্রতি মাসে কারেন্সি পরিবর্তন করে আমদানি-রপ্তানি মূল্য পরিশোধ করা যাবে না এবং তা বাস্তবসম্মত হবে না।এখানেই রাষ্ট্রীয়ঋণের প্রয়োজনীয়তা আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বছরের পর বছর তো আর একটি দেশের পাওনা আটকে রাখা যায় না এবং তাও আবার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটা পর্যায়ে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এমনিতেই বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন যে মেরূকরণের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, সেখানে চীন একটা মেরুর কেন্দ্রবিন্দুতে। এখন রাষ্ট্র হিসেবে চীনের যে বৈশিষ্ট্য, তাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চা কিন্তু নেই ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী জনসমর্থন আদায়ের জন্য তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে মানবাধিকার ইস্যুটাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবে। তবে সেটার প্রকাশ দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়। বিশেষ করে ইন্দোপ্যাসিফিক অঞ্চলের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এই পরাশক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলাদেশ একটা ক্ষেত্র বা মঞ্চে পরিণত হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের আর কয়েক মাস বাকি। দেশ-বিদেশে আলোচনা একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের বিষয়। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ পশ্চিমা বিশ্বের প্রবল চাপ। র্যাবের সাত কর্মকর্তার ওপর নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নয়া ভিসা নীতি ঘোষণা। এর প্রতিক্রিয়ায় সরকারের কড়া জবাব। সরকারের অবস্থানে চীনের সমর্থন। সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এখন পুরো বিশ্বের নজরে।
বাংলাদেশে গণতন্ত্রের মান, নির্বাচন, মানবাধিকার পরিস্থিতিসহ অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে বরাবরই নীরবতা অবলম্বনের কৌশল অনুসরণ করে এসেছে চীন, রাশিয়া, জাপানসহ সামরিক ও অর্থনৈতিক পরাশক্তি দেশগুলো। নীরবতা ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র জাপান সম্প্রতি নির্বাচন নিয়ে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। কথা বলছে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে গত মাসে বাংলাদেশের জন্য নতুন ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই অবস্থায় ভূরাজনীতিতে দেশটির প্রতিদ্বন্দ্বী চীন এবং রাশিয়াও এখন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া দেখাতে শুরু করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ করে অর্থনৈতিক শক্তি যেহেতু আগের অবস্থায় নেই। আর চীন বিশ্বে প্রভাব বিস্তার করছে। চীনের এই প্রভাব বিস্তারকে ঘিরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুবই স্পর্শকাতর। সেজন্যই চীনের এই দুর্বল বৈশিষ্ট্যকে ঘিরে তারা তাদের পররাষ্ট্রনীতিটা বাস্তবায়ন করতে চাইছে। যেটার প্রকাশ বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও ঘটছে। এখন চীনের সমর্থনের মধ্যদিয়ে এটা খুব স্পষ্ট হয়ে গেল যে, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বলয়ের যে প্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতার মাঝখানে আমরা চাপে পড়েছি। এটার মধ্যদিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কিন্তু আরেকটি প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। ফলে এই সংকট কাটার চাইতে বরং সংকট আরও ঘনীভূত হওয়ার ক্ষেত্রে এই ধরনের সমর্থন সহায়ক হয়ে উঠছে। ৮ জুন বাংলাদেশে নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেক্সান্ডার মন্টিটস্কি বলেছেন, তাঁর দেশ আশা করে বাংলাদেশে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে। তাছাড়া নির্বাচন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। রাশিয়া অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না।এদিকে অর্থনৈতিক বিকাশ, রাজনৈতিক পরিপক্বতা, ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে গুরুত্ব বাড়ছে বাংলাদেশের।
বঙ্গোপসাগর তথা বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে একটি উদীয়মান শক্তি হিসেবে আাবির্ভূত হয়েছে বাংলাদেশ। আবার এ অঞ্চলের তিনটি বৃহৎ শক্তির সঙ্গে বাংলাদেশের সমীকরণ এবং ঐ তিন বৃহৎ শক্তির নিজেদের মধ্যকার জটিল মাঝখানে রয়েছে বাংলাদেশ। ভারতের সঙ্গে ঐতিহাসিক ও বিশেষ সম্পর্ক, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অধিকারভিত্তিক ইস্যুতে অস্বস্তিকর সম্পর্ক এবং চীনের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে আসন্ন আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তিন বৃহৎ শক্তির অবস্থান ক্রমশই প্রকাশিত হচ্ছে। পরিবর্তীত বাস্তবতায় বাংলাদেশ স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বজায় রেখে আগামী দিনে কীভাবে পরিস্থিতি মোকাবেলা করবে, এদিকে তাকিয়ে আছে বাংলাদেশের মানুষ। যুক্তরাষ্ট্র, জাপানসহ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোও রেকর্ড পরিমাণ বাণিজ্য ঘাটতির সম্মুখীন। তারা সুদের হার বৃদ্ধি থেকে শুরু করে কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। কিন্তু তাতেও খুব একটা সুফল মিলছে না। দেশগুলো রফতানি ও বিনিয়োগ বাড়াতে বাড়তি জোর দিয়েছে। তার পরও বাণিজ্য ঘাটতি কমানো যাচ্ছে না। এর অন্যতম কারণ আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যমূল্যের বৃদ্ধি। কভিডের বিপর্যয় কাটিয়ে পুনরুদ্ধার হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি। দ্রুতগতিতে বেড়েছে অর্থনৈতিক কার্যক্রম। বিধিনিষেধ শিথিলের পর তৈরি হয় তুমুল ভোক্তা চাহিদা। পাশাপাশি সরকারের দেয়া বিপুল পরিমাণ প্রণোদনা বাড়িয়ে দিয়েছে ভোক্তা ব্যয়। এ অবস্থায় চাহিদা মোকাবেলায় বিপুল পরিমাণ পণ্য আমদানি করতে হয়েছে ওয়াশিংটনকে। ফলে ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। ডলারের বিপরীতে ইয়েনের বিনিময় হারে পতন অব্যাহত। অস্থিতিশীল রয়ে গিয়েছে জ্বালানির বাজারও। ফলে আমদানিতে আরো বেশি অর্থ গুনতে হচ্ছে জাপানকে।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ পরিস্থিতি আরো জটিল হচ্ছে। এ অবস্থায় প্রতি মাসে দেশটির বাণিজ্য ঘাটতি রেকর্ড ভেঙে চলেছে। বাংলাদেশকে তাই আগে থেকেই সজাগ থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। দেশের বাণিজ্য ঘাটতি আশঙ্কাজনক জায়গায়। রফতানির তুলনায় আমদানি প্রায় দ্বিগুণ। আমদানি বিল মেটাতে ডলারের চাহিদা ক্রমেই বাড়তে থাকায় পড়ছে টাকার দামও। জাতীয় অর্থনীতির গভীর অসুখ ক্রমেই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। রোববার আয়োজিত এক সেমিনারে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ৩ দশমিক ৫ শতাংশ বাণিজ্য ঘাটতি আশঙ্কাজনক। ক্রমবর্ধমান এ ঘাটতি যদি জিডিপির ৪ শতাংশ হয়, তাহলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় ঘটবে। বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে মূলত আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়া। সে তুলনায় রফতানি বাড়েনি, যদিও আগের চেয়ে বেড়েছে গত অর্থবছর। কিন্তু বৈশ্বিক কারণে মূল্যবৃদ্ধি ও টাকার বিনিময় হার বেড়ে গিয়েছে। এ কারণে আমদানি ব্যয় বেড়ে গিয়েছে টাকার অংকেও। অন্যদিকে রেমিট্যান্সপ্রবাহ বাড়েনি। আমদানি ব্যয় কমিয়ে এনে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে একাধিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে কিন্তু তার বড় প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এলসি খোলা কঠিন হলেও উড়োজাহাজের বিজনেস ক্লাসের সিট ফাঁকা থাকছে না। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে নেয়া উদ্যোগের যথাযথ বাস্তবায়ন ও বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সম্ভাব্য উৎস সন্ধানে আরো সক্রিয় হতে হবে।
লেখক: গবেষক ও কলাম লেখক
এমএসএম / এমএসএম

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
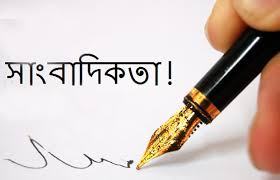
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

অকুতোভয় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা: ২২ বছরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল পরিকল্পনাকারীরা

বিতর্ক থেকে বিবর্তন: তারেক রহমানের রাজনৈতিক রূপান্তর

কুয়েত দূতাবাস সহ মধ্যপ্রাচ্য দূতাবাস গুলো সংস্কার অতি জরুরি

রাজনীতি মানেই কি ক্ষমতার লড়াই?

অধিক আসনের হিসাব না গ্রহণযোগ্য নির্বাচন- তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কোন পথে?

