বহির্বিশ্বে দেশের মান-মর্যাদা নিয়ে ভাবতে হবে

সম্প্রতি এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যার প্রভাব শুধু দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বাইরেও। এসব ঘটনা বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের সুনাম মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করছে। যার ফলে বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশের ব্যাপারে নানা কঠোরতা আরোপ করছে। এতে দেশের ও দেশের মানুষের ভাবমূর্তিই যে শুধু নষ্ট হচ্ছে তা নয়, এর সরাসরি প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও। যদিও বর্তমান সরকার দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করার জন্য বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতেও কোন কাজের কাজ হচ্ছে না। আমাদের রাজনীতির মূল সমস্যা সবকিছুতেই জয়লাভ করা। এখানে নির্বাচনে যে দল হারছে তারা প্রায় সর্বহারা হয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনী প্রতিযোগিতা প্রচণ্ড সংঘাতের রাজনীতি সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে আমাদের নির্বাচিত রাজনৈতিক শাসকগণ সামরিক শাসকদের অনেকে অগণতান্ত্রিক চর্চা পরিত্যাগ তো করেইনি বরং এগুলোকে তারা লালন করে নিয়মে পরিণত করেছেন। সংসদে একটি কার্যকর বিরোধী পক্ষের অভাবে আমরা সরকার প্রক্রিয়ার ভেতর কোনোরকম ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির প্রচলন ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছি। যা গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি টিকিয়ে রাখার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি, আগামীর বাংলাদেশ আর আমাদের চলমান সংকটের নেপথ্যে কি? এমন নানা প্রশ্নে আলোচনার যেন শেষ নেই। ১৯৯১ এর পর থেকে আমরা নির্বাচনী গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেবার চেষ্টা করেও কেন বারবার বার্থ হচ্ছি। নির্বাচনী গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার হস্তান্তর। নির্বাচনে এক দল হারবে, এক দল জিতবে। যারা একবার হারল তারা এর পরের বার আবার জিততেও পারে। নির্বাচনী গণতন্ত্রে বিভিন্ন দলের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা হতে পারে, তবে সেই প্রতিযোগিতা কখনো সংঘাতে পরিণত হওয়া উচিত নয়। সংঘাতের রাজনীতির ফলে দুই প্রধান দলের মধ্যে বাদানুবাদ কখনই রাজনৈতিক সংলাপের মধ্যেদিয়ে সমাধান করা যাচ্ছে না।
রাজনীতিতে বিভিন্ন দলের মধ্যে মতভেদ থাকতেই পারে, কিন্তু একটা ব্যবস্থা সকল দলকেই মানতে হবে যার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে এই সব মতভেদ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে এবং সমাধানের বিভিন্ন পথ খুঁজে বের করা যায়। আমাদের দেশের রাজনীতির মূল সমস্যা হলো সকল দলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি ব্যবস্থা আমরা গড়ে তুলতে পারিনি যার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক বিভেদগুলোর সমাধান করতে পারা যায় এবং শান্তিপূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়। আমাদের এখানে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী না হওয়ার পেছনে প্রতিবন্ধকতাগুলো কোথায়? গত ৫২ বছর ধরে আমরা রাজনীতি চর্চা এবং শাসনপ্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এমন কিছু রীতিকে নিয়মে পরিণত করেছি যেগুলো আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী হওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক। এর মধ্যে কিছু রীতি সামরিক শাসন থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি;দুর্ভাগ্যবশত,আমাদের নির্বাচিত রাজনৈতিক শাসকগণ সামরিক শাসকদের অনেক অগণতান্ত্রিক চর্চা পরিত্যাগ তো করেইনি, বরং এগুলোকে তারা লালন করে নিয়মে পরিণত করেছেন। রাজনীতি আবারো সংকটে-বারবার দেশ একইরকম পরিস্থিতির দিকে কেন ফিরছে? বিশেষজ্ঞদের মতে, যতদিন পর্যন্ত না সব রাজনৈতিক দল তাদের নিজেদের মধ্যে মতভেদ এবং শান্তিপূর্ণভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে একটি ব্যবস্থা সম্পর্কে ঐকমত্যে না পৌঁছাতে পারবে ততদিন পর্যন্ত আমরা বারে বারে এই সংকটে পড়বো। তবে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা থাকলে যেকোন সংকট মোকাবিলার করা সম্ভব। উন্নয়ন আগে, গণতন্ত্র পরে-এ কথাটি নানাভাবে আলোচনায়। এই আলোচনা একেবারেই অবান্তর এবং যুক্তিহীন। দুটোই একে অপরের সম্পূরক। দুটোই জনগণ চায় এবং এক সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া উচিত। প্রতিটি রাজনৈতিক সংগঠন মুখে এবং তাদের দলিলপত্রে এ কথাই বলে যে, তাদের লক্ষ্য, ক্ষমতায় গিয়ে জনগণের সঙ্কট মোচন করে তাদের উন্নত জীবন নিশ্চিত করবে।
এমন সব দল আছে যারা নিজেরাই বিশ্বাস করে, যারা তাদের সংগঠনের শক্তি সামর্থ্য এতকম যে,কস্মিনকালেও তাদের পক্ষে এককভাবে ক্ষমতায় যাওয়া অসম্ভব। তারপরও তারা জনকল্যাণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে উচ্চকণ্ঠ। এর কারণ, প্রতিশ্রুতির বন্যায় মানুষকে না ভাসালে প্রচলিত রাজনীতি করা যায় না। তাই সবাই মনে করে, এসব যতটা না আন্তরিক তার চেয়ে বেশি রাজনৈতিক।তা ছাড়া, রাজনীতি হয়ে উঠেছে অনেকের পেশা। এ কারণে অন্য আর দশটি পেশার মতোই নিজের ভূত-ভবিষ্যৎ ভেবে সমৃদ্ধির পথকে নিষ্কণ্টক করে তোলাই হচ্ছে রাজনীতি পেশাজীবীর লক্ষ্য। আগের মতো রাজনীতি এখন আর জনাশ্রয়ী নয়, এটা বর্তমানে আত্মাশ্রয়ী। অতীতে উন্নত আদর্শ ও উত্তম কর্মপন্থা নিয়ে রাজনীতির চর্চা করা হতো। এখন এর লক্ষ্য হচ্ছে নিছক ক্ষমতা লাভ আর আত্মপ্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের রাজনীতির অনেক বড় বড় সঙ্কটের মধ্যে রয়েছে, এমন মানসিকতা পোষণ করা। এই রাজনৈতিক দূষণ আসলে নৈতিক অবক্ষয়ের পরিচায়ক এবং তা থেকে বাঁচতে হলে এসবের ঊর্ধ্বে উঠতে হবেই। এমন অবাঞ্ছিত মানসিকতার কারণে এসব নেতার সাহচর্য যারা পেয়ে থাকে, তারাও লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে অনিয়ম দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। আর এদের ভূমিকার কারণেই সমাজজীবন কলুষিত হয়ে মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এসব কারণে আমাদের সমাজে রাজনীতির সাথে সাধারণ মানুষের সাধারণত সংশ্রব নেই। রাজনীতি যে সমাজকে কল্যাণকর কিছু দিতে পারে, সে বিশ্বাস ও আস্থা হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ এমন ধারণা গণতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য মঙ্গলজনক নয়। রাজনীতির সঙ্কটের যে চিত্র নিয়ে কথা বলা হলো, এর প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভেতর নানাভাবে পড়েছে ও পড়ছে। বিশেষ করে সুনীতির বোধ বিবেচনা রাজনীতিতে আর নেই। দলগুলো যখন গণতন্ত্রের কথা বলে,তখন মনেহবে তারা গণতন্ত্রগত প্রাণ।
কিন্তু দলের ভেতরে ও বাইরে তাদের আচরণ একটা থেকে আরেকটা ভিন্ন। জাতীয় সাধারণ নির্বাচনগুলোর সময় তাদের প্রকৃত আচরণ লক্ষ করা যায়। তখন দেখা যায়, গণমানুষের ভোটাধিকারের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র আস্থা বা শ্রদ্ধা নেই। যেনতেন প্রকারে নিজেদের বিজয়ী করতে কোনো নীতিবোধের তোয়াক্কা করে না এসব দল।
গণতন্ত্রের যে চেতনার অর্থ, মানুষের পছন্দ-অপছন্দের প্রতি শ্রদ্ধা বিশ্বাস দেখানো, তার বিন্দুমাত্র অনুশীলন এ দেশে লক্ষ করা যায় না। এভাবে ‘বিজয়ী’ হওয়ার পর ক্ষমতা কুক্ষিগত করে তারা যে আচরণ করে থাকে, তাতে কর্তৃত্ববাদিতা ছাড়া আর কিছু তেমন থাকে না। আর এটি নতুন কিছু নয়, বহুকাল থেকে এমনই লক্ষ করা যাচ্ছে অন্তত আমাদের বাংলাদেশে। এতে যে মানুষের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় বিধিবিধান লঙ্ঘিত হয় আর গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ভেঙে চুরমার হয়; আর শুধু তা নিয়ে দেশেই নয়, দেশের বাইরে আন্তর্জাতিকভাবে রাষ্ট্রের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, সেটা তোয়াক্কা করা হয় না। একটি দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যদি অগ্রগতি হতে থাকে, সেখানে বহির্বিশ্বে যদি রাজনীতিকদের কারণে দেশ ও জাতির সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়, তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হতে পারে কি? মানুষ এমন আশাই করে যে, নেতাদের আচরণ হওয়া উচিত পরিশীলিত। অথচ আজকের দিনে এমন আশা করাটা যেন স্বপ্নবিলাস। রাজনৈতিক নেতাদের বিবেচ্য একটাই- তার এবং তার সহযোগীদের প্রভাব প্রতিপত্তি সহায় সম্পদের সুরক্ষার, তথা তাদের ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থের জন্য নিবেদিত হয়ে থাকা। বাংলাদেশে এটা সবারই জানা যে, এখানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বেসুমার। এর কারণ দল গঠন করতে বিশেষ কোনো যোগ্যতা ও জনসমর্থনের প্রয়োজন হয় না। আর বেশি দলের বিদ্যমান থাকাটা অধিকতর গণতান্ত্রিক সমাজের পরিচায়ক, এটা মনে করা যায় না। আবার মাত্র কয়েকটি দলের অবস্থান মানে এমন নয় যে, এ দেশে গণতন্ত্রের ঘাটতি রয়েছে। প্রতিটি দলের স্বতন্ত্র মেজাজ, নীতি, আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থাকতে হবে।
আর এ থেকেই জনগণ যে সংগঠনের সাথে নিজের মত ও পথের সামঞ্জস্য পাবে, তাকেই গ্রহণ করবে। এটাকে গণতান্ত্রিক পছন্দ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। শুধু বাংলা দেশেই প্রকৃত দলের সংখ্যা কম, তা নয়। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতেও মূল স্রোতের দলের সংখ্যা খুব সীমিত। অথচ এ তিনটি দেশই গণতান্ত্রিক দিক থেকে আদর্শের অবস্থানে বিরাজ করছে। বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য থেকে যে মুল বক্তব্যটি প্রকাশ পেয়েছে তাহলো, সাধারন মানুষ রাজনৈতিক এই হানাহানি থেকে মুক্তি চায়, তারা বিশ্বাস করে, মানুষের জন্যই রাজনীতি, ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো আন্দোলন করুন, তাদের যুক্তিসংগত আন্দোলন নিয়ে কারো মাথা ব্যাথা নেই, কিন্তু যখন আন্দোলনের নামে মানুষ হত্যা করা হয় এবং আবার তা দমন করতে গিয়ে মানুষ হত্যা করা হয় সেটা কোন ভাবেই মেনে নেয়া যায় না।তারা রাজনৈতিক দল- গুলোর কাছে দাবি জানিয়েছে অবিলম্বনে আন্দোলনের নামে এই মানুষহত্যা বন্ধ হোক পাশাপাশি বিরোধীমত দমনের নামে সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসও বন্ধ হোক। কারন যেই মরুক মরছে, মরছে আমাদের মানুষই। এমন সব অন্যায় প্রবণতা রাজনীতির প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। এটা হলো রাজনীতির এক সঙ্কট। তাছাড়া বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি যেদিকে এগুচ্ছে তাতে ভবিষ্যৎ কোনদিকে যাচ্ছে বলা কঠিন। তবে এ ধরনের পরিস্থিতির মোকাবিলা করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার কলা কৌশল রাজনীতিকদের ওপরই নির্ভর করবে। স্বাধীনতার পর থেকে ক্রমান্বয়ে আমাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নতি যথেষ্ট হয়েছে এবং ভবিষতেও ভালো হবে বলে মনে হচ্ছে। তবে রাজনৈতিক উন্নয়ন এবং গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এখনো আমাদের সামনে বিরাট চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ নিয়ে বিশ্বশক্তিগুলোর মেরুকরণ প্রকাশ্যে চলে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পালটা পালটি মতামত দিয়েছে,যা বাংলাদেশের জন্যে মঙ্গল বয়ে
আনবে না বরং ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেছেন, বড় শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশকে নিয়ে টানাটানি করা বিপজ্জনক। বাংলাদেশের সমস্যা নিজেদেরই সমাধান করা প্রয়োজন। শক্তিশালী দেশগুলোরও তাদের বৈরিতায় আমাদের টানা উচিত নয়। অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন, গণতন্ত্র ও মানবাধিকার প্রভৃতি ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত ঢাকাকে চাপ দিচ্ছে। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না। ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এক হয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। এখন তারা পরস্পরের বৈরী সম্পর্কে আবদ্ধ। তাদের এ বৈরিতার মধ্যে আজকে আমাদের টানা হচ্ছে। এটা আমাদের জন্যে কতটুকু মঙ্গলজনক তা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে আমরা কারও পক্ষে কিংবা বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া ঠিক হবে না। এখন বড় শক্তিগুলো যা করছে তা ভূ-রাজনীতির স্বার্থকে সামনে রেখে করছে। কিন্তু আমাদের স্বার্থে নয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের ভূমিকা পরিপক্ব। তারা এ ব্যাপারে চুপ থাকার কৌশল নিয়েছে। আবার মৌনতা কখনও কখনও অসম্মতির লক্ষণ। আমরা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল দেখতে চাই। পরাশক্তির লড়াইয়ের মাঝে আমাদের না পড়াটাই ভালো। যে বিষয়গুলোকে নিয়ে এটা হচ্ছে, সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে আমাদের নিজেদেরকেই জরুরি ভিত্তিতে উদ্যোগী হওয়া দরকার। আমাদের সমস্যা আছে ঠিকই, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সব দেশের ক্ষেত্রে সমানভাবে পরামর্শ দেয় না। তাদের সহযোগী দেশগুলোর মানবাধিকার কিংবা গণতন্ত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলে না। ফলে যুক্তরাষ্ট্র যত শক্তিশালী দেশই হোক তাদের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে আমাদের সমস্যা আমাদেরই সমাধান করা উচিত।
লেখক: গবেষক ও কলাম লেখক
এমএসএম / এমএসএম

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
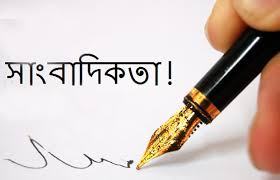
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

অকুতোভয় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা: ২২ বছরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল পরিকল্পনাকারীরা

বিতর্ক থেকে বিবর্তন: তারেক রহমানের রাজনৈতিক রূপান্তর

কুয়েত দূতাবাস সহ মধ্যপ্রাচ্য দূতাবাস গুলো সংস্কার অতি জরুরি

রাজনীতি মানেই কি ক্ষমতার লড়াই?

অধিক আসনের হিসাব না গ্রহণযোগ্য নির্বাচন- তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কোন পথে?

