ব্রিকস সম্মেলন পশ্চিমাদের জন্য সতর্ক বার্তা

২০০৯ সালে ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত ও চীন ‘ব্রিক’ নামে একটি জোট গঠন করে। পরের বছর দক্ষিণ আফ্রিকা যোগ দিলে এ জোটের নতুন নাম হয় ‘ব্রিকস’। শুরুর দিকে অবশ্য জোটটি নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়নি। এটির সফলতা নিয়েও সন্দেহ ছিল। তবে পশ্চিমা উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর বাইরে ব্রিকস বর্তমানে একটি শক্তিশালী জোটে পরিণত হয়েছে। দেশগুলো তাদের প্রভাব ও উপস্থিতি বিশ্বজুড়ে জানান দিতে পেরেছে। এ জন্য পুরো বিশ্বের নজর এখন জোহানেসবার্গে শুরু হওয়া জোটের ১৫তম শীর্ষ সম্মেলনের দিকে। আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন ধরনের ভাবনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সূচনা কালে এই ভাবনার পরিধি বেড়েই চলেছে। নতুন নতুন চিন্তাকেন্দ্রিক স্বপ্নের দ্বারোন্মোচনে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। সময়ের প্রয়োজনে প্রতিযোগীরা রাজনীতির অঙ্ক মেলাতে গলদঘর্ম হয়ে উঠেছেন। কৌশলগত অংশীদারিত্বের প্রত্যাশা নিয়ে জোটবদ্ধ হচ্ছে বিভিন্ন ইস্যুতে। কিন্তু মূল লক্ষ্য সবারই এক ও অভিন্ন, তা হচ্ছে নিজ নিজ দেশের উন্নতি সাধন। বিশ্ব বাজার পরিস্থিতি বর্তমান সভ্যতায় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি।এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় রাজনীতির কৌশলও বদলাতে হচ্ছে। ইউক্রেন সংঘাতের পটভূমিতে এবং ব্রিকসের দুই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য চীন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে বাইডেন প্রশাসনের দ্বৈত অবরোধ কৌশলের প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি বড়ই কঠিন। দক্ষিণ আফ্রিকার কর্মকর্তারা জানান, এ পর্যন্ত ৪০টিরও বেশি দেশ এই জোটে যোগ দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এর মধ্যে ২২টি দেশ যুক্ত হওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আবেদন করেছে। বাংলাদেশও এই জোটে যোগ দিতে পারে বলে এর আগে আভাস পাওয়া গেলেও নতুন ছয়টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম নেই। এবারের ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২শে অগাস্ট দক্ষিণ আফ্রিকা যান।
তবে ব্রিকসের ১৫ তম বৈঠকে জোটটির সাথে বাংলা- দেশের যুক্ত না হওয়ার সম্ভাব্য কারণ হিসেবে অর্থনীতি এবং ভূ-রাজনীতির বিষয়গুলোকে সামনে নিয়ে আসছেন কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে বিষয়টিকে এখনই কূটনৈতিক ব্যর্থতা হিসেবে দেখছেন না তারা। তারা বলছেন যে, প্রকৃত কারণ জানতে হলে আরো কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে। যদিও কেউ কেউ বলছেন, এবার সদস্যপদ দেয়ার ক্ষেত্রে কিছু বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছে। হয়তো সেসব বিষয়ে বাংলাদেশ তুলনামূলক পিছিয়ে থাকায় এ দফায় বাংলাদেশকে সদস্যপদ দেয়ার ক্ষেত্রে বিবেচনায় নেয়া হয়নি। আশ্চর্যজনকভাবে সাম্প্রতিক অতীতে চীন এবং রাশিয়া তাদের বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গিতে নাটকীয় পরিবর্তন এনেছে এবং দৃঢ়ভাবে মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। এ দুই বৃহৎ প্রতিবেশীর মধ্যে সীমাহীন বন্ধুত্ব ব্রিকসের অন্য সদস্যদের থেকে তাদের কিছুটা আলাদা করে দিয়েছে। এটি জোটের রসায়নকে প্রভাবিত না করে পারে না। যদিও তাদের বাস্তববাদ এবং বিচক্ষণতার দৌলতে যূথবদ্ধতার চেতনা অব্যাহত রয়েছে। বলে রাখা দরকার, অনেক দেশ ব্রিকসে যোগ দিতে চায় মূলত এ ধারণা থেকে যে, এটি বিশেষত ছোট এবং মাঝারি রাষ্ট্রগুলোর বিষয়ে অনেকটা ন্যায়সংগত এবং কম স্বার্থপর বিশ্ব শাসনকে সমর্থন করে।এটাকে ব্রিকসের এক প্রকার দ্বিতীয় স্তম্ভ বলেও আখ্যায়িত করা যায়। ভুলে যাওয়া উচিত নয়, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ব শাসনের সব অভিজ্ঞতা, সাধারণ মূল্যবোধ এবং অংশীদারিত্বমূলক স্বার্থের ভিত্তিতে তৈরি পশ্চিমা জোটের দখলে। তবে পরিহাসজনক হলো, এটি তাদের ব্লক মানসিকতা’য় আটকে দিয়েছে। ব্রিকসের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং বিশ্ব এজেন্ডা সেট করার ক্ষমতার অভাব রয়েছে, যা জি-৭ কয়েক দশক ধরে করে আসছে।সাম্প্রতিক বছর গুলোতে বৈশ্বিক পরিসরে যুক্তরাষ্ট্রের নানা উদ্যোগকে ব্রিকস যে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে,তাতে সন্দেহ নেই।
বিশেষ করে ইউক্রেন ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার ওপর যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে, কূটনৈতিক দিক থেকে সেই নিষেধাজ্ঞাকে ব্রিকস প্রচ্ছন্নভাবে খাটো করেছে। এদিকে ডলারকে দুর্বল করে দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী মুদ্রার মর্যাদা থেকে তাকে নামিয়ে আনার চেষ্টাও ব্রিকস দেশগুলো করে যাচ্ছে বলে গুঞ্জন রয়েছে। ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার জোট সংগঠন ব্রিকস-এর নেতারা ২২ আগস্ট জোহানেসবার্গে যখন দুই দিনের সম্মেলনে যোগ দেবেন, তখন ওয়াশিংটনের নীতি নির্ধারকেরা সন্দেহাতীতভাবে ওই নেতাদের কথা খুব মন দিয়ে শুনেছেন। এই সম্মেলনে ব্রিকসের সদস্যসংখ্যা ২৩-এ উন্নীত করার পরিকল্পনা রয়েছে। সদস্য হতে আগ্রহী দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র বিরোধী ইরান, কিউবা ও ভেনেজুয়েলার মতো দেশও আছে। অর্থাৎ ব্রিকস দিন দিন যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থবিরোধী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে তাতে সন্দেহ নেই। এই অবস্থায় ওয়াশিংটন কী করবে এবং ব্রিকসের কাজকর্মের প্রতিক্রিয়া জানাবে, সেটি একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। টাফ্টস বিশ্ব- বিদ্যালয়ের গবেষণা দল উদীয়মান শক্তিদের জোটগুলো নিয়ে গবেষণা করে আসছে এবং তারা ব্রিকসের বিবর্তন প্রক্রিয়া ও তাদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক নিয়ে মূল্যায়ন করেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, চীনা আধিপত্যের অধীনে থাকা ব্রিকস নামের এই গ্রুপ মার্কিন স্বার্থবিরোধী অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নের নীতি অনুসরণ করে থাকে বলে সাধারণভাবে যা বলা হয়ে থাকে, তা আসলে ঠিক নয়।বরং ব্রিকসভুক্ত দেশগুলো অভিন্ন উন্নয়ন স্বার্থ ও বহুমুখী বিশ্বব্যবস্থার অন্বেষণে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে যেখানে কোনো একক শক্তির আধিপত্য নেই। তবে এটি সত্য যে ব্রিকসে জড়ো হওয়া দেশগুলো একটি শক্তিশালী গ্রুপে পরিণত হয়েছে, যা এখন ওয়াশিংটনের ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যকে চ্যালেঞ্জ করে বসছে। যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র দেশ আলজেরিয়া ও মিসরের মতো দেশগুলোও এখন ব্রিকসে যোগ দিতে চাইছে।
সে ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের একটি ব্রিকস নীতি তৈরি করা উচিত, যা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিকে নতুন করে কল্পনা করতে সাহায্য করতে পারে। ব্রিকস নীতি নিশ্চিত করতে পারবে যে যুক্তরাষ্ট্র এখন আর কোনো একক দেশের খবরদারির বিশ্বে নয়, বরং একটি বহুমুখী বিশ্বে অবস্থান করছে। এবার ব্রিকস শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে ভারতের মনোভাব কিছু বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এ জোট সম্পর্কে ভারতের ধারণার মধ্যে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে। ধারণাটি হলো, ব্রিকস বিশ্বের সংশোধনবাদী কিছু শক্তির একটি জোট, যারা বিদ্যমান বিশ্বব্যবস্থার ধ্বংস চায় না; শুধু চায় এ ব্যবস্থায় তাদেরও স্বার্থ অন্তর্ভুক্ত হোক। তবে সময় থেমে থাকেনি। এরই মধ্যে বিশ্বায়ন মুমূর্ষু হয়ে পড়েছে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে গঠিত যে ব্যবস্থা এর ভিত্তিস্বরূপ কাজ করে, তা আদৌ অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়। একদিকে রাশিয়া ও চীন মার্কিন নিষেধাজ্ঞার অধীনে রয়েছে, বিপরীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সম্ভবত ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে। উভয়ে মিলে প্রায় একটি জোট গঠন করেছে; ওয়াশিংটন যাকে শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব হিসেবে বর্ণনা করে। শুধু তা-ই নয়, চীনের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এমনকি ভারতের জন্য সুবিধা বয়ে আনছে বললেও ভুল হবে না। চিপ শিল্পকে কেন্দ্র করে দুটি দেশের মধ্যে প্রক্রিয়াধীন ঘনিষ্ঠ বন্ধন এ ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ হতে পারে। বলা যেতে পারে, এর ফলে ভারতের জীবনযাত্রা আরও ভালো হয়ে উঠতে পারে। তাই দেশটির এলিটদের পক্ষে বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার ধ্বংস দূর স্থান, এর মৌলিক পুনর্গঠনের জন্যও আগ্রহী হওয়ার কোনো কারণ থাকতে পারে না। মূল কথা হলো, ব্রিকসের প্রভাব খাটিয়ে বিশ্বকে আরেকটু ন্যায়সংগত এবং স্থিতিশীল করা গেলে ভারত তাতেই সন্তুষ্ট থাকবে। আর এটি এক অবাস্তব স্বপ্নও নয়। কারণ ব্রিকস ইতিহাসের সঠিক দিকেই রয়েছে।
এ জোটের সদস্যদের কারোরই এ দুর্নাম নেই যে, তাদের বিদ্যমান অর্থনৈতিক সুযোগ এবং রাজনৈতিক প্রভাব রক্ত ঝরিয়ে অর্জিত এবং কয়েক শতাব্দী ধরে সঞ্চিত এ সম্পদকে তারা আঞ্চলিক এবং বিশ্বব্যাপী আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত করেছে। ফলে ভারত তার উদ্দেশ্য পূরণে বেশ সাবলীল বোধ করছে। কেন জাতীয় বৈশিষ্ট্য, মূল্যবোধ এবং স্বার্থের এত ভিন্নতা সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মিসর ও সৌদি আরবের মতো দেশ জোটটির প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। এ দেশগুলো এমনকি এটাও মনে করে যে পাশ্চাত্যের কাছ থেকে বিশ্ব শাসনের ব্যানার হস্তগত করার সামর্থ্য এ জোট রাখে। অবশ্য এ ধরনের প্রত্যাশা অযৌক্তিক। কারণ সেগুলো সমগ্র আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার একটি নির্দিষ্ট পূর্বনির্ধারিত দিকমুখী বিবর্তনের ওপর ভিত্তি করে রচিত, বাস্তবতা যাকে সমর্থন করে না। কাজেই এটা খুবই স্বাভাবিক যে আগামী দিনগুলোতে বিশ্ব শাসনে ব্রিকস সত্যিকার অর্থে কতটা নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে, ব্রাজিল বা ভারত তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে পারে। সত্যি করে বললে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্রিকসের পক্ষে অতীতের সংশোধন- বাদী আচরণটুকুও বজায় রাখা সম্ভব কিনা, তা নিয়েই অনিশ্চয়তা রয়েছে। সমস্যাটি ইউক্রেন সংঘাতের ফলাফল সম্পর্কিত নয়। এ যুদ্ধে রাশিয়া হারতে পারে না এবং হারবেও না। তবে এখানে গো-হারা হারলেও রাশিয়ার প্রতিপক্ষ বিশ্ব সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে, এমন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। যদি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে ব্রিকস প্রসারিত হয়, তাহলে জোটের ঐক্য দুর্বল হতে পারে এবং পরিণামে জোটটি ঢিলা ও অকার্যকর হয়ে যেতে পারে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ক্ষেত্রে এটাই হয়েছিল। তথাপি সময়টা রূপান্তরের; রাজনীতির চিরন্তন নীতি সম্পর্কে ডব্লিউবি ইয়েটসের বিক্ষুব্ধ রচনা থেকে বলা যায়,যেখানে সর্বোত্তম মানুষদের মধ্যে ন্যূনতম প্রত্যয়ের অভাব রয়েছে, অন্যদিকে সবচেয়ে বাজে মানুষেরা অনুভূতির তীব্রতায় পূর্ণ।
এখানে বেশ কিছু কারণ জড়িত এবং বিরোধাত্মক মনে হলেও একটি প্রধান কারণ হলো, ভারতের ব্রিকস অংশীদার চীনের অভূতপূর্ব উত্থান, যা দেশটির অভ্যন্তরে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। নিরাপত্তার সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত যে কয়েকটি উপায় কার্যকর মনে করে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অংশীদারিত্ব হলো সেগুলোর একটি।
এতৎসত্ত্বেও ভারতের ব্রিকস অংশীদাররা জাতীয় স্বার্থের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি চালিয়ে যেতে সক্ষম বলে ভারত বিশ্বাস করতে পারে এবং তাদের তা করা উচিত। সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই যে ভারত বিশ্বকে আরও ন্যায়সংগত ও স্থিতিশীল করে তুলতে প্রয়োজনীয় বৈশ্বিক এজেন্ডার প্রধান বিষয়গুলো নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্রিকসের চূড়ান্ত প্রভাবে বিশ্বাস করে। সব মিলিয়ে প্রশ্ন হলো-ব্রিকস কি যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের বিকল্প অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক স্তম্ভ হিসেবে আবির্ভূত হবে? অথবা অভ্যন্তরীণ পার্থক্য কি গ্রুপটির সক্ষমতা সীমিত করতে পারে? এসব বিবেচনায় বিশ্লেষকরা বলছেন, ব্রিকস জোটের প্রভাব আরও বাড়তে পারে। তবে এটি নাটকীয় ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যবস্থার প্রতিস্থাপন করতে পারবে বলে মনে হয় না। এর পরও বিকাশমান পাঁচ অর্থনীতির দেশের জোট ব্রিকসের সদস্যসংখ্যা বাড়ানোর চুক্তি নিয়ে ব্রিকসের সদস্য হওয়ার জন্য ছয়টি দেশকে আমন্ত্রণ জানানোর ঘোষণা দিয়েছে জোটটি। আমন্ত্রণ পাওয়া দেশ ছয়টি হলো আর্জেন্টিনা, মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। যদিও বিদ্যমান বিশ্ব ব্যবস্থায় খন্ড খন্ড অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক বিকল্প তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তা ছাড়া এটি পশ্চিমের সঙ্গে আরও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। যাহোক,এখন শুধুই অপেক্ষার পালা। বিশ্ব কি বিভক্তির দিকে যাচ্ছে, নাকি সমঝোতার মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে? তা সময়ই বলে দেবে।
লেখক: গবেষক ও কলাম লেখক
এমএসএম / এমএসএম

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
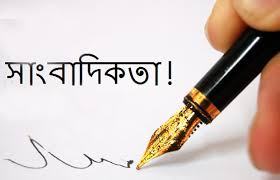
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

অকুতোভয় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা: ২২ বছরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল পরিকল্পনাকারীরা

বিতর্ক থেকে বিবর্তন: তারেক রহমানের রাজনৈতিক রূপান্তর

কুয়েত দূতাবাস সহ মধ্যপ্রাচ্য দূতাবাস গুলো সংস্কার অতি জরুরি

রাজনীতি মানেই কি ক্ষমতার লড়াই?

অধিক আসনের হিসাব না গ্রহণযোগ্য নির্বাচন- তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কোন পথে?

