সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ বড় চ্যালেঞ্জ

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা-এফএও এর তথ্য অনুযায়ী, গত অগাস্ট মাসে সারা বিশ্বে খাদ্য মূল্যস্ফীতি কমে সর্বনিম্ন হয়েছে। এই সময়ে চাল ও চিনি ছাড়া বিশ্ববাজারে প্রায় সব খাদ্যপণ্যের দামই কমেছে। তবে উল্টোচিত্র দেখা গেছে বাংলাদেশে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা ছাপিয়ে ধার দেওয়াটা মূল্যস্ফীতিকে উসকে দিয়েছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ সুদহার বাড়িয়ে যেখানে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করছে সেখানে বাংলাদেশ হাঁটছে উল্টো পথে। ব্যবসায়ীদের সুবিধা দিতে এখনো কৌশলে সুদহার কমিয়ে রাখা হয়েছে। তাছাড়া বাজার অব্যবস্থাপনার কারণেও মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। অগাস্টে মুদ্রাস্ফীতি ২৩ বেসিস পয়েন্ট বেড়ে যাওয়ার কারণে গড় মূল্যস্ফীতি ৯.৯২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। তবে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী, অগাস্টে খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেড়ে ১২.৫৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে যা ১২ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর আগে খাদ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল ২০১১ সালের অক্টোবরে-১২.৮২ শতাংশ। খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেশি বেড়েছে গ্রামীণ এলাকায়। সেখানে এর পরিমাণ ১২.৭১ শতাংশ। গত জুলাইতে এটি ছিল ৯.৮২ শতাংশ। সব মিলিয়ে ২০২৩ সালে গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ৯.৪০ শতাংশ। এমন একসময়ে এই মূল্যস্ফীতি বাড়ছে যখন আশপাশের দেশসহ সারা বিশ্বে এটি কমে আসছে। কিন্ত বাংলাদেশে কেন বাড়ছে তা ভেবে দেখার সময় এখনই। মূল্যস্ফীতি নিয়ে আলোচনায় যে বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়,তা হচ্ছে-কী কারণে দাম বেড়েছে? নীতি পদক্ষেপের মাধ্যমে দাম বাড়ানোর হার কমানো যেত কিনা? এবং উপশম করার কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কি না? যদিও মূল্যস্ফীতির ফলে সবার ওপর সমান প্রভাব পড়ে না। খাদ্য মূল্যস্ফীতি এক যুগের মধ্যে সর্বোচ্চ। নিম্ন, নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষ খাদ্যে বেশি পরিমাণে খরচ করে বিধায় তাদের ওপর অভিঘাতের মাত্রা বেশি।
একইভাবে গ্রামাঞ্চলে সার্বিক মূল্যস্ফীতি শহরের সার্বিক মূল্যস্ফীতি থেকে বেশি হওয়ায় বৈষম্যমূলক প্রভাব বিরাজমান। এক বছরের বেশি সময় ধরে বাজারে প্রতিটি পণ্যের দাম অস্বাভাবিক হারে বেড়েছে। বিশেষ করে চিনি, মাছ, সবজি, বিভিন্ন মসলা, তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি পণ্যের দাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বিগুণ-তিন গুণও হয়েছে। প্রকৃত খাদ্য মূল্যস্ফীতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বা বিবিএসের দেয়া তথ্যের চেয়ে বেশি। এর কারণ হিসেবে বিশেষজ্ঞরা দেখছেন, খাদ্য পণ্যের ওপর কম গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ এখন সরকারের হাতে খানা জরিপের নতুন তথ্য আছে। মূল্যস্ফীতির সময়কাল বেশি হওয়ায় তাদের জীবন যাত্রায় ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা তৈরি হয়েছে। সরকারি আয় তলানিতে। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদন তথা জিডিপিতে করের পরিমাণ দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান ছাড়া অন্য সব দেশের নিচে। এছাড়া দিন দিন কর-জিডিপি অনুপাত হ্রাস পাওয়া এবং আয় কম থাকায় ঋণ বাড়ছে। ২০২২ সালের জুলাই-পরবর্তী এক বছরের হিসাব লক্ষ করলে দেখা যাবে সরকারের ঋণের মাত্রা ৩৮ দশমিক ৩০ শতাংশ বেড়ে ১ লাখ ৭ হাজার ৯২৬ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক রেকর্ড পরিমাণ টাকা ছাপিয়ে সরকারকে ঋণ দেয়ায় মূল্যস্ফীতি উসকে দিতে বড় ভূমিকা রাখছে। মূল্যস্ফীতি ঊর্ধ্বমুখী হলে প্রথাগতভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রা সরবরাহ কমিয়ে দেয়ার কথা।কিন্তু এক্ষেত্রে তা না করে সরকারকে ঋণ দিতে বাধ্য হচ্ছে। মূল্যস্ফীতির ভার লাঘবে সরকার নিম্ন বা নির্দিষ্ট আয়ের মানুষকে সহায়তা করে। কিন্তু বাংলাদেশে যে সামাজিক নিরাপত্তা জাল বা কর্মসূচি আছে সেগুলো বহু খণ্ডে খণ্ডিত এবং ত্রুটিযুক্ত। যারা অন্তর্ভুক্ত থাকার কথা নয় তারাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। আবার যাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা তারা অন্তর্ভুক্ত থাকছেন না। এতে কোনো প্রকার সহায়তা সঠিকভাবে কাজ করছে না।
অন্যদিকে মজুরি হার না বাড়ার কারণে সাধারণ মানুষ দাম বাড়ার কশাঘাতে জর্জরিত। ডলারের চলমান চাপ থাকার কারণে মুদ্রা বিনিময় হারের কারণেও বাজারে মূল্যস্ফীতি ঘটছে। আবার অন্যদিকে দেখা যাবে যে সম্পদের কেন্দ্রীভবন ঘটছে। এমনটা ঘটলে বাজারের ওপর বড় রকমের দখল তৈরি হয়। বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থাপনার বড় রকমের ঘাটতি সবারই জানা। তার মাধ্যমে গোষ্ঠীতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতার ব্যবহার করে বাজারকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি ঘটে। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের দাম কমায় অন্যান্য দেশে মূল্যস্ফীতির হার নিম্নমুখী হলেও বাংলাদেশে ঊর্ধ্বমুখী। দেশীয় পণ্যগুলোর ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য এবং অন্যদিকে আমদানির বাজারকে কাজ করতে না দেয়ার কারণে দ্রব্যমূল্য বেড়েই চলছে। অন্যান্য দেশে এমনকি শ্রীলংকায়ও মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু বাংলাদেশে মূল্যস্ফীতি কমছে না। দেখা যাচ্ছে কভিড-পরবর্তী সময়ে যে মূল্যস্ফীতি ঘটছে, তার সঙ্গে রাজস্ব নীতি এবং মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে কার্যকারণ জানা সত্ত্বেও সঠিক নীতিনির্ধারণ না করার জন্যই মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরা যাচ্ছে না। বাংলাদেশ নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো বিষয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-
জ্বালানি ও খাদ্যনিরাপত্তা। দেখা যায়, খাদ্য মূল্যস্ফীতি বেশি এবং এক্ষেত্রে নিরাপত্তাহীনতাও অধিক। আমদানি উৎসস্থলে বৈচিত্র্য না থাকায় খাদ্যপণ্যের আমদানি নির্দিষ্ট কিছু দেশ থেকে করা হচ্ছে। রফতানির ওপর বিধিনিষেধ জারি অথবা অধিক শুল্ক ধার্য করায় বাজারে দাম বেড়ে যায়। সাম্প্রতিক কালে চাল, পেঁয়াজ, মরিচের ক্ষেত্রে তা লক্ষ করা গেছে। আমদানি নীতিকাঠামোর মধ্যে ঘাটতি রয়েগেছে। আমদানি উৎস্যে বৈচিত্র্য না থাকায় বড় রকমের ঝুঁকি তৈরি হয় এবং মাঝেমধ্যেই সে ঝুঁকির বড় রকমের অভিঘাত সাধারণ মানুষের ওপর পড়ে।
যেহেতু বিশ্ববাজারে খাদ্যের উৎপাদন এবং দাম সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়, তা খাদ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের জানা থাকা সত্ত্বেও সঠিক সময়োপযোগী কার্যক্রম না নেয়ার কারণে খাদ্যনিরাপত্তা হুমকির মধ্যে পড়ে। কিন্ত জ্বালানি আমদানিনির্ভরতা অনেক বেশি এবং জ্বালানি নিরাপত্তার বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে উৎপাদন খরচ বাড়ছে। পরিবহন থেকে শুরু করে সর্বস্তরে প্রভাব পড়ে। ডলারের রিজার্ভ ধরে রাখার জন্য জোর করে আমদানি কমিয়ে রাখায় বিদেশী পণ্যগুলোয় সরবরাহজনিত ঘাটতির কারণে দাম বেড়ে যাচ্ছে। ডলারের সরবরাহ কম থাকায় টাকার বিপরীতে ডলারের দাম বাড়ায় তথা টাকার অবমূল্যায়নে আমদানি ব্যয় বেড়েছে। এভাবে উৎপাদনের খরচ বাড়ায় মূল্যস্ফীতি ঘটেই চলছে। অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ক্রমহ্রাসমান চাপ, ডলারের অভাব ও ডলারের মানের বৃদ্ধি ক্রমাগত মূল্যস্ফীতির অন্যতম প্রধান নিয়ামক। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আগে থেকেই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমছিল। গত বছরের আগের বছর আমদানির মাধ্যমে পুঁজি পাচারে বড় উল্লম্ফনের অভিযোগ রয়েছে। আবার গত অর্থবছরে রফতানির মাধ্যমে পুঁজি পাচারের অভিযোগ আছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হুন্ডি ও হাওলা। পুঁজি পাচার, হুন্ডি, হাওলাসহ অন্যান্য যেসব অভিযোগ রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে ব্যবস্থা না নেয়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমেই চলছে। এটি মোকাবেলার জন্য সঠিক পদক্ষেপ না নিয়ে জোর করে আমদানি কমিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। ৩১ দশমিক ১৯ শতাংশ আমদানি হ্রাস পেয়েছে। কাঁচামাল, মধ্যবর্তী পণ্য ও মূলধনি যন্ত্রপাতি আমদানি কমায় ভবিষ্যতে রফতানি বাণিজ্যের ওপর প্রভাব পড়বে। তেমনি বাংলাদেশের উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ফলে জনমানুষের আয়ের ওপর প্রভাব পড়বে।
অথচ মূল্য স্থিতিশীলতা রক্ষা করাই বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ম্যান্ডেট। মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষার মূল দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর বর্তায়। এই মৌল ম্যান্ডেট বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংক মূল্যস্ফীতির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মুদ্রা সরবরাহ, বৈদেশিক লেনদেন বিনিময় ও সুদের হার নির্ধারণসহ বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্ট ব্যবহার করে। যেমন, ডলারের ক্রমাবনতিশীল অবস্থাসংশ্লিষ্ট তথা পুঁজি পাচার, হাওলা ও হুন্ডিসংক্রান্ত যে অভিযোগগুলো করা হয়েছে, তা নিরসনে সঠিক কার্যকর পদক্ষেপের অনুপস্থিতি রয়েছে। জনমানুষ যখন দুর্দশায় নিমজ্জিত হয়, তখন রাজস্ব নীতি তথা রাষ্ট্রীয় সহায়তার মাধ্যমে তাদের জীবন ধারণ চালিয়ে যাওয়ার বিধান সারা পৃথিবীতেই করা হয়। তা সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি নামে অভিহিত হয়। যদিও তার বিস্তৃতি, প্রকৃতি একেক দেশে একেক রকম। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে যে সামাজিক সুরক্ষা জাল ব্যবস্থা বাংলাদেশে খণ্ড-বিখণ্ড। এটা বেশ বিক্ষিপ্ত এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নয়। সামাজিক সুরক্ষায় এখন পর্যন্ত কোনো সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। কার্যকর পদক্ষেপ থাকলে নগদ সহায়তা বা যতটুকু সহায়তা দেয়া হয় তা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ কর্মসূচি নেয়া হয়। সরকারের আর্থিক ক্ষমতা না থাকায় বিশেষ কর্মসূচি নিতে পারেনি। মূল্যস্ফীতি দীর্ঘমেয়াদি হওয়ার কথা ছিল না। এর পেছনের কারণগুলো সবই জানা। সরকার যদি সঠিক ব্যবস্থা নিতেন তাহলে এতদিন পর্যন্ত নিম্ন আয়ের, নির্দিষ্ট আয়ের দরিদ্র মানুষের এ রকম অবস্থায় নিপতিত হতে হতো না। কিন্তু ত্রুটিযুক্ত ব্যবস্থা থাকার কারণে দেখা যাচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে দরিদ্র মানুষের পরিমাণ বেড়ে গেছে। ফলে সরকারের আসলেই মূল্যস্ফীতির সময়ে কোনো বিশেষ পদক্ষেপ নেয়ার অবকাশ থাকছে না। মুশকিল হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানের যে দায়িত্ব পালন করা দরকার, সে দায়িত্ব পালনে তারা তাদের সক্ষমতা প্রমাণ করতে পারছেন না।
তার মাত্রা আরো বেড়ে যায় যখন জবাবদিহিহীতার সংস্কৃতি বিরাজমান থাকে না। প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দোবস্তের বড় রকমের সম্পর্ক আছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে দুটি মূল সংস্থার একটি বাংলাদেশ ব্যাংক। তাদের মূল ম্যান্ডেন্ট হচ্ছে প্রাইস স্ট্যাবিলিটি। কার্যকর সক্ষমতার প্রকাশ ঘটছে না। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের বা নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। দারিদ্র্যসীমার নিচে ধাবিত হওয়া মানুষের সংখ্যা অনেক এলাকায় বাড়ছে। তাদের মধ্যে পুষ্টিহীনতা বাড়ছে, খাদ্য গ্রহণ হ্রাস পাচ্ছে। তাদের শিক্ষা বাবদ ও স্বাস্থ্যগত ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে। আবার ঠিক হারে মজুরি পাচ্ছে না সংশ্লিষ্টরা। সবচেয়ে বড় ক্ষতি হচ্ছে সঞ্চয় হার কমে যাওয়ায় কারণে বিনিয়োগও কমছে। এতে আনুষ্ঠানিক খাতে নতুন কর্মসংস্থানও বাড়ছে না। যেটুকু কর্মসংস্থান তৈরি হচ্ছে তা অনানুষ্ঠানিক খাতে হচ্ছে। অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মসংস্থান কখনই টেকসই হতে পারে না। এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে দেশের মূল্যস্ফীতির এ ঊর্ধ্বগতি থামবে কবে?মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি রোধ করাই এখন অর্থনীতির অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। বর্তমান সরকারকে মেয়াদের শেষ বছরে এসে উচ্চ মূল্যস্ফীতির এই চাপ সামলাতে হবে। ভোটের বছরে মানুষের কাছে জিনিসপত্রের দাম বড় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এখন নিত্যপণ্যের দাম কীভাবে কমানো যাবে, সেদিকেই নজর দিতে হবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদরা। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কষ্ট লাঘবের জন্য সরকারকে বেশ কিছু সংস্কারমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। এছাড়াও সুশাসন, নিয়মতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও স্বচ্ছতা আনার জন্য কাঠামোগত সংস্কার বাস্তবায়নে মনোযোগ দিতে হবে।
লেখক: গবেষক ও কলাম লেখক
এমএসএম / এমএসএম

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
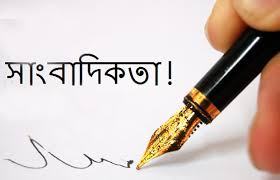
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

অকুতোভয় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা: ২২ বছরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল পরিকল্পনাকারীরা

বিতর্ক থেকে বিবর্তন: তারেক রহমানের রাজনৈতিক রূপান্তর

কুয়েত দূতাবাস সহ মধ্যপ্রাচ্য দূতাবাস গুলো সংস্কার অতি জরুরি

রাজনীতি মানেই কি ক্ষমতার লড়াই?

অধিক আসনের হিসাব না গ্রহণযোগ্য নির্বাচন- তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কোন পথে?

