রাজনৈতিক অস্থিরতা অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের জন্য বড় হুমকি

গত ১৪ বছরে দেশ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। বর্তমান সরকার ধারাবাহিকভাবে সরকার পরিচালনায় আছে বলেই এসব অর্জন সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ ২০৩০ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৯তম এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ২৩তম অর্থনীতিতে উন্নত দেশে পরিণত হবে। আর ২০২৬ সালেই বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালেই উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করবে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে তার বড় প্রমাণ হলো গত কয়েক বছর ধরে দেশের মানুষের মাথাপিছু আয় বেড়েছে। বর্তমান মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৮২৪ ডলার। অর্থনৈতিক অগ্রগতির সূচকে বিশ্বের শীর্ষ কয়েকটি দেশের একটি আজ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। মেট্রোরেল ও পদ্মা সেতু উদ্বোধন দুটিই উন্নয়নের মাইলফলক। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত-স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তোলার প্রত্যয়ে কাজ করছে। এজন্য প্রেক্ষিত পরিকল্পনা-২০৪১ প্রণয়ন করে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে। আজকে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হতে পেরেছে। কিন্ত প্রশ্ন উঠেছে, এতো উন্নয়নের পরও আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কেন এই বিদেশি চাপ আর কেনই বা দেশে এতো আন্দোলন ও হতাশার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে? এমনকি বাংলাদেশের সামনের দিনগুলো আরো কঠিন বা জটিল হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। যা গোটা জাতিকে একধরনের আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনায় দেশ ও জাতির চিন্তা মাথায় রেখেই রাজনীতিবিদদের মধ্যে শান্তির পথ খোঁজার ব্যবস্থা করতে হবে। মনে রাখতেই হবে, নিজেদের শান্তি নিজেরাই তৈরি করতে হবে, বিদেশিরা নয়। আমেরিকার ন্যাশনাল ব্যুরো অব ইকোনমিক রিসার্চের গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের রাজধানী শহর ঢাকাকে বিশ্বের সবচেয়ে ধীরগতির শহর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।
১৫২টি দেশের ১ হাজার ২০০টির বেশি শহরে যান চলাচলের গতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতগতির ২০টি শহরের ১৯টি যুক্তরাষ্ট্রের। একটি কানাডার অন্টারিও অঙ্গরাজ্যের উইন্ডসর। অন্যদিকে সবচেয়ে ধীরগতির ২০টি শহরের তালিকায় ঢাকার পরে রয়েছে নাইজেরিয়ার দুই শহর-লাগোস ও ইকোরোদু। ধীরগতির শহরের তালিকায় ঢাকা ছাড়াও বাংলাদেশের দুই শহর হচ্ছে-ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম। কলকাতা, মুম্বাইসহ ভারতের আটটি শহরও রয়েছে এই তালিকায়।
ঢাকা শহরের যানজট কমাতে ৩৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হচ্ছে প্রথম মেট্রোরেল। আরও দুটি মেট্রোরেল তৈরি করা হচ্ছে ৯৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে। ৯ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বানানো হচ্ছে এক্সপ্রেসওয়ে। প্রথম মেট্রোরেল ও এক্সপ্রেসওয়ে আংশিক চালু হয়েছে সম্প্রতি। এর আগে আটটি উড়ালসড়ক নির্মাণ করা হয়েছিল কয়েক হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে। উড়ালসড়ক ও এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে চট্টগ্রামেও। কিন্তু এই দুই শহরে সড়কে গতি আসেনি। সরকারের দাবি, ঢাকাসহ সারা দেশে যোগাযোগব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সেই উন্নয়নের জন্য কী মূল্য দেশকে দিতে হয়েছে এবং জনগণ কতটা সুফল পেয়েছে, সেটা ভাবার বিষয়। সরকার যখন ঢাকাকে সবকিছুর কেন্দ্র হিসেবে দেখছে, তখন এর গতির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। সিপিডির গবেষণায় দেখা যায়, প্রতিদিন ঢাকার নাগরিকদের সড়কে প্রতি ২ ঘণ্টায় ৪৬ মিনিট যানজটে আটকা থাকতে হয়। বছরে জনপ্রতি নষ্ট হয় ১২৬ ঘণ্টা। দেড় কোটি জন-অধ্যুষিত ঢাকা শহরে প্রতিদিন যে লাখ লাখ মানুষ চলাচল করে, তার খুব সামান্য অংশই মেট্রোরেল বা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের সুফল ভোগ করবে। বাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সহজ চলাচল নিশ্চিত করতে নীতিনির্ধারকদের ভাবনা কী? ঢাকা শহরের প্রবেশপথ গুলোর নাজুক অবস্থা সড়কের গতি আরও কমিয়ে দিয়েছে।
একটি শহরে কেবল বড় বড় উড়াল বা পাতাল সড়ক করলেই তো হবে না, সংযোগস্থলগুলোতেও চলা চলের মসৃণ ব্যবস্থা থাকতে হবে।যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও নগর-পরিকল্পনাবিদেরা ঢাকা শহরে জনজীবনে গতি আনতে বিকেন্দ্রীকরণ ও পরিকল্পিত নগরায়ণের ওপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু সরকারের নীতিনির্ধারকেরা এর কোনোটি আমলে নিয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁরা যখন উড়ালসড়ক করেছেন, মেট্রোরেলের কথা ভাবেননি। যখন মেট্রোরেল করেছেন, এক্সপ্রেসওয়ের কথা মনে রাখেননি। যানবাহনের সংখ্যা ও ধরন নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও তাদের কোনো হেলদোল আছে বলে মনে হয় না। আর সড়ক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে।কিছু অবকাঠামো বানানোই যেন সব, সড়ক ব্যবস্থাপনা যে গুরুত্বপূর্ণ, সেদিকে কোনো নজর নেই। ঢাকা শহরের জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং এই চাপ নেওয়ার ক্ষমতা শহরটির নেই। এমন একটি বাস্তবতায় উড়াল-পাতাল সড়ক ও মেট্রোরেল কতটা সুফল দেবে? উন্নয়নের সঙ্গে সড়কের গতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সরকারের উন্নয়ন-পরিকল্পনায় যদি সেই গতিই না বাড়ে, তাহলে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করা হলো কেন? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া যোগাযোগ খাতের প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলেই শহরে গতি ফিরে আসছে না। এবং যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ব্যক্তিগত কিংবা ছোট গাড়ির আধিক্যকে সড়কে গতি না আসার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। গণপরিবহন মসৃণ ও সাশ্রয়ী হলে ব্যক্তিগত গাড়ির ব্যবহার হয়তো কিছুটা কমবে। কিন্তু সরকারের নীতিনির্ধারকদের বুঝতে হবে বিকেন্দ্রীকরণ ছাড়া ঢাকা শহরকে গতিশীল করা যাবে না। রাষ্ট্রের একচেটিয়া শক্তি প্রয়োগের যে ক্ষমতা, তার ওপর ভর করে দেশে গোষ্ঠীতন্ত্রের শাসন কায়েম হয়েছে। গোষ্ঠীতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষার লক্ষ্য নিয়েই দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক কাঠামো কার্যকর ও পরিচালিত হচ্ছে।
কোন গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসনের ফলাফল কী হতে পারে, তা আমরা ব্যাংকব্যবস্থায় বিপর্যয়, ডলার-সংকট বা নিয়ন্ত্রণহীন মূল্যস্ফীতিতে লক্ষ করছি। অর্থাৎ রাষ্ট্রে এমন এক ধরনের স্বজনতোষী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে, যার মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করা যায়। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপরও একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কাজটিও রাষ্ট্রীয়ভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।
উন্নয়নের যে কথাটি তৈরি হয়েছে, তা নিজেই নিজের জায়গায় বন্দী হয়ে পড়েছে। ভোক্তাপর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে দেশে রাস্তাঘাট রাস্তাঘাট হচ্ছে, অন্যদিকে যানজট বাড়ছে। বাংলাদেশে অবকাঠামো তৈরির খরচ সবচেয়ে বেশি। একদিকে বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতা বাড়ছে, কিন্তু দাম বাড়ছে, লোডশেডিংও হচ্ছে, ক্যাপাসিটি ট্যাক্সের খরচ বাড়ছে। সবচেয়ে বেশি খরচ হচ্ছে যে ঢাকা শহরে সেখানে দারিদ্র্য বাড়ছে। বৈষম্য থামানো যাচ্ছে না। বিভিন্ন অর্থনৈতিক নির্দেশকে অনেক কিছুই বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে, যার সঙ্গে বাস্তবতার মিল নেই। দেখা যাচ্ছে জিডিপির অনুপাতে কর কম। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সূচকগুলো নেমে যাচ্ছে, তা দৃশ্যমান হচ্ছে। কর্মহীন প্রবৃদ্ধি থেকে বের হওয়ার পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এসব পরিস্থিতিই বাংলাদেশের নেতিবাচক ঋণমানের জন্য দায়ী। বাস্তবতা হচ্ছে আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারছে না। দেশে গোষ্ঠীতন্ত্রের যে শাসন কায়েম হয়েছে, তাদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার জন্যই প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করে যাচ্ছে।আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ফরেনসিক অডিট হলে বোঝা যাবে সেখানে কত ধরনের ও কোন মাত্রায় অনিয়ম হয়েছে।ব্যাংকগুলোর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ নিয়মনীতি মেনে কাজ করতে পারছে না। তারা কার্যত ব্যাংক পরিচালকদের কাছে জিম্মি। ঋণ দেওয়ার বিষয়টি তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।
এসব কারণে খেলাপি ঋণ বেড়েই চলেছে। আমরা দেখছি, সুবিধামতো খেলাপি ঋণের সংজ্ঞা বদল করা হচ্ছে। দুঃখজনকভাবে সুদের হার কমা বা বাড়ার সঙ্গে বিনিয়োগের কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
বাংলাদেশের অর্থনীতি ব্যক্তি খাত নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ঋণমানের পূর্বাভাস আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের ওপর নিশ্চিতভাবেই প্রভাব ফেলবে। তবে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়বে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) ওপর। এফডিআই এমনিতেই অনেক কমেছে। গত এক দশকে মোট দেশজ উৎপাদনে ব্যক্তি খাতের অংশগ্রহণ স্থবির ছিল, সম্প্রতি আরও কমে গেছে। এখন যখন দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ দরকার, তখন ঋণমানের নেতিবাচক অবস্থান অনেকটা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো। আমাদের আরও মনে রাখা দরকার, এখন পর্যন্ত আমাদের যে প্রবৃদ্ধি, তা ভোক্তাভিত্তিক। টেকসই প্রবৃদ্ধির দিকে যেতে হলে দরকার বিনিয়োগনির্ভর প্রবৃদ্ধি। এটা করা গেলেই কর্মস্থান বাড়ানো ও দারিদ্র্য দূর করার গতি বাড়তে পারে। আইনি কাঠামোর আওতায় দেশে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে, যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে নিজেদের গোষ্ঠীকে সহায়তা করা। নানা কৌশলে তাদের অর্থনৈতিক সুবিধা ভোগের সুযোগ দিয়ে যাওয়া। এবং এই কাজ করতে গিয়ে তারা জনগণের উন্নয়ন-আকাঙ্ক্ষাকে কাজে লাগাচ্ছে। এই পরিস্থিতি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বের জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতি ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে এখানে আলাদা করে দেখার সুযোগ নেই।এই পরিস্থিতি জনমনে গভীরদুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার জন্য দায়ী কারা, কে কোন ধরনের অনিয়ম করেছে, তা বাংলাদেশ ব্যাংকের অজানা নয়। এসবের প্রতিকার কী হতে পারে, সে ব্যাপারেও তাদের ধারণা রয়েছে। তারা চাইলে অনেক কিছু করতে পারে, কারণ তাদের স্বায়ত্তশাসন রয়েছে।
কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক তাদের এই স্বায়ত্তশাসনকে ব্যবহার করছে না। তারাও যেন গোষ্ঠিস্বার্থের অংশ হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম কাজ দ্রব্যমূল্য যৌক্তিক পর্যায়ে রাখা। জনগণের সঙ্গে এর মধ্য দিয়েই তারা সরাসরি সম্পৃক্ত। কিন্তু জনগণের সঙ্গে এই আস্থার সম্পর্কটি তারা স্থাপন করতে পারেনি। ব্যক্তি গভর্নরের ডি
গ্রেড পাওয়ার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংক তার স্বায়ত্তশাসনকে কাজে লাগাতে পারেনি এবং পারছে না। বরং অবস্থাদৃষ্টে এটা মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে বাংলাদেশ ব্যাংক বরং ঋণখেলাপি ও লুট পাটের সঙ্গে জড়িতদের স্বার্থ রক্ষার কাজেই ব্যস্ত রয়েছে। গত ছয় মাসে বিশ্বের বিভিন্ন ঋণমান পূর্বাভাসকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিবেচনায় বাংলাদেশের মান নিচে নেমেছে। এমন এক পরিস্থিতিতে বিষয়গুলো সামনে আসছে, যখন বাংলাদেশের অর্থনীতি আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল বা আইএমএফের বেলআউট প্যাকেজের আওতায় আছে। একসময় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের উন্নয়ন-বিস্ময় আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়েছিল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এই উন্নয়ন-বিস্ময় কি শেষ পর্যন্ত উন্নয়ন-বিপর্যয়-এর দিকে যাচ্ছে? আমাদের বুঝতে হবে কেন এই পরিস্থিতির তৈরি হলো।
লেখক: গবেষক ও কলাম লেখক
এমএসএম / এমএসএম

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
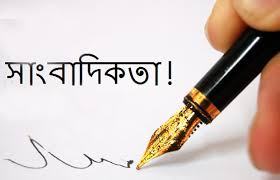
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

অকুতোভয় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা: ২২ বছরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল পরিকল্পনাকারীরা

বিতর্ক থেকে বিবর্তন: তারেক রহমানের রাজনৈতিক রূপান্তর

কুয়েত দূতাবাস সহ মধ্যপ্রাচ্য দূতাবাস গুলো সংস্কার অতি জরুরি

রাজনীতি মানেই কি ক্ষমতার লড়াই?

অধিক আসনের হিসাব না গ্রহণযোগ্য নির্বাচন- তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কোন পথে?

