উদ্বেগ আর আশঙ্কার মধ্যে অর্থনীতির যাত্রা

বিশ্ব অর্থনীতি নিয়ে ভালো কোনো পূর্বাভাস নেই।দেশের মধ্যেও সূচকগুলো আরও দুর্বল হচ্ছে।অর্থনৈতিক সংকট কেটে যাওয়ার কোনো লক্ষণ নেই। বরং তা আরও গভীর ও দীর্ঘ হচ্ছে। অর্থনীতির অনেকগুলো সূচকই আরও দুর্বল হয়েছে। জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকট আরও বেড়েছে। খাদ্য সংকটের আশঙ্কা বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়েই। চলতি বছরে বৈদেশিক মুদ্রার মজুত বা রিজার্ভ কমেছে ১১ বিলিয়ন ডলার বা ১ হাজার ১০০ কোটি ডলারেরও বেশি। রপ্তানি ও প্রবাসী আয়ের গতি কমেছে। বৈদেশিক মুদ্রা আয় কম বলে লেনদেনের ঘাটতি এখন রেকর্ড পরিমাণ। সাধারণ মানুষের সবচেয়ে বড় সমস্যা এখন মূল্যস্ফীতি। এতে জীবনযাপনের খরচ বেড়ে গেছে, কমেছে প্রকৃত আয়। উদ্যোক্তাদের জন্য বড় সমস্যা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট। বাংলাদেশ ব্যাংক এখনো হিমশিম খাচ্ছে ডলার নিয়ে। সরকারের আয়ও কম। ফলে ভর্তুকির বরাদ্দও বাড়াতে পারছে না। বিশ্ব অর্থনীতি নিয়েও কোনো ভালো কোনো পূর্বাভাস নেই।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগ্রাসী ভাবে চলতি বছরেই ছয়বার নীতি সুদের হার বাড়িয়েছে। তারপরও মূল্যস্ফীতি তেমন কমছে না। বরং এর ফলে বিশ্বমন্দার আশঙ্কা আরও বাড়ছে।আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বলছে,খারাপ সময় আসা এখনো আরও বাকি। সদ্য বিদায়ি সেপ্টেম্বরে প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্সে বৃহৎ পতন আমাদের জাতীয় অর্থনীতির জন্য নিঃসন্দেহে বিপদ সংকেত।বিভিন্ন প্রতিবেদন বলছে, গত মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রবাসীরা দেশে ১৩৪ কোটি ৩৬ লক্ষ ডলারের সমপরিমাণ অর্থ পাঠিয়েছেন,যা গত ৪১ মাসে সর্বনিম্ন।রেমিট্যান্সের এই পতন এমন সময়ে ঘটিল যখন দেশের রপ্তানি আয়ে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি হচ্ছে না। অতএব ক্ষীয়মাণ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পুনর্ভরণ এবং আমদানি বিল পরিশোধের জন্য রেমিট্যান্সই প্রধান ভরসা।
এই অবস্থা অব্যাহত থাকলে রাষ্ট্রীয় ও বেসরকারি খাতের জন্য বিভিন্ন সময়ে গৃহীত বৈদেশিক ঋণ পরিশোধেও সংকট সৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে বিশ্বপরিসরে বাংলা দেশের ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা সম্পর্কেও প্রশ্নের জন্ম দিবে, যা আবার নূতন বৈদেশিক ঋণ ও বিনিয়োগপ্রাপ্তি কঠিন করে তুলতে পারে, যার পরিণামে প্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলে বৈদেশিক মুদ্রা বিশেষত ডলার প্রবাহ আরও হ্রাস পেতে পারে। এই ঘূর্ণায়মান সংকটের জন্য অর্থনীতিবিদরা বরাবরই সরকারের ভুল আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনা নীতিকে দায়ী করে আসছেন। তাদের অভিযোগ, একদিকে বিশেষত গত এক দশকে বাংলাদেশ ব্যাংকের দুর্বল নজরদারির সুযোগে ব্যাংকিং খাত হতে প্রভাবশালী মহল ঋণের নামে শত সহস্র কোটি টাকা লুট করে বিদেশে পাচার করেছে; অপরদিকে এই চক্রেরই সুবিধার্থে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় ডলারের মূল্য সরকারি চ্যানেলে কম রাখা হয়েছে। তাহাদের অভিমত, এই কারণেই ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট ডলার সংকট হতে অপরাপর দেশ বাজারনির্ভর ডলার ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে ইতোমধ্যে অনেকটা মুক্ত হলেও বাংলাদেশ এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে। বিদ্যমান ডলার ক্রয়-বিক্রয় প্রক্রিয়ার কারণে গত সেপ্টেম্বরে ব্যাংক অপেক্ষা খোলাবাজারে ডলারের মূল্য ৬ থেকে ৭ টাকা বেশি ছিল। স্বাভাবিকভাবেই প্রবাসীরা দেশে টাকা পাঠাতে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় অধিকতর হারে হুন্ডির দ্বারস্থ হয়েছেন। সমস্যার টেকসই সমাধান হিসেবে ব্যাংক ও আর্থিক ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কার অবশ্যই জরুরি। তবে আপাতত ডলারের বিনিময় হার বাজারের উপর ছেড়ে দেয়ার বিকল্প নেই। একই সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক চ্যানেলে রেমিট্যান্সপ্রাপ্তির সুবিধা ও গুরুত্ব সম্পর্কে প্রবাসীদের সচেতন করতে জোরালো পদক্ষেপ নিতে হবে। ডলারের সংকট কাটাতে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে ৪৭০ কোটি ডলার ঋণসহায়তা নিচ্ছে সরকার।
এরই মধ্যে প্রথম কিস্তি পেয়েছে এবং দ্বিতীয় কিস্তির আলাপ চলছে। ঋণপ্রাপ্তির শর্তের মধ্যে খেলাপি ঋণ কমিয়ে আনার ওপর জোর দিয়েছে আইএমএফ। বিশেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের পরিমাণ হ্রাসে জোর তাগিদ দিয়ে আসছে বহুজাতিক সংস্থাটি। যদিও প্রাপ্ত তথ্য বলছে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণ কমার চেয়ে উল্টো বেড়েই চলেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক গুলো আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আওতায় না থেকে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকছে। এতে ওই ব্যাংকগুলোয় বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ কতটুকু আছে তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, ২০২২ সালের ডিসেম্বর শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লাখ ২০ হাজার ৬৫৬ কোটি টাকা। চলতি বছরের জুন শেষে এ খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১ লাখ ৫৬ হাজার ৩৯ কোটি টাকায় গিয়ে ঠেকেছে। সে হিসাবে, চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসেই ৩৫ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকার খেলাপি ঋণ বাড়ল। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত বছর শেষে দেশের ব্যাংক খাতের পুনঃতফসিলকৃত ঋণের স্থিতি ছিল ২ লাখ ১২ হাজার ৭৮০ কোটি টাকা, যা ব্যাংকগুলোর বিতরণকৃত মোট ঋণের ১৪ দশমিক ৪০ শতাংশ। খেলাপি ও পুনঃতফসিলকৃত ঋণকে দুর্দশাগ্রস্ত হিসেবে দেখায় আইএমএফ। এ হিসাবে দেশের ব্যাংকগুলোর ‘দুর্দশাগ্রস্ত’ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩ লাখ ৬৮ হাজার ৮১৯ কোটি টাকা। অন্যদিকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় আদায় অযোগ্য হওয়ায় ব্যাংকগুলো ৬৫ হাজার ৩২১ কোটি টাকার ঋণ অবলোপনও করেছে। সব মিলিয়ে দেশের ব্যাংক খাতের এক-চতুর্থাংশের বেশি ঋণ এখন দুর্দশাগ্রস্ত। দেশের মূল্যস্ফীতি হারের বিপরীতে আমাদের প্রতিবেশী দেশ গুলোসহ বিশ্বের অনেক দেশে বিদ্যমান মূল্যস্ফীতি হারে দেখা যায়, চলতি বছরের আগস্টে বার্ষিক ভিত্তিতে ভারতে খুচরা মূল্যস্ফীতি কমে ৬ দশমিক ৮৩ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জুলাইয়ে দেশটিতে মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ৭ দশমিক ৪ শতাংশে।
গত ১৩ সেপ্টেম্বর এমন তথ্য প্রকাশ করেছে ভারত সরকার। অর্থনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত শ্রীলংকায় মূল্যস্ফীতির হার গত দুই বছরের মধ্যে এই প্রথম এক অংকের ঘরে নেমে এসেছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে দেশটির মূল্যস্ফীতি ছিল ৬৯ দশমিক ৮ শতাংশ, যা চলতি বছরের জুলাইয়ে ৬ দশমিক ৩ শতাংশে নেমে আসে মর্মে দেশটির স্ট্যাটিস্টিকস ডিপার্টমেন্ট নিশ্চিত করেছে। অন্য এক সূত্রে জানা যায়, আগস্টে এ হার ৪ শতাংশে নেমে এসেছে। নেপাল রাষ্ট্র ব্যাংক সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের জুনে দেশটিতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ, যা গত বছরের একই সময় ছিল ৮ দশমিক ৫৬ শতাংশ। ব্যাংক অব থাইল্যান্ডের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২২ সালে থাইল্যান্ডে মূল্যস্ফীতির হার ৬ শতাংশের কিছু ওপরে আটকে রাখতে সক্ষম হয় থাই কেন্দ্রীয় ব্যাংক। চলতি বছর আরো নিয়ন্ত্রিত অবস্থানে চলে এসেছে মূল্যস্ফীতি। ২০২৩ সাল শেষে থাইল্যান্ডে মূল্যস্ফীতির হার আড়াই শতাংশে আটকে রাখার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সূত্রের বরাত দিয়ে ১৪ জুলাই প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নজির বিহীন ঊর্ধ্বগতির পর মূল্যস্ফীতিতে ইতিবাচক প্রবণতা দেখা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। দেশটিতে দুই বছরে সর্বনিম্ন হয়েছে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির হার। দেশটির শ্রম মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুসারে, ২০২২ সালের জুনে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৯ দশমিক ১ শতাংশ। চলতি বছরের জুলাইয়ে মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়ায় ৩ দশমিক ২ শতাংশে। ২০২১ সালের মার্চের পর এ মূল্যস্ফীতি হার সর্বনিম্ন। যুক্তরাজ্যের সরকারি হিসাবের বরাত দিয়ে ১৬ আগস্টের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরের জুলাইয়ে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক মূল্যস্ফীতির হার কমে ১৫ মাসের মধ্যে সর্বনিম্ন হয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার জুনের ৭ দশমিক ৯ থেকে কমে ৬ দশমিক ৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের মে মাসে যুক্তরাজ্যে বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ছিল ৯ দশমিক ১ শতাংশ, যা গত ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ।
কানাডার পরিসংখ্যান বিভাগের হিসাবে ২০২২ সালের জুনে মূল্যস্ফীতি বেড়ে ৮ দশমিক ১ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০২৩ সালের জুলাইয়ে কানাডায় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ২৭ শতাংশে। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, অস্ট্রেলিয়ায় চলতি বছরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে মূল্যস্ফীতি ৬ শতাংশে নেমে এসেছে, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৭ শতাংশ। অস্ট্রেলিয়ার রিজার্ভ ব্যাংক গভর্নর ফিলিপ লোই আশা প্রকাশ করেছেন, ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ দেশটিতে মূল্যস্ফীতির হার প্রায় ৩ দশমিক ২৫ শতাংশে নেমে আসবে। খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতির উল্লম্ফন কেন ভীতিকর তা নিয়ে আলোকপাত করা যাক। জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণগুলোর শীর্ষে অবস্থান খাদ্যের। আবার খাদ্যের বেশ কয়েকটি উপাদান থাকলেও দেশে খাদ্য বলতে মূলত চাল থেকে তৈরি ভাতকে বোঝায়। ভাত দেশের কমবেশি ৯০ শতাংশ মানুষের প্রধান খাদ্য। ভাত আমাদের ক্যালরির প্রধান উৎস। গত প্রায় দুই যুগে চালের দাম বেড়েছে চার-পাঁচ গুণ। একাধিক কারণে চালের উচ্চমূল্য সাধারণ মানুষের জীবনে ভীতিকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিবিএসের হিসাবে জাতীয় পর্যায়ে একটি পরিবারের মাসিক মোট ব্যয়ের ৫৪ দশমিক ৮১ শতাংশ খরচ হয় খাদ্যে। আবার মাসিক মোট খরচের ৩৫ দশমিক ৯৬ শতাংশ ব্যয় হয় চাল কেনায়।তাই চালের মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের দুর্ভোগ বাড়ছে। চালের মূল্যবৃদ্ধি, বিশেষ করে মোটা চালের মূল্যবৃদ্ধির ক্ষতিকর প্রভাব ওই চালের সব শ্রেণীর ভোক্তার ওপর পড়লেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে নিম্ন আয়ের মানুষ। এবং শুধু নিম্ন আয়ের মানুষ নয়,চালের দাম বৃদ্ধিতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মধ্যবিত্তরা- ও বিশেষ করে যাদের আয় নির্দিষ্ট। চালের মূল্যস্ফীতির কারণে মধ্যবিত্তদের মাছ-মাংস, ডিমসহ আমিষজাতীয় খাবার কেনা কমিয়ে দিতে হচ্ছে। এতে তাদের পরিবারে, বিশেষ করে শিশু ও মহিলাদের পুষ্টির অভাব ঘটছে। চাল ছাড়াও অন্যান্য খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতির খারাপ প্রভাব পড়েছে জনগণের মধ্যে।
এদিকে খাদ্যপণ্যের মূল্যস্ফীতির হার যখন গত সাড়ে ১১ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ, তখন মজুরি বৃদ্ধির হার মূল্যস্ফীতি হারের অনেক নিচে। অথচ মজুরি বৃদ্ধির হার মাত্র ৭ দশমিক ৫৮ শতাংশ। যাইহোক, দেশে মূল্যস্ফীতির হার, বিশেষ করে খাদ্যপণ্যে মূল্যস্ফীতির রেকর্ড হার হ্রাসে সরকারকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। সার্বিক মূল্যস্ফীতিসহ খাদ্যপণ্যের রেকর্ড মূল্যস্ফীতি কমানো না গেলে সমাজে শ্রেণীবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটতে পারে।অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বহুদিন ধরে অর্থনীতিতে নানারকম যে নীতি নেয়া হয়েছে, তার ফলে আস্তে আস্তে ঝুঁকি তৈরি হচ্ছিল। কোভিডের সময় সেসব ঝুঁকি প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। এরপর সেটা সমাধানের কোন উদ্যোগ না নেয়ায় ক্রমাগত বেড়ে এখন বড় ধরনের চাপ তৈরি করেছে। বিশেষ করে কঠোর নীতির অভাবে ব্যাংকিং খাত নাজুক হয়ে পড়েছে। খেলাপি ঋণ বেড়েছে। নিয়মনীতি না মেনে কিছু গোষ্ঠীর কাছে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে, ফলে পুরো ব্যাংকিং খাতে চরম অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়েছে। অনিয়ম দেখার পরেও এক্ষেত্রে সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি,যার খেসারত বহন করতে হচ্ছে সাধারণ জনগণকে।
লেখক: গবেষক ও কলাম লেখক
এমএসএম / এমএসএম

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
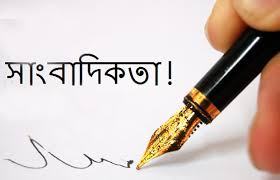
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

অকুতোভয় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা: ২২ বছরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল পরিকল্পনাকারীরা

বিতর্ক থেকে বিবর্তন: তারেক রহমানের রাজনৈতিক রূপান্তর

কুয়েত দূতাবাস সহ মধ্যপ্রাচ্য দূতাবাস গুলো সংস্কার অতি জরুরি

রাজনীতি মানেই কি ক্ষমতার লড়াই?

অধিক আসনের হিসাব না গ্রহণযোগ্য নির্বাচন- তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কোন পথে?

