চীন-মার্কিন দ্বন্দ্বে বিভক্তির ঝুঁকিতে বিশ্ব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি এবং বার্লিন প্রাচীরের পতনের মধ্যবর্তী সময়ে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাকে নিজেদের মতো করে সংজ্ঞায়িত করা বিশ্বের দুই প্রধান শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আদর্শগতভাবে দ্বন্দ্বরত থেকেছে। এই দ্বন্দ্ব গোটা বিশ্বকে দুটো শিবিরে বিভক্ত করেছিল। এর জের ধরে বিশ্বে স্বাধীনতা চাওয়া দেশের সংখ্যাও বেড়েছে। ১৯৪৫ সালে স্বাধীনতা চাওয়া দেশের সংখ্যা ছিল ৫০। ১৯৮৯-৯১ সালে সেই সংখ্যা দেড় শর বেশি হয়ে দাঁড়ায়। যখন দুটি শক্তির মিথস্ক্রিয়া জারি ছিল, তখন মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব সামনের দিকে উঠে আসছিল। স্বাধীনতার সংগ্রামগুলো প্রায়ই প্রক্সিযুদ্ধে রূপ নিচ্ছিল এবং দেশগুলোকে হয় যেকোনো একটি শিবিরে যোগ দিতে হচ্ছিল, নয়তো তাদের নিজেদের জোটনিরপেক্ষ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে বাধ্য করা হয়েছিল। বর্তমানে ঠিক একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে যাচ্ছে বলে যুক্তরাষ্ট্র মনে করছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র তার সবচেয়ে শক্তিধর ও সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের মুখোমুখি হয়ে নিজ মিত্রদের নিয়ে বেইজিংবিরোধী কৌশল অবলম্বন করছে।সেই কৌশলের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা অর্থনৈতিকভাবে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং ঝুঁকিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গুলোর লেনদেন বাতিল করার নীতি গ্রহণ করেছে। এটি আদতে শীতল যুদ্ধের সময়কার নিয়ন্ত্রণ নীতিরই একটি অর্থনৈতিক সংস্করণ। এবারের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৮তম অধিবেশনে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেছেন, ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়তে থাকায় বিশ্ব ক্রমে অস্থির হয়ে উঠেছে। ফলে ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে হচ্ছে।
বৈশ্বিক ব্যবস্থা এমন এক সময়ে পশ্চাৎপদ অবস্থান নিয়েছে, যখন শক্তিশালী, আধুনিক ও বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর আগের চেয়ে বেশি প্রয়োজন রয়েছে। যদি প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্বকে তার মতো করে প্রতিনিধিত্ব না করে, তাহলে আমরা কার্যকর ভাবে সমস্যার সমাধান করতে পারি না। সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে, প্রতিষ্ঠান গুলো সমস্যার অংশ হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে।জাতিসংঘ মহাসচিব আরও বলেন, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি; উত্তর ও দক্ষিণ এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বিভক্তি গভীরতর হচ্ছে। অর্থনৈতিক ও আর্থিক ব্যবস্থা আর বাণিজ্যিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এযাবৎকালের সবচেয়ে বেশি বিভক্তির দিকে এগোচ্ছে বিশ্ব। প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নিয়ে বিভক্ত কৌশল একক ও উন্মুক্ত ইন্টারনেট ব্যবস্থাকে হুমকিতে ফেলছে এবং নিরাপত্তা কাঠামোয় সম্ভাব্য সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি তৈরি করছে। আজকের বিশ্বব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যস্ত যে আমেরিকা নিজের ও বিশ্ব অর্থনীতির ব্যাপক ক্ষতি না করে চীন থেকে তার বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পূর্ণভাবে তুলে আনতে পারবে না। অধিকন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এখন শুধু কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রসারের দ্বারা হুমকি বোধ করছে না; তারা অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরতায় পরিচালিত বিশ্বব্যবস্থার হুমকি নিয়েও চিন্তিত। নিরাপত্তা-সংক্রান্ত কারণে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র চাইলে আংশিক বিচ্ছিন্ন হতে পারে; কিন্তু সামগ্রিকভাবে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত লোকসান জনক হবে। যুক্তরাষ্ট্রের খুব কমসংখ্যক মিত্রই এই নীতি অনুসরণ করতে রাজি হবে। কারণ, অধিক সংখ্যক দেশ তাদের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে চীনকে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। এ ছাড়া পারস্পরিক নির্ভরতার পরিবেশগত এমন কিছু দিক রয়েছে, যা চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্ন হওয়াকে অসম্ভব করে তোলে।
কোনো দেশ একাই জলবায়ু পরিবর্তন, মহামারি হুমকি বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সমস্যা মোকাবিলা করতে পারে না। ভালো হোক খারাপ হোক, আমরা চীনের সঙ্গে একটি সহযোগী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আটকে আছি। ফলে এই পরিস্থিতিকে শীতল যুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা চলে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে ক্ষমতার যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলছে, সেটিকে চলতি শতাব্দীর প্রথমার্ধের একটি সংজ্ঞা নির্ধারণী বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। তবে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে ঠিক কোন ধরনের সংজ্ঞায় আটকানো উচিত হবে, তা নিয়ে খুব কম লোকই একমত হতে পেরেছেন। কেউ কেউ এটিকে গত শতাব্দীর দুটি বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানি ও ব্রিটেনের মধ্যে শুরু হওয়া দীর্ঘ দ্বন্দ্বের মতো একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলে অভিহিত করেছেন। আবার অন্যরা আশঙ্কা করছেন, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে স্পার্টা ও এথেন্সের মধ্যে যে আদলে যুদ্ধ হয়েছিল, আমেরিকা ও চীন সেই ধরনের যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছে। সমস্যা হলো, যুক্তরাষ্ট্র-চীন সংঘাত অনিবার্য-এমন একটি ধারণা সবার মনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাস্তব হয়ে ওঠা একটি ভবিষ্যদ্বাণীতে রূপ নিতে পারে। তবে দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিজেই একটি বিভ্রান্তিকর শব্দবন্ধ। ১৯৪৯ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিসি) ক্ষমতায় আসার পর থেকে চীন-আমেরিকা সম্পর্ক যতগুলো ধাপ পেরিয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে একটু চিন্তা করলে দেখা যায়। ১৯৫০-এর দশকে কোরীয় উপদ্বীপে আমেরিকান ও চীনা সেনারা পরস্পরকে হত্যা করেছে। এরপর ১৯৭০-এর দশকে চীনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের ঐতিহাসিক সফরের সুবাদে এই দুই দেশ কাছাকাছি এসেছিল। এই সময়টাতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভারসাম্যমূলক জায়গায় আটকে রাখতে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে শুরু করে।
১৯৯০-এর দশকে দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক যুক্ততা বাড়তে থাকে। এর সূত্র ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় চীনের অন্তর্ভুক্তিকে সমর্থন দিয়েছিল। এখন যুক্তরাষ্ট্রের নেতারা চীনকে যেভাবে মার্কিন অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামরিক ব্যবস্থার জন্য ধাবমান হুমকি বলে অভিহিত করছেন, ২০১৬ সালের আগে এমনটি ছিল না। যদি এই দুই দেশের মধ্যকার দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ পর্যন্ত সহিংস সংঘাতে নাও গড়ায়, তাহলেও তাদের মধ্যে যে শীতল যুদ্ধ চলমান থাকছে, তার কী হবে? দীর্ঘস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বিতা-এই শব্দবন্ধ দিয়ে যদি সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে বলা যায়, বিশ্ব ইতিমধ্যে সে অবস্থার মধ্যে আছে। তবে যদি ঐতিহাসিক তুলনার জায়গা থেকে দেখি, তাহলে মার্কিন-চীন সম্পর্কের চ্যালেঞ্জগুলো সম্পর্কে আমাদের বিভ্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আছে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বৈশ্বিক পরিসরে উচ্চ স্তরের সামরিক নির্ভরশীলতা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কার্যত কোনো অর্থনৈতিক, সামাজিক বা পরিবেশগত পরস্পর-নির্ভরতা ছিল না। সেই দিক থেকে দেখলে বোঝা যাবে, আজকের চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক একেবারে ভিন্ন। চীন ও রাশিয়ার প্রভাবকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা যেতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা করতে সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মিত্র দেশ জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার নেতাদের সঙ্গে ক্যাম্প ডেভিডে বৈঠক করেছেন। বিশেষ করে আফ্রিকার সাহেল অঞ্চলের দেশগুলোতে রাশিয়ার প্রভাবে যেভাবে একের পর এক অভ্যুত্থান হয়েছে, তা নিয়ে বাইডেন ও তাঁর মিত্ররা উদ্বিগ্ন হয়ে এই ধারা কীভাবে ঠেকানো যাবে, সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন।
অন্যদিকে, সম্প্রতি ব্রিকসভুক্ত দেশ ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চীন ও দক্ষিণ আফ্রিকার নেতারা জোহানেসবার্গে মিলিত হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গুলোতে পশ্চিমাদের খবরদারির তীব্র সমালোচনা করেছেন।
শীতল যুদ্ধ সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তারা এর আগে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তা যে বাস্তব অবস্থায় চলে এসেছে, এখন তার প্রমাণ মিলছে। আজকের দিনে পশ্চিমের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা হলো চীন, সোভিয়েত ইউনিয়ন নয়; পশ্চিমের সামনে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্রিকস, ওয়ার শ প্যাক্ট নয়। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র আদর্শগত মেরুকরণের মধ্য দিয়ে আদল পেতে শুরু করা দ্বিতীয় স্নায়ুযুদ্ধের আশঙ্কা করছে। অন্যদিকে চীন বৈশ্বিক বিভক্তির ওপর বাজি ধরে সেটিকেই কাজে লাগাতে চাইছে বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, চীন অ-পশ্চিমা দেশগুলোকে জি-৭ কিংবা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের মতো পশ্চিমা আধিপত্যের অধীনে থাকা সংস্থাগুলোর বিকল্প কিছু গড়ার চেষ্টা করেছে। চীন একটি বহু মেরুভিত্তিক বিশ্ব চায়। চীন জানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন শিবিরের সঙ্গে তারা লড়াইয়ে পেরে উঠবে না। তবে প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে তারা অন্তত একটি খণ্ডিত বৈশ্বিক ব্যবস্থায় একটি পরাশক্তি হিসেবে জায়গা করে নিতে পারবে। মার্কিন নেতাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা জারি থাকার পরও যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্ররাও মার্কিন ব্লক থেকে খণ্ডিত হওয়ার প্রবণতা থেকে মুক্ত হতে পারছে না। এটি যুক্তরাষ্ট্রকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছে। গত বছরে সম্ভবত সবচেয়ে বড় চমক ছিল ব্রিকসের এই ঘোষণা: আর্জেন্টিনা, মিসর, ইথিওপিয়া, ইরান, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত-এই ছয় দেশ আগামী বছরের শুরুতেই পূর্ণ সদস্য হয়ে উঠবে। চীনের নেতাদের মনে এটি নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি নেই যে ব্রিকসের মধ্য দিয়ে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশগুলো অধিকতর পশ্চিমাবিরোধী হয়ে উঠবে। এতে চীন তার লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগোবে। ব্রিকসে যোগদান এই দেশগুলোর জন্য কাজের স্বাধীনতা বাড়াবে।
এবং এর মাধ্যমে তাদের অর্থায়নের বিকল্প উৎস বাড়বে; প্রকৃত অর্থেই মার্কিন ডলারের বিকল্প হিসেবে অন্য মুদ্রার ব্যবহার বাড়বে এবং বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে।
এই ধরনের সংগঠনের মাধ্যমে এমন একটি বিশ্বব্যবস্থা তৈরির স্বপ্ন দেখা হচ্ছে, যা পশ্চিমাদের ওপর নির্ভরশীল নয়। তার মানে সেটি হবে চীনের ওপর নির্ভরশীল।আর এটি যুক্তরাষ্ট্রের মাথাব্যথার বড় কারণ। তাই নতুন একটি শীতল যুদ্ধাবস্থা অনেকটাই ঘনিয়ে এসেছে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। যদিও বিদ্যমান বিশ্ব ব্যবস্থায় খন্ড খন্ড অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক বিকল্প তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তা ছাড়া এটি পশ্চিমের সঙ্গে আরও উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। যাহোক,এখন শুধুই অপেক্ষার পালা। বিশ্ব কি বিভক্তির দিকে যাচ্ছে, নাকি সমঝোতার মধ্য দিয়ে এগোচ্ছে? তা সময়ই বলে দেবে।
এমএসএম / এমএসএম

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
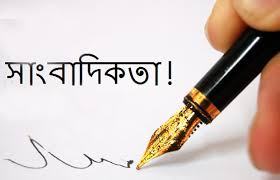
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

অকুতোভয় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা: ২২ বছরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল পরিকল্পনাকারীরা

বিতর্ক থেকে বিবর্তন: তারেক রহমানের রাজনৈতিক রূপান্তর

কুয়েত দূতাবাস সহ মধ্যপ্রাচ্য দূতাবাস গুলো সংস্কার অতি জরুরি

রাজনীতি মানেই কি ক্ষমতার লড়াই?

অধিক আসনের হিসাব না গ্রহণযোগ্য নির্বাচন- তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি কোন পথে?

