রাজনীতিতে রাজা আছে, নীতি নাই

মানবসভ্যতার ইতিহাসে রাজনীতি একটি অপরিহার্য অঙ্গ। রাষ্ট্র, শাসনব্যবস্থা ও সামাজিক সংগঠন, সবই রাজনীতির অন্তর্গত। রাজনীতির মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত জনগণের কল্যাণ, ন্যায় প্রতিষ্ঠা, সামাজিক স্থিতি রক্ষা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তবে রাজনীতি বহু সময়েই তার এই মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ফলে প্রশ্ন জেগেছে, “রাজনীতিতে রাজা আছে, নীতি নাই।”
এই প্রবাদবাক্যের অর্থ হলো, রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী বা শাসক উপস্থিত থাকলেও শাসনের নৈতিক ভিত্তি অনুপস্থিত। ক্ষমতার কেন্দ্রে যে ব্যক্তিই থাকুন না কেন, যদি নীতি-নৈতিকতা, স্বচ্ছতা ও জনকল্যাণের প্রতি দায়বদ্ধতা না থাকে, তবে রাজনীতি পরিণত হয় নিছক ব্যক্তিস্বার্থের খেলায়।
এই প্রবন্ধে রাজনীতি ও নীতির পারস্পরিক সম্পর্ক, ইতিহাসে নীতিহীন রাজনীতির উদাহরণ, আধুনিক বিশ্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার অভিজ্ঞতা, এর প্রভাব ও সম্ভাব্য সমাধান নিয়ে আলোচনা করছি।
১ : রাজনীতি ও নীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি:
১.১. রাজনীতির সংজ্ঞা:
রাজনীতি শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ ”পলিস” থেকে, যার অর্থ নগররাষ্ট্র। অ্যারিস্টটল রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন মানুষের সমষ্টিগত কল্যাণের জন্য সংগঠিত শাসনব্যবস্থা হিসেবে। তাঁর মতে, “মানুষ একটি রাজনৈতিক প্রাণী” অর্থাৎ মানুষ সমাজে বাস করে, আর সমাজকে সংগঠিত করার জন্য রাজনীতি অপরিহার্য।
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন ক্ষমতার বণ্টন ও প্রয়োগের প্রক্রিয়া হিসেবে, অর্থাৎ রাজনীতি হলো কে কী পাবে, কবে পাবে এবং কিভাবে পাবে, এই প্রশ্নের উত্তর।
১.২. নীতির সংজ্ঞা:
নীতি শব্দটি এসেছে গ্রিক ’ইথোস’ থেকে, যার অর্থ চরিত্র, অভ্যাস বা নৈতিকতা। নীতি হলো ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কর্তব্য-অকর্তব্যের মধ্যে সঠিক পথ নির্বাচন করার দিকনির্দেশনা। দর্শনশাস্ত্রে নীতি হলো সেই মূলনীতি যা মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।
নীতি ছাড়া রাজনীতি হলে তা হয়ে ওঠে কৌশল, প্রতারণা ও ক্ষমতার নগ্ন খেলা। তাই দার্শনিকরা বারবার রাজনীতিতে নীতির গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন।
১.৩. রাজনীতি ও নীতির সম্পর্ক:
রাজনীতি ও নীতি দুটি ভিন্ন ধারণা হলেও তাদের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। রাজনৈতিক নেতৃত্বের উদ্দেশ্য যদি হয় জনকল্যাণ, তবে নীতিই সেই পথপ্রদর্শক। কিন্তু যদি নীতি অনুপস্থিত থাকে, তবে রাজনীতি হয়ে যায় নিছক ক্ষমতার প্রতিযোগিতা।
প্লেটো তাঁর ’রিপাবলিক’ গ্রন্থে ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, শাসক হবেন দার্শনিক-রাজা (ফিলোসোফার কিং), যিনি নীতি ও জ্ঞান দিয়ে শাসন করবেন।
অ্যারিস্টটল ন্যায়ের ভিত্তিতে রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক সজ্ঞা হলো, রাষ্ট্র হলো এমন একটি সংগঠন যা সদস্যদের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও উত্তম জীবন যাপনে সক্ষম করে তোলে, যেখানে শাসনকার্যের মূল লক্ষ্য হলো সাধারণ কল্যাণ নিশ্চিত করা। তিনি মনে করতেন, মানুষ স্বভাবতই একটি রাজনৈতিক প্রাণী, একা বসবাস করলে হয় পশু বা ঈশ্বর হবে, তাই রাষ্ট্র গঠনের মাধ্যমে মানুষ তার পূর্ণতা লাভ করে। তিনি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে শাসকের সংখ্যা এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করেছেন: রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, রাষ্ট্রব্যবস্থা (সাধারণ কল্যাণ) এবং তাদের বিকৃত রূপ যেমন স্বৈরাচার, অভিজাততন্ত্র, এবং গণতন্ত্র।
কনফুসিয়াস নৈতিক শাসনের গুরুত্ব দিয়েছেন “যদি রাজা নৈতিক হন, তবে প্রজারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নৈতিক হয়ে উঠবে।”
চাণক্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে বলেন, রাজা যদি ন্যায়ভ্রষ্ট হন, তবে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।
১.৪. বাস্তব রাজনীতিতে নীতির সংকট:
তাত্ত্বিক আলোচনায় রাজনীতি ও নীতির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হলেও বাস্তবে অধিকাংশ সময় রাজনীতি নীতিহীন হয়েছে। এর কয়েকটি কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নিম্নরূপ:
ক্ষমতার লোভ: শাসকরা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য সবকিছু বিসর্জন দেন।
দুর্নীতি: ব্যক্তিগত সম্পদ সঞ্চয়ের জন্য নীতি বিসর্জন দেওয়া হয়।
স্বজনপ্রীতি ও পরিবারতন্ত্র: যোগ্যতার পরিবর্তে আত্মীয়কেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
বৈষম্য সৃষ্টি: রাষ্ট্রের সম্পদ কেবল শাসকশ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়।
১.৫. তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচনা:
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভেলি ’দ্য প্রিন্স’ গ্রন্থে বলেছিলেন, “রাজনীতিতে উদ্দেশ্যই প্রধান; লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে কোনো উপায় গ্রহণযোগ্য।” এই দর্শনই অনেক শাসককে নীতিহীন রাজনীতির পথে ঠেলে দেয়। কিন্তু সমালোচকরা বলেন, এই দর্শন সাময়িকভাবে শাসকের স্বার্থ রক্ষা করলেও দীর্ঘমেয়াদে রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। কারণ, জনগণের আস্থা একবার ভেঙে গেলে তা আর সহজে ফিরিয়ে আনা যায় না।
২ : রাজনীতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:
রাজনীতির ইতিহাস যত পুরোনো, নীতিহীন রাজনীতির উদাহরণও ততই পুরোনো। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা পর্যন্ত আমরা দেখি, রাজনীতি প্রায়শই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ, দমননীতি, লোভ এবং প্রতারণার মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছে। যদিও অনেক দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও সংস্কারক নীতিনিষ্ঠ রাজনীতির স্বপ্ন দেখিয়েছেন, বাস্তবের শাসকরা অধিকাংশ সময়েই সেই নীতি বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিস্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এই অধ্যায়ে আমরা প্রাচীন, মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক সময়ের কিছু উল্লেখযোগ্য উদাহরণ তুলে ধরছি।
২.১. প্রাচীন গ্রিস ও রোম:
গ্রিসে নীতি ও রাজনীতির দ্বন্দ্ব: প্রাচীন গ্রিসকে বলা হয় গণতন্ত্রের জন্মভূমি। এথেন্স নগররাষ্ট্রে জনগণের অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা ছিল। তাত্ত্বিকভাবে সেখানে নীতিনিষ্ঠ রাজনীতির চেষ্টা দেখা যায়। তবে বাস্তবতায় রাজনৈতিক ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল অভিজাত নাগরিকদের মধ্যে। নারী, দাস এবং বিদেশিরা রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।
অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, “ন্যায়পরায়ণতা রাজনীতির মূল ভিত্তি।” কিন্তু বাস্তবে এথেন্সসহ অনেক নগররাষ্ট্রে ক্ষমতার জন্য সংঘর্ষ, ষড়যন্ত্র ও হত্যা ছিল নিয়মিত ঘটনা। সুতরাং রাজনীতিতে রাজা বা শাসক ছিল, কিন্তু সর্বজনীন নীতি ছিল না।
রোম সাম্রাজ্য:
রোমের ইতিহাস নীতিহীন রাজনীতির উজ্জ্বল উদাহরণ। প্রজাতন্ত্রী রোমে প্রথমে কিছুটা নীতির চর্চা থাকলেও সাম্রাজ্যিক যুগে তা দ্রুত হারিয়ে যায়। জুলিয়াস সিজার ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার জন্য সেনেটকে পাশ কাটিয়ে একক শাসন কায়েম করেন। নিরো ছিলেন রোমের সবচেয়ে কুখ্যাত সম্রাট। তিনি ভোগবিলাসে মেতে থাকতেন এবং বলা হয় রোম নগরীতে আগুন লাগার সময় তিনি বীণা বাজাচ্ছিলেন। তিনি খ্রিষ্টানদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালিয়েছিলেন। ক্যালিগুলা ছিলেন মানসিকভাবে অসুস্থ শাসক, যিনি নিজের ঘোড়াকেও সেনেটর বানাতে চেয়েছিলেন। এথেকে বুঝা যায়, রোমে রাজা বা সম্রাট ছিল, কিন্তু নীতি ছিল অনুপস্থিত।
২.২ প্রাচীন ভারতীয় উপমহাদেশ:
ভারতের ইতিহাসেও নীতিহীন রাজনীতির অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে। মৌর্য সাম্রাজ্য: চাণক্য যদিও রাজনীতিকে অর্থশাস্ত্রে নীতিনিষ্ঠ করার চেষ্টা করেছিলেন, তবুও চন্দ্রগুপ্তের পরবর্তী শাসকদের মধ্যে সেই আদর্শ টেকেনি।
মৌর্য সম্রাট অশোক প্রথমদিকে নিষ্ঠুর যুদ্ধ চালিয়েছিলেন (কালিঙ্গ যুদ্ধ), যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে নীতিনিষ্ঠ রাজনীতির পথে হাঁটেন।
মুঘল সাম্রাজ্য: সম্রাট আকবরের শাসনে কিছুটা নীতি ও সহিষ্ণুতা দেখা গেলেও আওরঙ্গজেবের শাসন ছিল কঠোর, সাম্প্রদায়িক এবং দমননীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত।
ভারতের নবাবি আমলেও নীতিহীন রাজনীতির শিকার হয়ে দেশ পরাধীন হয়েছিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন এর বড় উদাহরণ। পলাশীর যুদ্ধে তাঁর সেনাপতিরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ব্যক্তিস্বার্থে।
২.৩. মধ্যযুগীয় ইউরোপ:
মধ্যযুগে ইউরোপে চার্চ ও রাজনীতির মেলবন্ধন ঘটেছিল। পোপ ও রাজারা যৌথভাবে জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করতেন।
ক্রুসেড যুদ্ধসমূহ (১১তম থেকে ১৩তম শতাব্দী) বাহ্যত ধর্মীয় যুদ্ধ হলেও বাস্তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা ও ভূখণ্ড দখলের জন্য পরিচালিত হয়েছিল। রাজারা চার্চকে ব্যবহার করতেন নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য। এর ফলে ধর্ম ও নীতির আড়ালে দুর্নীতি ও স্বার্থপরতা ফুলেফেঁপে ওঠে। এ সময়ে সাধারণ মানুষ ছিল শোষণের শিকার। কৃষকরা দাসত্বে আবদ্ধ ছিল, অথচ রাজা ও অভিজাতরা ভোগবিলাসে মত্ত ছিল।
২.৪ উপনিবেশবাদী যুগ:
১৫তম থেকে ২০তম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় শক্তিগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল দখল করে উপনিবেশ বানিয়েছিল। উপনিবেশবাদ ছিল নীতিহীন রাজনীতির এক ক্ল্যাসিক উদাহরণ।
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভারতীয় উপমহাদেশকে প্রায় ২০০ বছর শাসন করেছে। “সভ্যতার আলো ছড়ানো”র নামে তারা অর্থনৈতিক শোষণ, দমননীতি এবং বিভাজন কৌশল চালু করেছিল। বাংলার বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়, কৃষকরা নীলচাষে বাধ্য হয়, দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়।
আফ্রিকা: ইউরোপীয় শক্তিগুলো আফ্রিকার দেশগুলোকে ভাগ করে নিজেদের উপনিবেশ বানায়। স্থানীয় মানুষদের দাস বানিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকায় বিক্রি করা হয়।
আমেরিকা মহাদেশ: ইউরোপীয়রা স্থানীয় আদিবাসীদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং তাদের জমি দখল করে।
উপনিবেশবাদ দেখিয়েছে, রাজনীতি যখন নীতিহীন হয়, তখন তা সভ্যতার নাম নিয়ে সভ্যতাকে ধ্বংস করে।
২.৫. আধুনিক সময়ে নীতিহীন রাজনীতি:
হিটলার ও নাৎসি জার্মানি:
২০তম শতাব্দীতে অ্যাডলফ হিটলার ছিলেন নীতিহীন রাজনীতির প্রতীক। তিনি ক্ষমতায় আসার পর গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ইহুদি নিপীড়ন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, এবং লাখ লাখ মানুষের গণহত্যা তাঁর রাজনীতিকে কলঙ্কিত করেছে।
স্টালিন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন:
যোসেফ স্টালিন সমাজতন্ত্রের নামে কোটি কোটি মানুষকে শ্রম শিবিরে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর শাসনে ভিন্নমতকে দমন করা হয়েছিল নিষ্ঠুরভাবে। অর্থাৎ জনগণের নামে রাজনীতি হলেও নীতি সেখানে অনুপস্থিত ছিল।
আফ্রিকার একনায়করা:
উগান্ডার ইদি আমিন, জিম্বাবুয়ের রবার্ট মুগাবে, এরা সকলেই ক্ষমতায় থেকে নিজেদের স্বার্থ পূরণ করেছেন, জনগণের নয়।
২.৬. বিশ্লেষণ:
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট, রাজনীতিতে সব সময়ই রাজা বা ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল, কিন্তু নীতি প্রায়ই অনুপস্থিত থেকেছে। প্রাচীন রোমের নিরো থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের হিটলার পর্যন্ত উদাহরণগুলো আমাদের শেখায়, নীতিহীন রাজনীতি স্বল্পমেয়াদে শাসকের ক্ষমতা মজবুত করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতার জন্য তা ধ্বংসাত্মক।
৩. প্রাচীন যুগের রাজনীতি:
রাজনীতির ইতিহাস মানবসভ্যতার ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকেই শাসনব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সবসময়ই তা নীতিনিষ্ঠ ছিল না। বরং ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে আমরা এমন উদাহরণ পাই যেখানে শাসক বা রাজা ব্যক্তিগত স্বার্থ, ক্ষমতার লালসা কিংবা দমননীতির মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন।
৩.১. মেসোপটেমিয়া ও ব্যাবিলন:
বিশ্বের প্রথম দিককার সভ্যতা মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক অঞ্চলে) রাজনীতির একটি প্রাথমিক রূপ গড়ে তোলে। হ্যামুরাবির বিখ্যাত আইনকানুন থাকলেও শাসকগণ প্রায়শই আইনকে নিজেদের ক্ষমতা সুসংহত করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতেন। সেখানে জনগণের ন্যায্য অধিকার সবসময়ই অবহেলিত হতো। আইনকে বাহ্যত ন্যায্য মনে হলেও বাস্তবে তা শাসকের সুবিধামতো প্রয়োগ করা হতো।
৩.২. প্রাচীন মিশর:
মিশরের ফারাওরা নিজেদের “দেবতার প্রতিনিধি” বলে দাবি করতেন। তারা মহৎ পিরামিড, মন্দির ও সমাধি নির্মাণ করলেও শ্রমিকদের ওপর অমানবিক পরিশ্রম চাপিয়ে দিতেন। সাধারণ প্রজাদের জীবন ছিল দুর্বিষহ, অথচ রাজা বিলাসে জীবনযাপন করতেন। এতে প্রতিফলিত হয়, রাজা ছিলেন, কিন্তু জনগণের ন্যায়নীতি ছিল গৌণ।
৩.৩. প্রাচীন রোম:
রোমান সাম্রাজ্যে প্রথমদিকে প্রজাতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো থাকলেও পরবর্তীতে সম্রাটরা একনায়কতন্ত্র কায়েম করেন। জুলিয়াস সিজারের হত্যাকাণ্ড (৪৪ খ্রিষ্টপূর্ব) এবং তার পরবর্তী সময়ের সম্রাটদের শাসন এই বাস্তবতাকে উন্মোচিত করে।
৪. মধ্যযুগীয় রাজনীতি:
৪.১. ইউরোপের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা:
মধ্যযুগে ইউরোপজুড়ে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বিরাজ করত। সেখানে রাজা বা লর্ডরা নিজেদের ক্ষমতা সুসংহত করতে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করত। চার্চের প্রভাবের কারণে ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ার বানানো হয়। কিন্তু সাধারণ মানুষ ছিলেন চরম দারিদ্র্যের শিকার। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক উভয় কর্তৃত্বই মানুষের মৌলিক অধিকারের প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয়নি।
৪.২. ইসলামি খেলাফত ও সুলতানাত:
প্রাথমিক ইসলামি খেলাফত তুলনামূলকভাবে ন্যায্য শাসনের দৃষ্টান্ত তৈরি করলেও পরবর্তী আমলে কিছু খেলাফতের রাজনৈতিক চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ, উমাইয়া ও আব্বাসীয় খেলাফতের শেষ পর্যায়ে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বিলাসিতা ও ভোগ-বিলাসে আসক্তি দেখা যায়। মুসলিম বিশ্বে একদিকে উন্নত সভ্যতা গড়ে উঠলেও নৈতিক রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্ষয়ে যেতে থাকে।
৪.৩. ভারতীয় উপমহাদেশ:
ভারতের মোগল সম্রাটদের মধ্যে কিছু যেমন আকবর “সুলহে কুল” নীতি গ্রহণ করে তুলনামূলক ন্যায্য শাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু আওরঙ্গজেবের সময় ধর্মীয় সংকীর্ণতা, নিপীড়ন ও ক্ষমতার লড়াই তীব্র হয়ে ওঠে। প্রজারা ক্রমেই অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। ফলে মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে। এখানে বোঝা যায়, নীতি উপেক্ষিত হলে কেবল শক্তিশালী সাম্রাজ্যও টিকে থাকতে পারে না।
৫. আধুনিক যুগের রাজনীতি:
১৬শ শতক থেকে ইউরোপীয় শক্তিগুলো এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় ঔপনিবেশিক শাসন চালু করে। ব্রিটিশ, ফরাসি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ ও ডাচরা অর্থনৈতিক শোষণ, প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠন এবং স্থানীয় জনগণের উপর দমননীতি চালু করে।
বাংলাদেশসহ ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন ছিল “রাজা আছে, নীতি নাই”-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তারা প্রশাসনিক কাঠামো গড়লেও উদ্দেশ্য ছিল কেবল নিজেদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা। দুর্ভিক্ষ, কৃষকের দারিদ্র্য এবং শিল্পের ধ্বংস এ নীতিহীন শাসনেরই ফল।
৫.১. ফরাসি বিপ্লব ও পরবর্তী ইউরোপ:
ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯) এক অর্থে জনগণের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের “নীতিহীন রাজনীতি”-র প্রতিক্রিয়া। লুই ষোড়শ ও তার দরবার বিলাসিতায় ডুবে থাকলেও সাধারণ মানুষ ক্ষুধার্ত ছিল। জনগণই তখন বিদ্রোহ করে এবং নতুন গণতন্ত্রের পথ প্রশস্ত করে।
৫.২. একনায়কতান্ত্রিক শাসন:
২০শ শতাব্দীর বিশ্বে নীতিহীন রাজনীতির সর্বাধিক ভয়ঙ্কর রূপ দেখা যায় ফ্যাসিবাদ ও স্বৈরশাসনে।
অ্যাডলফ হিটলার (জার্মানি): জাতিগত ঘৃণা ও ক্ষমতার লালসার কারণে লক্ষ লক্ষ ইহুদীকে হত্যা করেন। বেনিতো মুসোলিনি (ইতালি): রাষ্ট্রকে ব্যক্তিগত ক্ষমতার খেলাঘরে পরিণত করেছিলেন। জোসেফ স্টালিন (সোভিয়েত ইউনিয়ন): সমাজতান্ত্রিক নামধারী হলেও বাস্তবে ব্যাপক দমননীতি ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চালান। এই উদাহরণগুলো দেখায়, রাজনীতিতে শক্তিমান রাজা বা শাসক ছিলেন, কিন্তু নীতি ছিল অনুপস্থিত।
৫.৩. ঐতিহাসিক শিক্ষা:
ইতিহাস আমাদের শেখায় যে, কোনো রাজনীতিই নীতি ছাড়া টেকসই হয় না। প্রাচীন মিশরের ফারাওরা, রোমের নিরো, মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপ, ঔপনিবেশিক শক্তি কিংবা ২০শ শতকের স্বৈরশাসক, সবাই একসময় পতনের মুখোমুখি হয়েছে। নীতির অনুপস্থিতি স্বল্পমেয়াদে ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা ধ্বংস ডেকে আনে।
৫.৪. কেস স্টাডি:
বিভিন্ন কেস স্টাডি থেকে স্পষ্ট হয় যে, নীতিহীন রাজনীতি সাময়িকভাবে শাসকের ক্ষমতা সুসংহত করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে তা ধ্বংস ডেকে আনে। রোমের নিরো থেকে শুরু করে হিটলার, মুসোলিনি, স্টালিন, ঔপনিবেশিক শক্তি কিংবা আফ্রিকার স্বৈরশাসক, সবার পতন প্রমাণ করে নীতি ছাড়া রাজনীতি টেকসই নয়।
৬. দক্ষিণ এশিয়া ও বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট:
ভূমিকা
বিশ্ব রাজনীতির নীতিহীনতা যেমন এক সর্বজনীন সত্য, তেমনি দক্ষিণ এশিয়াও এর বাইরে নয়। ভারতীয় উপমহাদেশ দীর্ঘ ইতিহাস ধরে নানা ধরনের শাসক, ঔপনিবেশিক শক্তি, স্থানীয় সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি এবং স্বাধীনতার পরবর্তী রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ভেতর দিয়ে গেছে। প্রতিটি সময়েই আমরা দেখতে পাই, রাজনৈতিক নেতৃত্বে “রাজা আছে, নীতি নাই” প্রবাদের প্রতিফলন।
৬.১. মগধ ও মৌর্য সাম্রাজ্য:
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও সম্রাট অশোকের সময় ভারতবর্ষে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তবে অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের আগে কলিঙ্গ যুদ্ধ ছিল নীতিহীন রাজনীতির উদাহরণ, যেখানে লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়েছিল।
৬.২. দিল্লি সুলতানাত ও মোগল যুগ:
দিল্লি সুলতানাতের অনেক শাসক ছিলেন অত্যাচারী ও দমনমূলক। জনগণের করের টাকা দিয়ে বিলাসী জীবনযাপন করতেন।
মোগলদের মধ্যে আকবর তুলনামূলক নীতিনিষ্ঠ শাসক হিসেবে পরিচিত হলেও আওরঙ্গজেব ধর্মীয় সংকীর্ণতা ও ক্ষমতার লড়াইকে প্রাধান্য দেন। এর ফলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ জন্ম নেয় এবং সাম্রাজ্যের ভাঙন শুরু হয়।
৬.৩. ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন:
৬.৩.১. শোষণমূলক রাজনীতি
১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এরপর ধীরে ধীরে পুরো উপমহাদেশ তাদের দখলে আসে। ব্রিটিশ শাসন ছিল অর্থনৈতিক শোষণের উপর ভিত্তি করে। কৃষকদের কাছ থেকে অমানবিক হারে খাজনা আদায় করা হতো। ১৭৭০ সালের বাংলার মহাদুর্ভিক্ষে প্রায় ১ কোটি মানুষ মারা যায়, অথচ ব্রিটিশরা তখনো কর আদায় চালিয়ে যায়।
৬.৩.২. “ভাগ করে শাসন” নীতি:
ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে তাদের শাসন দীর্ঘায়িত করে। এটি ছিল সম্পূর্ণ নীতিহীন কৌশল, যার প্রভাব আজও ভারতীয় উপমহাদেশে বিরাজ করছে।
৬.৩.৩. ভারত-পাকিস্তান বিভাজন ও রাজনীতি:
ভারত-পাকিস্তান বিভাজন (১৯৪৭) ছিল মূলত রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষমতার লড়াইয়ের ফল। ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভাজন ঘটলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করা। বিভাজনের সময় দাঙ্গা ও সহিংসতায় লক্ষাধিক মানুষ নিহত ও কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়।
৬.৩.৪. পাকিস্তানি শাসন (১৯৪৭-১৯৭১):
পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলাকে (পরে বাংলাদেশ) উপনিবেশের মতো ব্যবহার করেছিল। অর্থনৈতিক বৈষম্য, ভাষার অধিকারহরণ, রাজনৈতিক দমননীতি সবই ছিল নীতিহীন রাজনীতির প্রতিফলন। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সেই শোষণ ও অনীতির বিরুদ্ধে বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম।
৭. স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতি:
১৯৭১ সালের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ পুনর্গঠনের পথে এগোয়। তবে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও আন্তর্জাতিক স্বার্থচক্রের কারণে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনি সপরিবারে নিহত হন। এর পর থেকেই বাংলাদেশ আবারও নীতিহীন রাজনীতির পথের দিকে দাবিত হয়।
৭.১. সামরিক শাসন ও অনীতি
১৯৭৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত বাংলাদেশ বারবার সামরিক শাসনের মুখোমুখি হয়। জনগণের অধিকার উপেক্ষিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে দমন করা হয়।
৭.২. গণতান্ত্রিক ধারা ও দ্বন্দ্ব:
১৯৯০ সালে গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরশাসকের পতন ঘটে এবং গণতান্ত্রিক ধারা শুরু হয়। কিন্তু এর পরবর্তী সময়েও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, বিতর্কিত নির্বাচন, দুর্নীতি, দলীয়করণ এবং স্বজনপ্রীতি নীতি থেকে বিচ্যুতি প্রমাণ করে।
৮. দক্ষিণ এশিয়ায় ক্ষমতার রাজনীতি বনাম জনস্বার্থ:
বাংলাদেশ: বর্তমান বাংলাদেশে রাজনীতি প্রায়শই ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক শক্তিকে দমন, নির্বাচনী প্রক্রিয়ার দুর্বলতা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, সবকিছুই “রাজা আছে, নীতি নাই” প্রবাদের আধুনিক প্রতিফলন। জনগণ স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনার ভিত্তিতে একটি ন্যায্য ও কল্যাণমুখী রাষ্ট্র প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু বাস্তবে রাজনীতি অনেকাংশেই ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থের কাছে বন্দী হয়ে পড়েছে।
ভারত: ভারতে গণতন্ত্র কার্যকর হলেও দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং ক্ষমতার রাজনীতি নীতির অভাবকে প্রকাশ করে।
পাকিস্তান: পাকিস্তানে সামরিক শাসন, দুর্নীতি ও রাজনৈতিক অস্থিরতা নীতিহীন রাজনীতির উদাহরণ।
শ্রীলঙ্কা ও নেপাল: শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধ ও জাতিগত রাজনীতি দীর্ঘদিন নীতি ও মানবাধিকারের বিরুদ্ধে অবস্থান করেছে। নেপাল দীর্ঘসময় রাজতন্ত্র ও রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার।
উপসংহার:
দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি প্রমাণ করে এখানে শাসক বা রাজনৈতিক দল সবসময়ই উপস্থিত থেকেছে, কিন্তু নীতি অনেক সময় অনুপস্থিত থেকেছে। ঔপনিবেশিক শাসন, পাকিস্তানি দমননীতি, কিংবা স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রতিটি স্তরেই “রাজা আছে, নীতি নাই” প্রবাদের বাস্তব রূপ দেখা যায়।
তবে ইতিবাচক দিকও রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ, গণআন্দোলন এবং জনগণের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম দেখিয়েছে, জনগণ সবসময় নীতির রাজনীতি প্রত্যাশা করে।
৯ : নীতিহীন রাজনীতির প্রভাব ও ভবিষ্যৎ করণীয়:
ভূমিকা:
রাজনীতিতে নীতি হারিয়ে গেলে সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্বর প্রভাব পড়ে। ইতিহাসে যেমন দেখা গেছে, নীতিহীন রাজনীতি জনগণের দুঃখ-কষ্ট বাড়িয়েছে, তেমনি সমকালীন বিশ্বেও এই প্রবণতা বিদ্যমান। তবে এর পাশাপাশি প্রশ্ন ওঠে, ভবিষ্যতে কীভাবে রাজনীতি নীতিনিষ্ঠ করা সম্ভব? এখানে নীতিহীন রাজনীতির বহুমাত্রিক প্রভাব এবং ভবিষ্যৎ করণীয় বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।
৯.১. নীতিহীন রাজনীতির সামাজিক প্রভাব:
৯.১.১. নৈতিক অবক্ষয়:
যখন রাজনৈতিক নেতারা নীতি উপেক্ষা করেন, তখন সমাজে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অসততা সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। জনগণও বিশ্বাস করতে শুরু করে যে অনৈতিক উপায়ে উন্নতি লাভ করাই একমাত্র পথ।
৯.১.২ সামাজিক বিভাজন:
নীতিহীন রাজনীতি প্রায়শই ধর্ম, জাতি বা ভাষার ভিত্তিতে বিভেদ তৈরি করে। যেমন ভারতবর্ষে ব্রিটিশরা “ভাগ করে শাসন” নীতি প্রয়োগ করেছিল, তেমনি আধুনিক সময়েও অনেক রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক বিভাজন রাজনীতির হাতিয়ার।
৯.১.৩ মানবাধিকার লঙ্ঘন:
স্বৈরাচারী শাসকরা নীতির তোয়াক্কা না করে জনগণের মৌলিক অধিকার কেড়ে নেয়। ফলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণ সীমিত হয়ে পড়ে।
৯.২. অর্থনৈতিক প্রভাব:
৯.২.১. দুর্নীতি ও লুটপাট:
নীতিহীন রাজনীতির অন্যতম বড় প্রভাব হলো দুর্নীতি। সরকারি সম্পদ ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। ফলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।
৯.২.২. বৈষম্য বৃদ্ধি:
যখন নীতি উপেক্ষিত হয়, তখন উন্নয়ন কেবল কিছু গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। সমাজে ধনী-গরিবের বৈষম্য বাড়তে থাকে।
৯.২.৩. অস্থিতিশীল অর্থনীতি:
অনৈতিক নীতি, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে বিনিয়োগ কমে যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আস্থাহীনতা সৃষ্টি হয়। এর ফলে সামগ্রিক অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে।
৯.৩. রাজনৈতিক প্রভাব:
৫.৩.১ গণতন্ত্রের অবক্ষয়:
নীতিহীন রাজনীতিতে নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হয়। ভোট কারচুপি, প্রতিদ্বন্দ্বী দমন, এবং দলীয়করণ গণতন্ত্রকে দুর্বল করে।
৯.৩.২. রাজনৈতিক সহিংসতা:
নীতির পরিবর্তে শক্তি ও সহিংসতা রাজনীতির মাধ্যম হয়ে ওঠে। এতে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ভেঙে পড়ে।
৯.৩.৩. আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা:
নীতিহীন রাজনীতি রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অবিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। এতে কূটনৈতিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
৯.৪. সাংস্কৃতিক প্রভাব:
৯.৪.১. মূল্যবোধের অবক্ষয়:
যখন রাজনীতি নীতিহীন হয়, তখন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষা খাতেও সেই প্রভাব পড়ে। নৈতিকতা ও মানবিকতা দুর্বল হয়ে যায়।
৯.৪.২. স্বাধীন চিন্তার সংকোচন:
নীতিহীন রাজনীতি মুক্তচিন্তা, গবেষণা ও সৃজনশীলতাকে দমন করে। ফলে জাতির অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়।
৯.৫ আন্তর্জাতিক প্রভাব:
৯.৫.১. যুদ্ধ ও সংঘাত:
নীতিহীন রাজনীতি প্রায়শই যুদ্ধের জন্ম দেয়। যেমন হিটলারের নীতিহীন আগ্রাসন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়।
৯.৫.২ শরণার্থী সংকট:
অন্যায় শাসন ও যুদ্ধের কারণে কোটি মানুষ শরণার্থী হয়ে পড়ে। আধুনিক কালে সিরিয়া, আফগানিস্তান ও মিয়ানমারের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য।
৯.৬. ভবিষ্যৎ করণীয়:
৯.৬.১. নৈতিক নেতৃত্ব গড়ে তোলা:
শিক্ষা ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাধ্যমে নৈতিক নেতৃত্ব তৈরির প্রয়োজন। নীতিহীন নেতাদের প্রতিরোধ করতে জনগণকেও সচেতন হতে হবে।
৯.৬.২. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা:
সরকারি কাজকর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা ছাড়া নীতি ফিরে আসবে না। গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকে সক্রিয় হতে হবে।
৯.৬.৩. গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি শক্তিশালী করা:
নির্বাচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বাধীন করতে হবে। দলীয় স্বার্থের বাইরে গিয়ে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
৯.৬.৪. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:
বৈশ্বিক রাজনীতিতে ন্যায্যতা আনতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে কার্যকর করতে হবে। উন্নত দেশগুলোর নীতিহীনতা বন্ধ করতে হবে।
৯.৭. উপসংহার:
নীতিহীন রাজনীতি কেবল একটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সমস্যাই নয়, বরং তা বৈশ্বিক শান্তি ও উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। অতএব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও নীতিনিষ্ঠ রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। ইতিহাস প্রমাণ করেছে— “রাজা আছে, নীতি নাই” ধারা দীর্ঘমেয়াদে টেকসই হয় না।
১০. চুড়ান্ত উপসংহার:
মানবসভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই, নীতিহীন রাজনীতি কখনোই টেকসই হয়নি। প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক বিশ্ব, সর্বত্রই এমন শাসকের উদাহরণ আছে যারা ক্ষমতার মোহে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়েছে। তারা হয়তো সাময়িকভাবে জনগণকে দমন করেছে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুণ্ঠন করেছে, এমনকি যুদ্ধ শুরু করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইতিহাস তাদের নির্মমভাবে বিচার করেছে।
“রাজনীতিতে রাজা আছে, নীতি নাই” প্রবাদটি আসলে ক্ষমতাসীনদের প্রতি সতর্কবার্তা। নীতিহীনতা সাময়িকভাবে সফলতার মুখ দেখালেও তা জনগণের আস্থা ধ্বংস করে, সমাজকে বিভক্ত করে এবং রাষ্ট্রকে দুর্বল করে তোলে।
অন্যদিকে ইতিহাসে আমরা নীতিনিষ্ঠ নেতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তও দেখি, যেমন আব্রাহাম লিঙ্কন, মহাত্মা গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, মেজর জিয়াউর রহমান কিংবা মাদার তেরেসার মতো ব্যক্তিত্বরা প্রমাণ করেছেন, রাজনীতিতে নীতি থাকলে তা দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন আনে এবং জনগণের মুক্তি নিশ্চিত করে।
বর্তমান বিশ্বে নীতিহীন রাজনীতি নানা রূপে বিদ্যমান। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, সাম্প্রদায়িক বিভাজন, এগুলো কেবল উন্নয়নকে ব্যাহত করছে না, বরং বৈশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্যও হুমকি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। সুতরাং আজকের পৃথিবীতে নীতির আলোকে রাজনীতি পরিচালনা করা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি জরুরি।
ভবিষ্যতের জন্য আমাদের করণীয় হলো, শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতার চর্চা বৃদ্ধি, রাজনৈতিক নেতৃত্বে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। কেবল তাহলেই আমরা এমন এক রাজনীতি গড়ে তুলতে পারব যেখানে থাকবে রাজা, আবার থাকবে নীতি।
লেখক: কবি ও সাংবাদিক, সভাপতি, রেলওয়ে জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন।
এমএসএম / এমএসএম

পবিত্র শবে বরাত: হারিয়ে যেতে বসা আত্মার জন্য এক গভীর ডাক : মোহাম্মদ আনোয়ার

ঘুষ, দালাল ও হয়রানি: জনগণের রাষ্ট্রে জনগণই সবচেয়ে অসহায়!

সুস্থ জীবনের স্বার্থে খাদ্যে ভেজাল রোধ জরুরী

আস্থার রাজনীতি না অনিবার্যতা: তারেক রহমান ও বাংলাদেশের রাজনৈতিক শূন্যতা!

রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কঠিন পরীক্ষায় ত্রয়োদশ নির্বাচন

নির্বাচনী ট্রেইনে সব দল, ক্ষমতার চূড়ান্ত মালিক জনগণ!

ঈমানের হেফাজতের নগরী মদিনা: মক্কার চেয়ে দ্বিগুণ বরকতের অন্তর্নিহিত রহস্য!

বিপ্লবের আশা-আকাঙ্ক্ষার যেন অপমৃত্যু না হয়

গণমানুষের আস্থার ঠিকানা হোক গণমাধ্যম
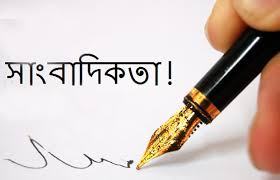
নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা: সরকার-বিরোধী উভয়েরই কল্যাণকর

শবে মেরাজের তাজাল্লি ও জিব্রাইল (আ.) এর সীমা: এক গভীর ও বিস্ময়কর সত্য!

অকুতোভয় সাংবাদিক মানিক সাহা হত্যা: ২২ বছরেও ধরাছোঁয়ার বাইরে মূল পরিকল্পনাকারীরা

